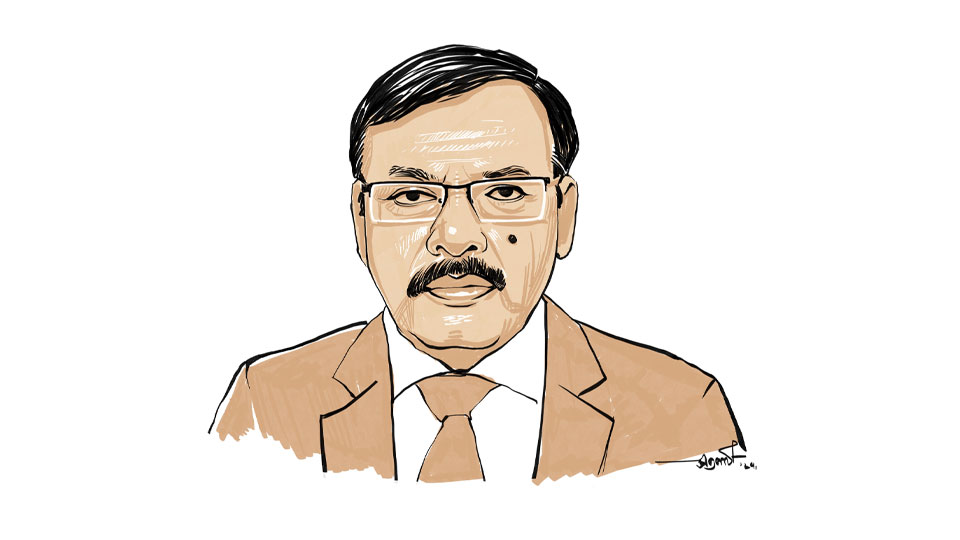নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়ত জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন পৌষ পর্ব।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: অগ্রহায়ণ পর্ব
আমাদের দেশটা আয়তনে ছোট হলেও উদ্ভিদ ও প্রাণবৈচিত্র্যে ভরপুর। এ দেশে প্রায় ৬ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট ও পরিবেশগত নানা কারণে বর্তমানে অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে সেগুলোকে বিপন্ন উদ্ভিদ বলা হয়ে থাকে। এখন বাংলাদেশের মোট উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ উদ্ভিদই বিপদের ঝুঁকিতে রয়েছে।
১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ২৫টি বিপন্ন উদ্ভিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশে বিপন্ন উদ্ভিদ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। এর ফলে দুটি খণ্ডে বিপন্ন উদ্ভিদগুলোর বিবরণ সম্বলিত ‘রেড ডাটা বুক অব ভাস্কুলার প্লান্ট’ নামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। প্রথম খণ্ডে ১০৬টি (২০০১) ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১২০টি (২০১৩) বিপন্ন উদ্ভিদ রেকর্ড করা হয়। এ বই দুটি এ দেশের বিপন্ন উদ্ভিদগুলো সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ, আইইউসিএন ২০২৪ সালে প্রকাশ করেছে এ দেশের ১০০০ মূল্যায়িত উদ্ভিদের বই ‘বাংলাদেশের উদ্ভিদ লাল তালিকা’। দুটি বিশাল খণ্ডের সে বইয়ে বলা হয়েছে যে, এ দেশে বর্তমানে ৩৯৫ প্রজাতির উদ্ভিদ বিপন্ন বা বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।
বাংলাদেশের ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী মোট ৫৪ প্রজাতির উদ্ভিদকে সংরক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব উদ্ভিদ ইচ্ছাকৃতভাবে উপড়ানো, উঠানো বা ধ্বংস করা যাবে না। এসব প্রজাতির উদ্ভিদ যেটা যেখানে রয়েছে তাকে সেখানেই সংরক্ষণ করতে হবে। ঢাকা শহরেও এই ৫৪ প্রজাতির উদ্ভিদের কিছু প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে, যেমন ধূপগাছ, বাঁশপাতি, কুম্ভি, সিভিট, কর্পূর, মনিরাজ, পাদাউক, রিটা, কুসুম, উদাল, উদয়পদ্ম, কুর্চি, তমাল, বুদ্ধ নারকেল ও বর্মি মাইলাম। পূর্বের পর্বগুলোর লেখার মধ্যে এসব বৃক্ষের অনেকগুলো নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্বে আলোচনা করা হলো সংরক্ষিত বৃক্ষ ধূপ, কুম্ভি ও বাঁশপাতি গাছ নিয়ে। তবে রাজ অশোক এ তালিকায় না থাকলেও তা বিপন্ন বা দুর্লভ বৃক্ষ বলে মনে হয়।

রাজ অশোক বা বার্মা ফুল
অশোক, স্বর্ণ অশোক আর রাজ অশোক তিন মিত্র। অশোকগাছ এ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেলেও স্বর্ণ অশোক ও রাজ অশোক গাছ খুব কম দেখা যায়। ঢাকার বিভিন্ন উদ্যানে এ তিন রকমের অশোক গাছই আছে। তিন অশোকগাছই এ দেশে এসেছে অন্য দেশ থেকে। অশোক (Saraca indica) ভারতীয় উপমহাদেশ ও মালয়ের গাছ, স্বর্ণ অশোক (Saraca thaipingensis) দক্ষিণ এশিয়ার ও রাজ অশোক (Amherstia nobilis) মিয়ানমারের গাছ। অশোক আর স্বর্ণ অশোক গাছের ফুলের গড়নে বেশ মিল রয়েছে, ছোট ছোট ফুল ফোটে খোঁপার মতো থোকা ধরে। অশোকের ফুল লাল, ফুল ফোটে বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। স্বর্ণ অশোকের ফুল হলুদ-সোনালি, ফোটে শীতকালে। রাজ অশোকের ফুল এ দুটো থেকে একবারেই আলাদা গড়নের, এলামেলো ফুলগুলো ফোটে লম্বা বেণীর মতো ছড়ায়, রঙ ফিকে লাল থেকে লাল, ফুল ফোটে হেমন্ত থেকে শীতকালে।
রাজ অশোক মাঝারি আকারের বৃক্ষ, গাছ ৮ থেকে ১০ মিটার লম্বা হয়। পাতা ও ডালপালা অশোকের মতোই, তবে রাজ অশোকের পাতায় ছিট ছিট দাগ আছে। পাতা যৌগিক ও একটি পত্রদণ্ডে ৬-৮টি বড় লম্বাটে পত্রক থাকে। কচি পাতা নিচের দিকে ঝুলতে থাকে ও লালচে রঙের। ঝাড়বাতির মতো ঝুলন্ত পুষ্পমঞ্জরিতে ৩-৫টি ফুল ফোটে। অশোক ও স্বর্ণ অশোকের চেয়ে রাজ অশোকের ফুল বড়, পাঁপড়ি পাঁচটি গাঢ় লাল, এর মধ্যে দুটি পাপড়ি ছোট, একটি বড় এবং সেই পাঁপড়িটির মাথার মাঝে সাদা ও লালে চিত্রিত, অন্য পাপড়ি দুটির আকারও ভিন্ন। ফল শিমের মতো, শক্ত। ফল পাকলে শক্ত খোসা ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। রাজ অশোকের বংশবৃদ্ধি সহজে করা যায় না, বীজে সবসময় চারা হয় না, চারা করতে হয় গুটি কলম করে। সেজন্য এ গাছটি এ দেশে খুব বেশি স্থানে ছড়ায়নি। ঢাকা শহরে রাজ অশোক দুর্লভ। বলধা গার্ডেনে ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে কয়েকটি রাজ অশোক গাছ আছে।

রাজ অশোক নামটি রেখেছিলেন বলধা গার্ডেনের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক শ্রী অমৃতলাল আচার্য্য। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর মতো সুন্দর রূপ না থাকলেও রাজ আশোক ফুলের দোলায়মান পুষ্পমঞ্জরির এলোমেলো নৃত্যের একটা ছন্দ আছে। সেজন্য কি না জানিনা, রাজ অশোকের আরেক বাংলা নাম করা হয়েছে উর্বশী, ইংরেজি নাম ‘Tree of heaven’। উর্বশী নাম রাখার সাথে এটাও সম্পর্কিত হতে পারে। ফুলের আকার-আকৃতি ও প্রস্ফুরণ অনেকটা অর্কিডের মতো। এজন্য রাজ অশোক গাছের অন্য নাম ‘Orchid tree’। দেশের নাম বার্মা থেকে মিয়ানমার হলেও এ গাছের নাম বদলায়নি, রয়ে গেছে তার ইংরেজি নাম ‘Pride of Burma’। এ জন্য কেউ কেউ রাজ অশোককে বলেন ‘বার্মা ফুল’। রাজ অশোকের জন্মভূমি মিয়ানমার। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে রাজ আশোক গাছ আছে। তবে এসব দেশেও রাজ অশোকগাছ খুব কম দেখা যায়।
‘বার্মা ফুল’ ও এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামকরণের পেছনে এক চমৎকার কাহিনী আছে। ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৬ সালে জনৈক জাঁদরেল কূটনীতিক ও প্রশাসক জন ক্রফার্ডকে বার্মায় পাঠান। ক্রফার্ডের একটা অভ্যেস ছিল ভ্রমণের সময় তিনি যা দেখতেন তার টুকিটাকি বিবরণ তিনি লিখে রাখতেন। বার্মায় তিনি একদিন মারতাবানে এক বৌদ্ধ গুহার সামনে একটি চমৎকার ফুলের দেখা পেলেন। অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছের সে ফুলের সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি এ ফুলের মধ্যে যেন বিশেষ কিছু খুঁজে পেলেন। ব্রিটেনে বা অন্য কোথাও তিনি এ গাছের কখনও দেখা পাননি। বৃটিশদের কাছে গাছটি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। তিনি তার খেরোখাতায় এ ফুলটি সম্পর্কে তাই লিখে রাখেন ‘‘এটা সত্যিই এক সুন্দর ফুল যা আগে কখনো দেখিনি।’’ তিনি ভাবলেন, ব্যতিক্রমী এ গাছটি হয়ত নতুন কোনও ‘উদ্ভিদ গণ’ যা তিনি আবিষ্কার করেছেন। নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাই তিনি গাছটির বিবরণ ও নমুনা সংগ্রহ করে শরণাপন্ন হন তৎকালীন ক্যালকাটা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিনটেন্ডেন্ট নাথানিয়েল ওয়ালিচের। মিয়ানমার থেকে সে গাছের চারা সংগ্রহ করে তিনি নিয়ে গেলেন কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে চারাটি রোপিত হলো বৃটিশদের এক প্রণয়াসক্ত ভালোবাসার প্রতীক হয়ে। ধীরে ধীরে একদিন ওয়ালিচ উদ্ভিদটির গণগত নামকরণ করলেন আমহার্স্টিয়া। যেহেতু গাছটির সাথে বৃটিশ রাজদের একটা সম্পর্ক ও সখ্যতা গড়ে উঠেছিল, তাই গাছের প্রজাতিগত নামের সাথে ‘নোবিলিস’ শব্দটি জুড়ে দেওয়া হলো। উদ্ভিদটির প্রজাতি তখন থেকে পরিচিতি পেল ‘আমহর্স্টিয়া নোবিলিস’ নামে।

আমরা বাঙালিরাও বৃটিশদের সে রাজসম্মান অক্ষুন্ন রেখে উদ্ভিদটির বাংলা নামকরণ করলাম ‘রাজ আশোক’। অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত রাজা। কথিত আছে যে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের এই পৌত্র কলিঙ্গরাজের সাথে যুদ্ধ করে হাজার হাজার মানুষের লাশ দেখে তাঁর জীবনের স্বভাবটাই বদলে ফেলেছিলেন। তাঁর নাম বদলে হয়েছিল সম্রাট অশোক। পুরাণের পার্বতী যে গাছের নিচে বসে তপস্যা করে তাঁর শোক দূর করেছিলেন, কালক্রমে সে গাছেরই নাম হয় আশোক। কিন্তু অশোক আর ‘রাজ আশোক’ এক গাছ নয়। আশোক আর রাজ আশোকের গাছ আছে ঢাকায় বলধা গার্ডেনের সাইকি অংশে, মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে। রাজ আশোকের ফুল ফোটে হেমন্তে, আশোকের ফুল ফোটে বসন্তে। মাঝখানে শীতে ফোটে স্বর্ণ আশোক। বলাবাহুল্য যে আমহার্স্টিয়া গণে একটি মাত্র প্রজাতিই আছে যা সচরাচর কোনও উদ্ভিদ গণের ক্ষেত্রে থাকে না। এ দিক দিয়েও সে গণেশ্বরী।
ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে উদ্ভিদবিদ ওয়ালিচ সে সময় বার্মা থেকে সংগ্রহ করা প্রায় ২০০০ প্রজাতির একটি তালিকা তৈরি করেন। সে তালিকায় তিনি আমহার্স্টিয়া নোবিলিস প্রজাতির নামও অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮২৮ সালে তিনি রাজ অশোকের একটি প্রজাতিগত বর্ণনা তৈরি করে লিনিয়ান সোসাইটিতে পাঠান। সে বিবরণে তিনি লেখেন, ‘‘চমৎকার এ গাছটির ফুল প্রায় দু ফুট লম্বা হয়ে পিরামিড আকারে নিচের দিকে পেন্ডুলামের মতো ঝোলে, পুষ্পমঞ্জরির গোড়ার দিকের বিস্তার প্রায় দশ ইঞ্চি।’’ তিনি লেখেন যে, ‘‘আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এ উদ্ভিদের প্রজাতিগত নামকরণ লেডি আমহার্স্টের সম্মানে আমহার্স্ট নোবিলিস রাখা হলো।’’ সেই থেকে এ উদ্ভিদের প্রজাতিগত নাম এটাই স্বীকৃতি পেল।
নিঃসন্দেহে ওয়ালিচের এই প্রজাতিগত নামকরণের পেছনে একটি রাজনৈতিক ও তোষামোদের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এ রকম ঘটনা বা সম্মান প্রদানের রীতি ইতিহাসের কখন কোথায় না ঘটেছে? রাজন্যবর্গের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোষামোদকারীদের তোষামোদীর সংস্কৃতি এ দেশে ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। নিঃসন্দেহে ওয়ালিচ ও ক্রফার্ড এই নামকরণের মাধ্যমে তৎকালীন গভর্নর জেনালের আমহার্স্টের কাছে তাদের আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে তাতে উদ্ভিদ জগতের কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং গভর্নর জেনোরেলের স্ত্রী সারাহ আমহার্স্ট (১৭৬২-১৮৩৮) ও তাদের কন্যা এলিজাবেথ আমহার্স্টের (১৮০১-১৮৭৬) এতে প্রকৃতিবিদ হওয়ার উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল। তারা দুজনই বার্মা ও ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির গাছ সংগ্রহে মেতে উঠেছিলেন। তারা এসব গাছের উদ্যান রচনাতেও ব্রতী হয়েছিলেন। আর তাদের কন্যা এলিজাবেথ সারাহ সেসব উদ্ভিদের অনেকগুলোর চমৎকার সব রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। গভর্নর হাউসকে তারা দুজন যেন একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরিণত করেছিলেন। এর ফলশ্রতিতে তৎকালীন ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে সৌখিন উদ্ভিদবিদ হিসেবে তাঁদের একটা স্বতন্ত্র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্যালকাটা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই রাজ অশোক গাছটিও ততদিনে অনেক দর্শনার্থীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।
কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস। ১৮২৮ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড বেন্টিংঙ্ক। গভর্নর জেনারেল পরিবর্তন হলে আমহার্স্ট ইংল্যান্ড ফিরে যান। আর তাদের মমতায় গড়া উদ্যানটিও হয়ে পড়ে অযত্নে মলিন, বিপন্ন। গভর্নর’স হাউসে নতুন গভর্নর জেনারেল সপরিবারে বসবাসের জন্য ওঠেন। গভর্নর’স হাউসের চারপাশে মনোরম সে উদ্যান দেখে জর্জ এডেনের বোন যার পর নাই আনন্দিত হয়ে বাকিংহামশায়ারে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিতে তিনি জানান, ‘‘লেডি আমহার্স্ট গভর্নর’স হাউসের চারপাশে সত্যিই চমৎকার একটি বাগান করে রেখে গেছেন যেখানে অনেক গাছপালা শোভা পাচ্ছে।’’ কিন্তু গভর্নর জেনারেল পরিবর্তন হওয়ার কিছুদিন পরই এমিলি এডেন শোক প্রকাশ করে আবার এক চিঠিতে লেখেন, ‘‘লেডি উইলিয়াম বেন্টিংঙ্ক বলেছেন, বাগানের গাছগুলো খুবই অস্বাস্থ্যকর, এবং তিনি প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই গাছগুলোকে উপড়ে ফেলেছেন।’’

গভর্নর’স হাউসের গাছগুলো চলে গেলেও কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই রাজ আশোক গাছ রয়ে গেছে। ফুল ফোটার মৌসুমে অনেকেই সেই রাজ অশোক ফুলের শোভা দেখতে সেখানে যান আর লেডি আমহার্স্টিয়ার উদ্ভিদপ্রেমের কথা স্মরণ করেন। এমনকি সে গাছের সুখ্যাতি শুনে ১৮৪৩ সালে জর্জ ডব্লিউ জনসন রাজ অশোককে দেখতে আসেন। দেখার পর তিনি তার ভ্রমণকাহিনী ‘The Stranger in India’ গ্রন্থে লেখেন ‘‘নিঃসন্দেহে এটি একটি সুদর্শন ও দুর্লভ উদ্ভিদসমূহের মধ্যে অন্যতম।’’ তাঁর এই কথা তৎকালীন বৃটিশ রাজদরবারে রাজন্যবর্গের মধ্যে বেশ ভালোই প্রতিধ্বনিত হয় ও অনেককেই এ গাছের প্রতি কৌতুহলী করে তোলে। এই গাছকে কলকাতা থেকে দেশের অন্যত্র এমনকি দূরদেশেও তারা ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।
এর কয়েক বছর আগে ১৮৩৭ সালে ডিউক অব ডেভনশায়ার কলকাতায় এক বোটানিক্যাল ট্রিপের পরিকল্পনা করেন। তাঁর সে ভ্রমণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ভারত থেকে কিছু গাছপালা সংগ্রহ করা। তাঁর সাথে ছিলেন জনৈক গার্ডেনার জন গিবসন, যিনি ছিলেন প্রখ্যাত গার্ডেনার যোশেফ প্যাক্সটনের ছাত্র। এই ভ্রমণ মিশনে গিবসন কিছুদিন খাসিয়া অঞ্চলে কাটান ও সেখান থেকে রাজ অশোকের দুটি নমুনা ও কিছু অর্কিডের নমুনা সংগ্রহ করেন। অর্কিডগুলোকে তিনি রেকর্ডভূক্ত ও নামকরণ করেন। কথিত যে, গিবসন রাজ অশোকের নমুনা দুটি ইংল্যান্ড নিয়ে যান। তবে পথেই একটি নমুনা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যটি তিনি ইংল্যান্ডের একটি উদ্যানে লাগান।
পরবর্তীকালে ‘Seeds of Fortune’-এর লেখিকা সুই শেফার্ড রাজ অশোক গাছের এক চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা দেন। তিনি লেখেন, ‘‘চ্যাটসওয়ার্থ গার্ডেনে আমহার্স্টিয়া হাউস নির্মাণ করে তার প্রাঙ্গণে একটি রাজ অশোক গাছ লাগানো হয়েছিল। রাজ অশোক গাছটি ছিল খুবই সুদৃশ্য। সেটাই ছিল সমগ্র ইউরোপের মধ্যে থাকা একমাত্র রাজ অশোক গাছ। ছোট্ট সে গাছের পাখির লেজের মতো ঝুলে থাকা নবপল্লব, আহা কি মনোরমই না ছিল গাছটি! ডেভনশায়ার হাউসে ডিউক প্যাক্সটনের সাথে বসে সকালের নাস্তা খাওয়ার সময় তা দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং গাছটির প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত মমতা জন্মে গিয়েছিল।’’
অবশ্য সেই গাছটি নিয়ে তর্কও কিছু কম ছিল না। কেউ কেউ দাবি করেন, ও গাছটি আসলে গিবসনের আনা ও লাগানো গাছটি নয়। গিবসন একটা রাজ অশোক গাছ লাগিয়েছিলেন বটে, তবে সেটিতে কখনও ফুল ফোটেনি, লাগানোর কয়েক বছর পর সেটি মরে যায়। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ‘The Gardener’s Chronicle and Agricultural Gazette’–এর তথ্য অনুসারে সেই রাজ অশোক গাছটি লাগিয়েছিলেন মিস্টার ফয়। কোথা থেকে তিনি কিভাবে সংগ্রহ করে সেটি লাগিয়েছিলেন তা কারও জানা নেই।

১৮৬৪ সালে জর্জ আরনেস্ট বালজার এসছিলেন কলকাতায়। কৌতুহলবশত তিনি কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে রাজ আশোক দর্শনে গিয়েছিলেন। ভুবনখ্যাত রাজ আশোককে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা তার ছিল। কিন্তু কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের মালিরা যখন তাঁকে জানাল যে, রাজ অশোক গাছে ফুল ফোটে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে বীজ সহজে হচ্ছে না। বীজ না হলে তারা চারাও তৈরি করতে পারছে না। তখন তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে যান। নিশ্চয়ই এ গাছে ফুল যখন ফোটে, বীজও হবে। কিন্তু তার উপযুক্ত জলবায়ু বা পরিবেশ কেমন দরকার?
রাজ অশোক এরপর আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠে একটি গল্পের সুবাদে। পলমল গেজেট ১৮৬৬ সালে একজন রাজকুমার ও তার ডাক্তারকে নিয়ে একটি রূপক গল্প প্রকাশ করে। রূপক গল্পের ডাক্তার একটি রাজ আশোক গাছ রোপণ করেন। ডাক্তার সেই গাছটির বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। বছরের পর বছর যায়। কিন্তু গাছটি বড় হয় না। সে গাছে কোনও ফুলও ফোটে না। ডাক্তার রাজকুমারকে মাটি থেকে গাছটি তুলে একটি পাত্রে লাগাতে বলেন ও তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাঁচঘরের ব্যবস্থা করতে বলেন। অবশেষে গাছটিকে আলো করে আগুনের শিখার মতো সেই গাছে ফুল ফুটল। ফুল দেখে সবাই চমৎকৃত হয়ে রাজ অশোকের প্রশংসায় মেতে উঠল। রূপক অর্থে আসলে ওই রাজকুমার ছিলেন ডিউক অব ডেভনশায়ার, ডাক্তার ছিলেন প্যাক্সটন আর গাছটি ভারত থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়ালিচ ও তাঁর বন্ধু ক্রফার্ড। আর কাকতালীয় হলেও সত্য, ইংল্যান্ডে রাজ আশোকের ফুল ফোটার দিনটি ছিল ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে পুরুষ শ্রমিকদের জন্য উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন আনীত সংস্কার বিলটি উত্থাপনের দিন। তাই শ্রমিক ও রাজন্যদের সাথেও রাজ আশোক ইংল্যান্ডে স্মৃতিময় হয়ে আছে। রাজ মর্যাদায় এ দেশেও অভিষিক্ত হয়েছে রাজ আশোক গাছ। রাজা বা রাজ কর্মচারীদের মতোই অন্যান্য গাছের মধ্যে রাজ অশোক সুন্দর, স্বল্প ও স্বতন্ত্র।
বিলাতি ঝাউ
ঝাউগাছ যেন অনাদরে থাকা অবহেলিত এক বুনো গাছ। পশ্চিমবঙ্গের কবি জয়দেব গোস্বামী তাঁর ‘ঝাউ গাছের পাতা’ কবিতায় মিত্রা দিদিকে নিয়ে যেন সেই দীর্ঘশ্বাসই ছেড়েছেন:
‘‘মিত্রা দিদি, তোমাকে নিয়ে কাব্য
লেখেনি কোন পুরুষ কোনদিন।
গলির মোড়ে বাজেনি সম্মিলিত
শীৎকার বখাটে ছেলেদের।’’

ধারণা করা হয় এই বিদেশি গাছ বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশে আসে। বনবিভাগ বিশ শতকে সত্তরের দশকে কক্সবাজার, কুয়াকাটা, নিঝুম দ্বীপ ও পার্কি সমুদ্র সৈকতে ঝাউগাছ লাগায়। এটিকে আগ্রাসী গাছ মনে করেই তার প্রতি কবির মতোই অবহেলা বা অনাদর করা হয়। অনাদরের কারণ, এ গাছ যেখানে জন্মে সেখানে সে আর কোনও গাছকে জন্মাতে দেয় না, শুধু স্বজাতিদের নিয়ে সে দাপটের সাথে সেখানে বেঁচে থাকতে চায়। এ গাছের কোনও অংশই কোনও জীব ও পরিবেশের জন্য মঙ্গলজনক না, এ গাছে কোনও পাখি ফল খেতে আসে না, ঝাউগাছের শিকড় ভূমির উপর দিয়ে বয়ে চলায় সেসব স্থানে বা ঝাউবনের সৈকতের বালুকাবেলায় কচ্ছপরা বালি খুঁড়ে ডিম পাড়তে পারে না, এ গাছের তলায় আর কোনও গাছ জন্মাতে চায় না। ঝাউ গাছের শিকড় মিথোজীবীতা করে ফ্রাংকিয়া নামের আগ্রাসী আগাছার জন্ম দেয়।
তবে ভারতীয় উপমহাদেশে ঝাউগাছ যে আরও আগেই এসেছিল সে প্রমাণ মেলে কবি তরু দত্তের ছোটবেলার সুখময় স্মৃতিকে ঘিরে ‘আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি’ কবিতাটিতে, যার অর্থ:
‘‘এই ঝাউগাছ আমার আত্মার আপনজন;
এর নিচে আমরা খেলা করেছি; যদিও অনেক বছর পার হয়ে গেছে,
আমার প্রিয় সাথী, তীব্র আবেগের সাথে যাকে ভালোবেসেছি,
আমাদের জন্য হলেও, এই গাছটি চিরকাল আমাদের প্রিয় হয়ে থাকুক।’’

ইউরোপ প্রবাসী বাঙালি এই নারী কবি মাত্র ২১ বছর বেঁচেছিলেন, ১৮৭৬ সালে তিনি মারা যান। এ স্বল্পায়ূ জীবনের মধ্যেই তিনি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় লিখে রেখে গিয়েছেন দুর্দান্ত কিছু কবিতা। এ কবিতাটি তাঁর ‘অ্যানসিয়েন্ট ব্যালেড অ্যান্ড লিজেন্ড অব হিন্দুস্তান’ গ্রন্থের শেষে বিবিধ কবিতাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। ঝাউগাছ তাই যতই আগ্রাসী হোক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খাতিরে ও আবেগের টানে সে অনেক লেখকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।
তাই কক্সবাজারের সৈকত ও মেরিন ড্রাইভ রোড দিয়ে গেলে সাগরপাড়ের ঝাউবন যে কোনও পর্যটককে মুগ্ধ করে, ঝাউবনে বেড়িয়ে যাওয়া মানুষদের স্মৃতিকাতরতায় ভোগায়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে সাগরের পানি বেড়ে যাওয়ায় এখন উপকূল ভেঙ্গে সেসব ঝাউ বন ধ্বংসের মুখে পড়েছে। ভরা পূর্ণিমায় ২০২৪ সালের জুলাইয়ের শেষে কক্সবাজারের সৈকত ভেঙ্গে অন্তত তিন হাজারের বেশি ঝাউগাছ উপড়ে পড়েছে। এতে সৈকতের সৌন্দর্যহানি হয়েছে। এতে সাগর থেকে উঠে আসা প্রবল নোনা বাতাসে ঝাউ বনের ঝিরিঝিরি পাতায় তোলা বায়বীয় মূর্চ্ছনা হয়ত আর সেভাবে অনেক দিন শোনা যাবে না। ঝাউ পাতায় বয়ে যাওয়া হাওয়ার শনশন শব্দ যেন ঘুমের আবেশ তৈরি করে। সে শব্দের অনুভুতি থেকে ঢাকাবাসী বঞ্চিত।
বিলাতি ঝাউ আর পাইন গাছ নিয়ে বিভ্রান্তির যেন শেষ নেই। আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি গাছকে একই রকম মনে হয়। অনেকে পাইন গাছকেও ঝাউ গাছ বলে ডাকেন। দুটি গাছকে আলাদাভাবে দেখলে তেমনটি মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ দুটি গাছকে পাশাপাশি দেখলে তখন দুটি গাছের পার্থক্য ধরা পড়ে। ইংরেজিতে বিলাতি ঝাউকে কেউ কেউ আবার অস্ট্রেলীয় পাইন বলে ডাকাতেও এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।
ঝাউ গাছের আদিনিবাস অস্ট্রেলিয়া, নিউ গিনি, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও ভারত। বিলাতি ঝাউকে সংক্ষেপে ঝাউ নামেও ডাকা হয়। ইংরেজি নাম ‘কোস্টাল শিওক’ বা ‘বিচ শিওক’। পাতাগুলোর গোছা ঘোড়ার লেজের আগার মতো দেখতে। এজন্য এর আর একটি ইংরেজি নাম ‘হর্সটেইল’। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ‘ক্যাসুরিনা ইকুইসেটিফোলিয়া’ (Casuarina equisetifolia) ও গোত্র ‘ক্যাসুরানিয়েসী’ (Casuraniaceae)। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) বিলাতি ঝাউগাছের এই প্রজাতিগত নামকরণ করেন। ক্যাসুরিনা নামটি অস্ট্রেলিয়ার এক ধরনের পাখি ক্যাসুরিয়াসের নাম থেকে উদ্ভুত যার অর্থ সেই পাখির পালকের মতো পাতা। ‘ইকুইসেটিফোলিয়া’ এসেছে লাতিন শব্দ ‘ইকুইসেটিয়াম’ থেকে যার অর্থ ঘোড়ার চুল। পত্রগুচ্ছ দেখতে অনেকটা ঘোড়ার চুলের মতো।
এদেশে কয়েক প্রজাতির ঝাউগাছ থাকলেও ক্যাসুরিনা ইকুইসেটিফোলিয়া প্রজাতির ঝাউ গাছই ‘বিলাতি ঝাউ’ বা ‘ঝাউ’ নামে পরিচিত। ক্যাসুরিনা গণের আর এক প্রজাতির ঝাউগাছ এদেশে আছে যার নাম ‘নীলঝাউ’। ট্যামারিক্স গণের ঝাউগাছগুলো হলো ‘লালঝাউ’, ‘এরিকা-ঝাউ’, ‘গোলা-ঝাউ’, ‘নোনা-ঝাউ’ ও ‘তরুপ-ঝাউ’।

বিলাতি ঝাউ একটি চিরসবুজ বহুবর্ষজীবী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এ গাছ লম্বা আকারের বৃক্ষ। গাছ ৬-৩৫ মিটার লম্বা হয়। তরুণ গাছ পিরামিড আকৃতির হলেও বয়স্ক গাছের ডালপালা ছড়ানো ও এলোমেলো। ঝাউ গাছের শিকড় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চয় করে তা মাটিতে যোগ করতে পারে। গাছের বাকল মসৃণ ও ধূসর, বয়স্ক গাছের বাকল খোসাযুক্ত ও শক্ত। কাঠ শক্ত হলেও তা ভঙ্গুর হওয়ায় জ্বালানি ছাড়া আর তেমন কোনও কাজে লাগে না। শাখা আনত ও দোলায়মান। ডাল ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা সংকুচিত ও ক্ষুদ্র হয়ে আইশের মতো গঠন তৈরি করে। ফুল একলিঙ্গী। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে ফোটে। স্পাইক মঞ্জরিতে পুরুষ ফুল ফোটে। যদিও একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল মঞ্জরিতে ফোটে, তবু সেগুলোর মঞ্জরি আলাদা। ‘কোন’ বা ‘মোচা’ আকৃতির মঞ্জরিতে স্ত্রী ফুলগুলো আঁটোসাঁটো হয়ে পাতার কোলে ডালের উপর অবস্থান করে। বাতাসের দ্বারা পরাগায়ণ ঘটে। পরাগায়ণের পর পুরুষ ফুলগুলো ঝরে যায় ও স্ত্রী মঞ্জরি ফলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মের শুরুতে ও হেমন্তের শেষে, বছরে এই দুবার ফুল ফোটে। ফল আসলে বহু ছোট ছোট কৌণিক ফলকণার সমষ্টি, আকৃতি গোলাকার, ছাই ধূসর রঙের, শুকনো ফল বাদামি। বীজ অত্যন্ত হালকা ও বাদামি। ফল কাষ্ঠল, প্রথমে সবুজ থাকলেও পরে তা বাদামি হয়ে যায়। পরিপক্ব হলে ফলগুচ্ছ ফেটে যায় ও তা থেকে ক্ষুদ্র বীজ ঝরে পড়ে। বীজ থেকে চারা হয়। উদ্যান ও পথতরু হিসেবে সড়কের পাশে বিলাতি ঝাউগাছ লাগানো যায়। তবে এ গাছের সুফল পাওয়া যায় বালিময় জমি ও সৈকতে লাগিয়ে ভাঙ্গন ও ভূমিক্ষয় ঠেকানোর জন্য।
ঢাকা শহরে মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের প্রবেশের পর গোলাপ বাগান পর্যন্ত প্রধান সড়কের দুপাশে সারি করে লাগানো ঝাউগাছগুলো যে কোনও দর্শনার্থীর মন জুড়ায়। সেসব ঝাউগাছের গোড়ায় অধিমূল চারদিকে ডানার মতো বিস্তৃত। রমনা উদ্যানের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম কোণে কয়েকটা বড় ও প্রাচীন ঝাউগাছ আছে। নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ঢাকা শহরে ষাটের দশকে তাঁর দেখা বিলাতি ঝাউ সম্পর্কে লিখেছেন: ‘‘ঢাকায় এ গাছ দুষ্প্রাপ্য। মিন্টো রোড এবং হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির কাছে যে দু একটি বিলাতি ঝাউ রয়েছে তাদের অবস্থান যেমন পথিকের চোখে পড়ার মতো নয়, তেমনি তারা স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল, এলোমেলো। এ গাছের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, বিশেষত নিদ্রাকর্ষী স্বনন ঢাকাবাসীর অজানাই রয়ে গেল।’’

বাঁশপাতি
ঢাকা শহরে অরণ্যের মহাবিপন্ন বাঁশপাতি গাছের দেখা পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। সে গাছের দেখা পেলাম ঢাকার দুটি উদ্যানে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে। বাঁশপাতি গাছ উষ্ণমণ্ডলীয় এবং উপউষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের হালকা জলজ বনে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০ থেকে ১৬০০ মিটার উচ্চতায় জন্মায়। এই নগ্নবীজী উদ্ভিদটি ভারত, নেপাল, চীন, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন, পাপুয়া নিউ গিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি প্রভৃতি দেশে জন্মে।
বাঁশপাতি গাছ বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অরণ্যে জন্মে। বর্তমানে এটি একটি দুষ্প্রাপ্য ও মহাবিপন্ন গাছ। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা আইইউসিএন ২০১০ সালে এ গাছকে লাল তালিকাভুক্ত করেছে। ২০১৭ সালে আরণ্যক ফাউন্ডেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৭ সালে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন প্রজাতির বৃক্ষ পরিচিতি গ্রন্থের তথ্যমতে, বর্তমানে সারা দেশে প্রাকৃতিকভাবে ও রোপিত বাঁশপাতি গাছের মোট সংখ্যা ১১১টি। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো গাছ রয়েছে মাত্র ১২টি এবং বাকি ৯৯টি লাগানো গাছ, যা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তফসিল-৪ অনুযায়ী এ প্রজাতিটি সংরক্ষিত।

ঢাকা শহরেও বাঁশপাতি গাছ বিরল। বলধা উদ্যানের সিবিলি অংশে একটি বড় বাঁশপাতি গাছ আছে। অন্যটি আছে মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরিকালচার অফিস ঘরের সামনেও রয়েছে একটি বাঁশপাতি গাছ। ফার্মগেটে কৃষি খামার সড়কের পাশে খামারবাড়ির প্রবেশপথে একটি বাঁশপাতি গাছ লাগানো হয়েছে, সেটি বেশ ছোট। বছর তিনেক আগে ঢাকা শহরের বাইরে সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গলে অবশ্য আর একটি বাঁশপাতি দেখেছিলাম। আর একটি বাঁশপাতি গাছ দেখেছি মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারে অফিস ভবনের সামনে। এ দুটি গাছই বয়সে তরুণ। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ উদ্যানে ও মৌলভীবাজারে লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনেও আছে বাঁশপাতি গাছ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রিতে বেশ কয়েকটি বাঁশপাতা গাছ রয়েছে। একসময় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বাঁশপাতাগাছ চট্টগ্রাম, রাঙামাটির পাবলাখালী, বাঘাইছড়ির কাসালং ও মাসালং, কক্সবাজারের উখিয়া এবং শ্রীমঙ্গলের লাউয়াছড়া বনাঞ্চলে পাওয়া যেত।
গাছটি দেখতে অনেকটা পাইন গাছের মতো বলে বাঁশপাতি বা বাঁশপাতা গাছের ইংরেজি নাম ‘ব্রাউন পাইন’। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম পডোকারপাস নেরিফোলিয়াস (Podocarpus neriifolius) ও গোত্র পডোকারপাসী (Podocarpaceae) পরিবারের একটি উদ্ভিদ। বাঁশপাতি একটি চিরসবুজ নগ্নবীজী বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ। বাঁশপাতি মূলত প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো দেশি প্রজাতির নগ্নবীজী উদ্ভিদের একমাত্র নরম কাঠের কনিফার বা মোচা আকৃতির ফলের নরম পেনসিল কাঠের গাছ। বাঁশপাতা গাছের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার এবং বেড় ২ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কাঠের রং ধূসর হলুদ বা হালকা বাদামি, নরম ও মসৃণ, সুন্দর পালিশ ওঠে। এর কাঠ পেনসিল, স্কেল, ছবি বাঁধাই করার ফ্রেম, হারমোনিয়াম, খেলনা, শোপিস ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

বাঁশপাতি গাছের ডাল ও পাতা ঝুলন্ত বা দোলায়মান। এই গাছের পাতা বাঁশপাতার মতো লম্বাটে, সাধারণত ১২-২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা ও ৩-৪ সেন্টিমিটার চওড়া, রং গাঢ় বা কালচে সবুজ, বোঁটাবিহীন। গোছাধরা পাতাগুলো দেখতে বাঁশের পাতার মতো বলেই এ গাছের এরূপ নাম। পাতার রস বাতের ব্যথায় উপকারী। পাতার রস বাত, গিঁটবাত এবং ঠাণ্ডাজনিত রোগে কাজে লাগে। বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যানে শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসেবে এ গাছ লাগানো হয়। গাছ ছেঁটে সুন্দর গড়নে রাখা যায়। কাটার পর গুড়ি থেকে পাতা গজায়।
এ গাছে সত্যিকারের কোনও ফুল-ফল হয় না, বীজ নগ্নভাবে থাকে। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে এদের ভিন্ন ভিন্ন গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল ফোটে। কখনও কখনও বছরে দুবারও ফুল ফুটতে দেখা যায়। বাঁশপাতার নগ্নবীজগুলো লম্বায় ৩ থেকে ৪ সেন্টিমিটার এবং দেখতে অনেকটা কাজুবাদামের ফলের মতো। ফলের মাংসল স্ফীত অংশ খাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বীজগুলো পরিপক্ব হয়ে আসে। তখন দেখতে উজ্জ্বল কমলা-লাল থেকে কালো রঙের হয়। প্রতি কেজি ফলে বীজের সংখ্যা ৪৫০ থেকে ৫০০টি। সাধারণ তাপমাত্রায় পাঁচ থেকে সাত দিন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বনাঞ্চলে সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে এ গাছের চারা জন্মে ও বংশবৃদ্ধি ঘটে। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তা ব্যাহত হতে পারে।
ধূপগাছ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘উৎসর্গ’ কাব্যগ্রন্থে ‘ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে’ কবিতায় লিখেছেন:
‘‘ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।’’
কবিতার প্রথম পংক্তিতেই ধূপের অভিপ্রায় ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট, মানে ধূপ হলো সুগন্ধ ধোঁয়া উৎপাদী গাছ। এজন্য এ গাছের আর এক নাম নাম ‘ধুনা-রাতা’। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এক সময় সন্ধ্যেবেলা ধূপের ধোঁয়া দেওয়ার প্রচলন ছিল। গোয়ালেও নারকেল ছিবড়ায় আগুন জ্বেলে তার মধ্যে ধূপ ছিটিয়ে সুগন্ধি ধোঁয়া তৈরি করা হতো। এতে মশারা পালাত। ঘরের অন্যান্য কীটদেরও ধুপের ধোঁয়া বিতাড়িত করত। এসব কাজে যে ধূপ ব্যবহার করা হতো সেটা আসলে ধূপ গাছের শুকনো কষ বা আঠা। গাছ থেকে সে আঠা সংগ্রহ করে শুকিয়ে ফিটকিরির মতো তা বাজারজাত করা হয়। এক সময় এ দেশে তাই ধূপ গাছের যেমন কদর ছিল তেমনি বন জঙ্গলে তার গাছও ছিল। এখন ধূপের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে, এর জায়গা দখল করেছে ধূপকাঠি বা আগরবাতি। ধূপগাছ এ দেশ থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

গ্রীষ্মের এক সকালে ‘বৃক্ষকথা’ ফেইসবুক গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে দলেবলে রমনা উদ্যানে গাছপালা দেখে বেড়াচ্ছি। গাছ দেখা শেষ হলে বেনুবর্ণা বললেন, অনেক গাছই তো দেখলাম, চলেন এবার একটা দুর্লভ গাছ দেখে আসি। কি গাছ? জিজ্ঞেস করতেই বললেন, ধূপগাছ। গাছটা সত্যিই সহজে চোখে পড়ে না, ঢাকা শহরে তো নয়ই, অরণ্যের গাছ। তাই তাঁর কথায় বেশ কৌতুহল বোধ করলাম। কোথায় আছে গাছটা? বেনুবর্ণা বললেন, রমনার কোথায় কোন গাছটা আছে তা মোটামুটি আমার মুখস্ত। অতএব, আমার সাথে চলুন। গেলাম তার পিছুপিছু কয়েকজন। কিন্তু কোথায় সে ধূপগাছ? অবশেষে দেখা মিলল খিরনি গাছের কাছে একটা লম্বা গাছের, থামের মতো সোজা সরল কাণ্ড, একেবারে মাথার দিকে কয়েকটা ডালপালা ছাতার মতো ছড়ানো। বেনুবর্ণা বললেন, এটাই ধূপগাছ। তাকিয়ে ভালো করে গাছ ও পাতাগুলো দেখার চেষ্টা করলাম, ফুল বা ফল কি ধরেছে? অনেক উঁচুতে ডালপালা ও পাতা থাকায় খুব ভালোভাবে তা দেখা সম্ভব হলো না। পাতাগুলোকে বরং গর্জন পাতার মতোই মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নিয়ে তাই গাছটিকে নিশ্চিতভাবে ধূপগাছ বলে আমরা শনাক্ত করতে পারলাম না।
মাস দুয়েক পর বলধা গার্ডেনের সাইকি অংশের ভেতরে সেরূপ আর একটি গাছের দেখা পেলাম। বিদ্যুতের খুঁটির মতো সোজা হয়ে গাছটা যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। কাণ্ডের গোড়া থেকে অনেক দূর পর্যন্ত কোনও ডালপালা নেই। নারকেল গাছের মতো মাথায় কয়েকটা ডালপালা ও পাতা। মাথায় কাণ্ড থেকে চারদিকে ছড়ানো ডালপালায় ঘন হয়ে রয়েছে পাতাগুলো। গাছের গোড়া গোলাকার অধিমূলযুক্ত, কাণ্ডের বাকল সবুজাভ ধূসর। দেখতে রমনার সেই গাছটার মতোই। নামফলক দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল যে রমনা ও বলধা গার্ডেনের গাছ দুটোই ধূপগাছ।

ধূপগাছ মাঝারি আকারের চিরসবুজ বৃক্ষ। এ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ক্যানারিয়াম রেজিনিফেরাম (Canarium resiniferum) পরিবার বার্সেরেসী (Burseraceae)। রেজিন মানে আঠা বা গদ। এ প্রজাতিটি ১৮৯৩ সালে বর্ণিত হয়েছিল। গাছ অনেকটা চোঙ্গার মতো লম্বা। বাকল ধূসর, মসৃণ ও পুরু। পাতা যৌগিক তবে সেগুলো বেশ অনিয়ত। অনুপত্র অবডিম্বাকার বা লম্বাটে। একটি পাতায় ৩-১৩টি অনুপত্র থাকে। পাতা চকচকে সবুজ, কিন্তু নিচের পিঠ হালকা পশমযুক্ত ও খসখসে। গাছে ক্ষত করলে সেখান থেকে এক ধরনের আঠা বের হয়। এই আঠা খুব সুগন্ধযুক্ত। আঠা শুকিয়ে ধূপ তৈরি করা হয়।
ধূপ গাছের কক্ষ থেকে ফুল হয়, ফুল ফোটে ও ফল ধরে জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা ছড়ায় ফুল ফোটে, ফুল পেয়ালাকার, ঘন মরচে রঙের কোমল রোমশ পাঁপড়ি, বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি হয়। বলধা গার্ডেন, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্যে ধূপ গাছ আছে। ধূপগাছের কাঠ থেকে তক্তা, চায়ের বাক্স তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের ২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের তফসিল-৪ অনুযায়ী এ প্রজাতির গাছ সংরক্ষিত উদ্ভিদ। অর্থাৎ এ গাছ যেখানে আছে সেখানে কেউ সে গাছের কোনও ক্ষতিসাধন করলে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।
কুম্ভি
প্রায় দশ বারো বছর আগে বোশেখের এক ভোরবেলায় নীলফামারীর সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার দুই পাশে দেখতে পেয়েছিলাম কয়েকটা কুম্ভি গাছ। গাছগুলো বেশ বুড়ো হয়েছে। ন্যাড়া মাথা, প্রায় পত্রহীন চার পাঁচটি গাছ। কচি কিছু তামাটে পাতা কয়লা রং পোড়া পোড়া ডাল ফুঁড়ে সবে বেরুচ্ছে। কিন্তু শাখা-প্রশাখা জুড়ে তখন তার থোকা থোকা ফুলের তাণ্ডব। না, তবে তা কেশহীন মাথায় ফুল গুজলে যেমন অসুন্দর দেখায়, তেমন নয়। বরং নিষ্পত্র গাছের শাখায় শাখায় যেন ঋতুরাজ বসন্ত লাগিয়ে গেছে অন্য রঙ। পাতার ভীড়ে হয়ত তা দেখাই যেত না। ২০২৪ সালে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুপাশের সেসব কুম্ভি গাছগুলোকে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোথায় সেসব গাছ? রাস্তা চওড়া হয়েছে, ধারণা করলাম সেই সুবাদে হয়ত বুড়ো কুম্ভি গাছগুলোকেও কেটে ফেলা হয়েছে। এভাবে দেশের বনজঙ্গল থেকেও গাছটির ব্যবহার না থাকায় সেসব গাছ হয়ত জ্বালানি বা আসবাবপত্রের কাঠ হিসেবে উজাড় হয়ে গেছে।

কুম্ভি গাছের একসময় এদেশে খুব কদর ছিল। কেননা, এর পাতা দিয়ে বিড়ি বানানো হতো, সেজন্য এর আর এক নাম ‘বিড়িপাতা’ বা ‘বিড্ডিপাতা’ গাছ। এখন আর এর পাতা দিয়ে বিড়ি বানানো হয় না, বিড়ি বানানো হয় কাগজ দিয়ে। সেজন্য কুম্ভিও বোধ হয় আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই কুম্ভিকে বাংলাদেশ সরকার সংরক্ষিত উদ্ভিদ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ঢাকা শহরে কয়েকটা বয়স্ক কুম্ভি গাছ সংরক্ষিত অবস্থায় টিকে আছে মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে।
কুম্ভি গাছের ইংরেজি নাম ‘Slow match tree’, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ‘Careya arborea’, আর গোত্র নাম ‘Lecythidaceae’। পাতাঝরা স্বভাবের এ গাছটি বৃহৎ বৃক্ষ প্রকৃতির। অনেক ডালপালা হয়। স্থানীয় লোকেরা কুম্ভিকে ‘টেন্ডু’ নামে চেনেন। কুম্ভি গাছের বাকল ধুসর লাল কালচে; ভিতরের দিকে আঁশ আছে। কাঠের রং রক্তাভ বাদামি, টেকসই ও ভাল পালিশ করা যায়। গাছের বাকল দিয়ে দড়ি তৈরি করা যায় এবং চামড়া রং করা যায়। কুম্ভি গাছের পাতা শীতে ঝরে যায় ও বসন্তে গজাতে শুরু করে। পাতা গজানোর আগেই কুঁড়ি ও ফুল ফোটে। ফুল দেখতে অনেকটা ‘রেইন ট্রি’ বা মেঘ শিরীষের মতো, তবে মেঘ শিরীষের চেয়ে কুম্ভির ফুল বড় ও সুদর্শন। ফুলের গড়ন ব্রাশের মতো, সাদা, গোড়ার দিকের কেশরগুলো লাল। দেখতে খুব সুন্দর, ফুল ফোটে থোকা ধরে, ফুল ফোটার সময় চৈত্র-বৈশাখ। পাতার আকৃতি অনেকটা রূপ চাঁদা মাছের মতো, বড়। ফোটা ফুল সকাল বেলায় ঝপ ঝপ করে প্রায় এক সাথেই গাছ থেকে ঝরে পড়ে। গাছের তলায় তখন রচিত হয় সে এক অন্য দৃশ্য। ফল বড়, দেখতে খানিকটা বেলের মতো, তবে ডিম্বাকার বা লম্বাটে গোল, ফল পাকলে শাঁস নরম হয়। ফলের রং হালকা সবুজ। গাছের বৃদ্ধি খুব ধীর।
এক সময় টেন্ডু পাতার বিড়ির খুব চল ছিল। বিড়ি তৈরির জন্য কুম্ভি পাতা ছিল অনন্য প্রাকৃতিক উপাদান। এখন বিড়ি তৈরি হয় কাগজ দিয়ে। তাই টেন্ডু পাতার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। কেউ আর এখন কুম্ভি গাছ লাগায় না। সেজন্য এ দেশ থেকে কুম্ভি গাছও খুব শিগগিরই চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। বিড়ি না হোক, ভালো আসবাবপত্র তো কুম্ভি থেকে তৈরি হয়। অন্তত সেজন্য হলেও যদি কুম্ভিকে নগরবনে, উদ্যানে, বেড়িবাঁধে এমনকি মহাসড়কের দু’ধারে ঠাঁই দেওয়া যায়। এতে একটি প্রজাতির উদ্ভিদ লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।
বৃক্ষ সংরক্ষণে ‘চিপকো’ আন্দোলন
তিনশো বছরেরও বেশি আগে ভারতের রাজস্থানে গাছ কাটা নিয়ে এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছিল। কিছু রাজকর্মচারী যখন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পবিত্র খিজরি গাছ কাটার জন্য তৈরি, তখন ‘বিশনয়’ সম্প্রদায়ের তিন শতাধিক নারী-পুরুষ অমৃতা দেবী নামের এক সাহসী নারীর নেতৃত্বে সে বৃক্ষগুলোকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়ান। প্রতিটি গাছকে তাঁরা আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে চেপে ধরে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু অনুরোধ ও হুকুম সত্ত্বেও যখন তাঁরা একইভাবে গাছকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন তাঁদের ওপর নেমে আসে কাঠুরেদের কুঠারের আঘাত। তাঁদের আত্মাহুতির মাধ্যমেই সূচিত হয় বৃক্ষ সংরক্ষণের ‘চিপকো’ আন্দোলন। গাছগুলোকে তাঁরা চেপে ধরে রেখেছিলেন বলেই তাকে বলা হয় ‘চিপকো’। চিপকো আন্দোলন এখন আর শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে যার নেতৃত্বে রয়েছেন নারীরা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, প্রতিদিন এ দেশে শত শত গাছ কাটা হলেও সেগুলো রক্ষার কেউ নেই। অন্তত বিপন্ন উদ্ভিদগুলোকে রক্ষায় আমাদের সচেতন হওয়া ও প্রতিরোধ করা উচিত।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: kbdmrityun@gmail.com