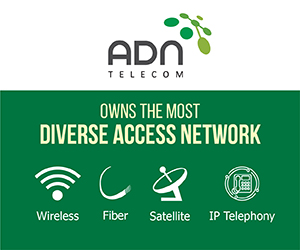পূর্ব ভারতে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ৩০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়। একে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পাশাপাশি ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনা হিসেবে দেখা হয়।
বিশ্বের কোথাও ওই দুর্ভিক্ষে মৃতদের স্মরণে নেই কোনও স্মৃতিস্তম্ভ, জাদুঘর বা ফলক। তবে সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের স্মৃতি নিয়ে আজও কিছু মানুষ বেঁচে আছেন।
‘তাড়া করে ফেরা ক্ষুধা’
“অনেক মানুষ একটু ভাতের জন্য তাদের সন্তানদের বিক্রি করেছিল। অনেক স্ত্রী ও তরুণীরা পরিচিত-অপরিচিত পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল।”
কথাগুলো বলছিলেন সেই দুর্ভিক্ষের জীবন্ত সাক্ষী বিজয়কৃষ্ণ ত্রিপাঠী। নিজের বয়স কত, তা আর আজ ঠিক করে বলতে পারেন না তিনি। তবে ভোটার কার্ড বলছে তার বয়স ১১২।
বয়োবৃদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলছিলেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মেদিনিপুর জেলায় তার বেড়ে ওঠার কথা। ১৯৪২ সালের গ্রীস্মে চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ার কথা।
সেই বছরের অক্টোবরেই আঘাত হানে প্রলয়ংকরী এক ঘূর্নিঝড়। বিজয়কৃষ্ণের বাড়ির চাল উড়ে যায়। মাঠের ধান নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ওই ধানের ওপরই ছিল তার গোটা পরিবারের ভরসা।

তার ভাষ্যে, “ক্ষুধা আমাদের তাড়া করছিল। ক্ষুধা আর মহামারী। সব বয়সী মানুষ মরতে শুরু করে। সবাই আধপেটা। খেতে না পেয়ে গ্রামের বহু মানুষ মারা গেল। খাবারের সন্ধানে শুরু হলো লুটপাট।”
ত্রাণ কিছু এসেছিল, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।
বিজয়কৃষ্ণের বারান্দায় বসে তার কথা শুনছিলেন তারই পরিবারের চার প্রজন্ম। তাদের সঙ্গে ছিলেন শৈলেন সরকার। তিনি গত কয়েক বছর ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধ্বংসাত্মক দুর্ভিক্ষে বেঁচে থাকা মানুষদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করছেন।
৭২ বছর বয়সী শৈলেন সরকার আজও যেন যুবক। তার প্রানখোলা হাসির কারণে বিজয়কৃষ্ণের মতো মানুষও তার কাছে মন খুলে কথা বলেন। আবহাওয়া যেমনই হোক, পায়ে স্যান্ডেল, পিঠে ব্যাগ আর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। সাবেকি কায়দায় তিনি আজও কাগজ আর কলমেই ভরসা রাখেন অভিজ্ঞতা টুকে রাখতে।
শৈশবে পারিবারিক একটি ফটো অ্যালবামের মাধ্যমে প্রথম শৈলেন বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানতে পারেন। অ্যালবামটিতে থাকা শীর্ণকায় মানুষগুলোর ছবি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সেই থেকেই বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে তার মধ্যে জিজ্ঞাসার বীজ বপন হয়।
অ্যালবামের ওই ছবিগুলো তুলেছিলেন শৈলেনের বাবা। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি স্থানীয় একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হয়ে ত্রাণ বিতরণের কাজ করতেন।
নিজের বাবা সম্পর্কে শৈলেন বলেন, “আমার বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র মানুষ। শৈশবে আমি তার চোখে ক্ষুধার্তের ভয় দেখেছিলাম।”
২০১৩ সালে শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর নেন শৈলেন। এরপরই মূলত তার বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। মেদিনিপুরের রাস্তায় হাটতে গিয়ে ৮৬ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপচারিতা তার চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়।
বিজয়কৃষ্ণের মতো শ্রীপতিচরণ সামন্তও মনে রেখেছেন ধ্বংসাত্মক সেই ঘূর্ণিঝড়ের কথা। সবকিছু মিলিয়ে তখন জীবন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। চালের দাম ক্রমশ বাড়ছিল। ১৯৪২ সালের অক্টোবরে দিনে মাত্র একবার ভাত খেয়ে টিকে ছিলেন তিনি।

ঘূর্ণিঝড়ের পর চালের দাম আরও বেড়ে যায়। বাজারে যতটুকু চাল ছিল তাও ব্যবসায়িরা চড়ামূল্যে কিনে নিয়েছিলেন।
শ্রীপতিচরণ শৈলেনকে বলেন, “কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের গ্রামে চাল শেষ হয়ে গেল। মানুষ কিছুদিনের জন্য সঞ্চিত খাদ্য মজুত থেকে চললো। কিন্তু এক পর্যায়ে চাল কিনতে মানুষ তাদের জমিও বিক্রি করতে শুরু করে।”
ঘূর্ণিঝড়ের পর শ্রীপতিচরনের ঘরে যে চাল মজুদ ছিল, তা দিয়ে কয়েকদিন মাত্র চলেছিল। এরপর শুরু হয় হাহাকার।
অগুনতি মানুষের মতো শ্রীপতিচরণও গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয়ের আশায় গিয়েছিলেন। তিনি যান শহর কলকাতায়। তার ভাগ্য আরও অনেকের চেয়ে ভালো ছিল। এক পরিচিত পরিবারে আশ্রয় পান। বেঁচে যান তিনি।
কিন্তু অনেকের ভাগ্যে তা ঘটেনি। তারা রাস্তায়, ডাস্টবিনের পাশে, ফুটপাতে পরে গিয়ে মারা গেলেন। তারা ভেবেছিলেন কলকাতায় গেলে সাহায্য মিলবে। অথচ সেই শহরই তাদের কাছে অপরিচিত হয়ে যায়। তাদের ঠাই হয়নি কোথাও।
দুর্ভাগ্য
কেন ওই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এর কারণ অনেক ও জটিল। আজও এনিয়ে বিস্তৃত পরিসরে বিতর্ক রয়েছে।
১৯৪২ সালে বাংলায় ধানের সরবরাহে তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।
বাংলার সীমান্তবর্তী তৎকালীন বার্মায় (বর্তমান মিয়ানমার) ১৯৪২ সালের শুরুতেই আক্রমণ করে জাপান। ফলে সেখান থেকে ধান আমদানি হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়।
তখন বাংলা যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতার সামনে দাড়িয়ে। যুদ্ধকালীন শিল্প কারখানায় লক্ষাধিক মিত্রবাহিনীর সৈন্য ও কর্মীদের আগমনে কলকাতায় চাপ বাড়ে। ধানের চাহিদাও বাড়ে। যুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বি হয়ে যায়। ফলে লাখ লাখ মানুষের জন্য ধানের দাম হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়।

এদিকে জাপানিদের পূর্ব ভারতে হামলার আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার ‘বাতিল’ নীতি গ্রহণ করে। এর অর্থ ছিল বাংলার ডেল্টা অঞ্চলের গ্রাম ও শহরগুলি থেকে অতিরিক্ত ধান ও নৌকা জব্দ করা। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল অগ্রসর বাহিনীকে খাদ্য ও পরিবহন ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখা। কিন্তু এতে দুর্বল অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। জিনিসপত্রের দাম আরও বেড়ে যায়। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য, কখনও লাভের আশায়, মানুষ গোপনে ধান মজুত করে রাখে।
সবকিছুর বাইরে ১৯৪২ সালের অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড়ে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর রোগে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয় অবশিষ্ট ফসলের বেশিরভাগ।
এই মানবিক দুর্যোগের জন্য কে দায়ী, তা নিয়ে এখনও তর্ক-বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে যুদ্ধের চাপের মধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এই বিপদ সম্পর্কে জেনেও ভারতীয়দের সাহায্যে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।
১৯৪৩ সালের শেষে নতুন ভাইসরয়, ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়েভেলের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু ততদিনে অনেক মানুষ মারা গেছে।
‘স্মৃতির জীবন্ত জাদুঘর’
কারণ ও দায়িত্বের বিতর্কের আড়ালে অনেক সময় হারিয়ে যায় বেঁচে থাকা মানুষের গল্প।
শৈলেন এখন পর্যন্ত ৬০ এর বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তারা ছিলেন ‘অশিক্ষিত’। তারা দুর্ভিক্ষের কথা খুব কমই বলেছিলেন। তাদের পরিবারের সদস্যরাও এবিষয়ে তাদের কাছে কখনও প্রশ্ন করেনি।
বেঁচে থাকা মানুষদের সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য কোন আর্কাইভ নেই। সাইলেন বিশ্বাস করেন, সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ও দুর্বল মানুষ হওয়ায় তাদের গল্পগুলো উপেক্ষিত।
তিনি বলেন, “সবাই যেন অপেক্ষায় ছিল। কেউ যদি তাদের কথা শুনত।”
শতবছর বয়সে শৈলেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নিরতন বেওয়ার। তিনি সন্তানদের লালনপালনের জন্য মায়েদের তখন অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করার কথা বর্ণনা করেছিলেন।
নিরতন বলছিলেন, “মায়েদের বুকে ছিল না এক ফোঁটা দুধ। কোনও মাংস নেই, শরীর যেন হাড়ের খাঁচা। অনেক শিশু জন্মের পরেই মারা যেত, তাদের মায়েরাও। সুস্থ হয়ে জন্ম নেওয়া অনেক শিশুও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কম বয়সেই মারা যেত। তখন অনেক নারী আত্মহত্যা করেছিলেন।”
শৈলেনকে নিরতন আরও বলেছিলেন, “কিছু স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যেত। কারণ তাদের খাবার দিতে পারতো না স্বামী। তখন লোকজন এসব নিয়ে কোনও কলঙ্ক দিত না। পেটে যখন ভাত নেই, কেউ খাওয়াতে পারে না, তখন কেউ আপনাকে বিচার করবে কেন?”
দুর্ভিক্ষ থেকে লাভবান হওয়া মানুষদের সঙ্গেও কথা বলেছেন শৈলেন। একজন ব্যক্তিতো তার কাছে স্বীকারই করেছেন যে, তিনি চাল, ডাল বা সামান্য অর্থের বিনিময়ে অনেক জমি কিনে নিয়েছিলেন। তিনি আরও জানান, একটি পরিবার উত্তরাধিকারী ছাড়াই মারা যাওয়ায় তার জমিজমা তিনি নিজের করে নিয়েছেন।

বাঙালি-আমেরিকান লেখক কুশানভ চৌধুরী। তিনি দুর্ভিক্ষে বেঁচে থাকা কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করতে শৈলেনের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন একবার।
তিনি বলেন, “তাদের খুঁজতে আমাদের ঘুরতে হয়নি। তারা লুকিয়েও ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সব গ্রামে গ্রামে তারা আছেন জীবন্ত সাক্ষী হয়ে। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলার কষ্ট করেনি। এটা আমাকে লজ্জা দিয়েছে।”
দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তৎকালীন ছবি ও স্কেচে।
কুশানভ বলেন, “ক্ষতিগ্রস্তদের বা বেঁচে থাকাদের কণ্ঠে দুর্ভিক্ষের কথা খুব কমই স্মরণ করা হয়েছে। গল্পটি লিখেছেন সেই মানুষেরা যাদের ওপর দুর্ভিক্ষের কোনো প্রভাব পড়েনি। কে গল্প বলে, কে বাস্তবতা তৈরি করে, এটা এক অদ্ভুত বিষয়।”
ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রুতি কাপিলার মতে, ১৯৪০ এর দশক ছিল ভারতের জন্য ‘মৃত্যুর দশক’। এই কারণে দুর্ভিক্ষের শিকাররা সব আলাপের বাইরে চলে গিয়েছিল।
প্রসঙ্গত; ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল।
এক বছর পর ১৯৪৭ সালে দেশকে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ও মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা চলে যায়। স্বাধীনতায় আনন্দ ছিল, কিন্তু বিভাজন ছিল রক্তক্ষয়ী ও মর্মান্তিক। একে অপরের ধর্মের প্রতি ঘৃণা আরও ১০ লাখের বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। নতুন সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিল প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ।
বাংলাকেই ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশে পরিণত হয়।

অধ্যাপক কাপিলা এই সময়কাল সম্পর্কে বলেন, “ধারাবাহিকভাবে যেসব গণমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যে বিরতি খুবই কম। আর এই কারণেই আমার মনে হয়, বাংলা দুর্ভিক্ষ এককভাবে সেই বর্ণনায় নিজস্ব স্থান খুঁজে পেতে হিমশিম খায়।
“যদিও নির্যাতিতদের কণ্ঠস্বর তাদের নিজস্ব ভাষায় ব্যাপকভাবে শোনা যায়নি, তবুও অনেক ভারতীয় মনে করেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকার।”
আশি বছর পার হয়ে গেলেও, কেবল হাতেগোনা কয়েকজন আজও বেঁচে আছেন। শৈলেন কথা বলতে গিয়েছিলেন ৯১ বছর বয়সী একজন ব্যক্তির সঙ্গে। তার নাম ছিল অনঙ্গমোহন দাস। কেন তিনি এসেছেন, তা শোনার পর সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো এবং তিনি বললেন, “এতো দেরিতে কেন এলে?”
কিন্তু শৈলেন যে কয়েক ডজন ঘটনা সংগ্রহ করেছেন তা লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ও আরও কয়েক লাখ মানুষের জীবন বদলে দেওয়া ঘটনার একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ মাত্র।
তাইতো শৈলনকে বলতে হয়, “যখন আমরা আমাদের ইতিহাস ভুলে যাই, তখন আমরা আমাদের সবকিছুই ভুলে যাই। বাংলার দুর্ভিক্ষের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।”
তথ্যসূত্র : বিবিসি