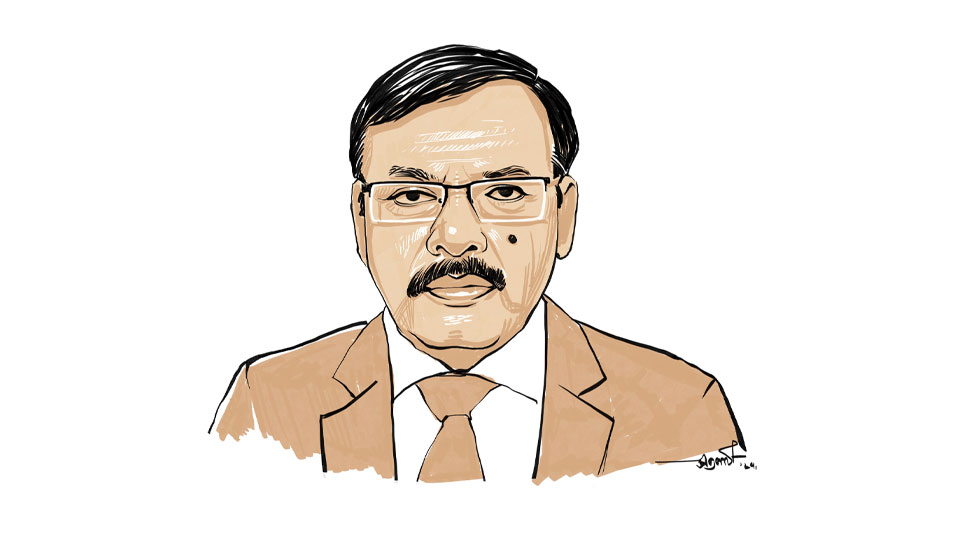নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়ত জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন চৈত্র পর্ব।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: ফাল্গুন পর্ব
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: বৈশাখ পর্ব
ঢাকায় আসার পরই অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, রাজধানীর গাছপালা নিয়ে একটি বই লিখবেন। তাঁর শাশুড়ি তাঁকে একটি মোটর সাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। সেটি চড়ে তিনি রাজধানী ঢাকার এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন আর গাছপালা দেখতেন। সেগুলো দেখে দেখে একটা পর একটা গাছ নিয়ে লিখতে শুরু করেন। লেখালেখিতে সাহায্যের জন্য নটরডেম কলেজের ফাদার টিম তাঁকে দিয়েছিলেন ডি.ভি. কয়েন লিখিত ‘ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ অ্যান্ড শ্রাবস অব ইন্ডিয়া’ বইটি। কলেজ লাইব্রেরিতে পেয়েছিলেন এ.পি. বেন্থলের ‘ট্রিজ অব ক্যালকাটা’ ও এম.এস. রানধাওয়ার ‘ফ্লাওয়ারিং ট্রিজ অব ইন্ডিয়া’ বই দুটি।
তিনি ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করেন রাজধানী ঢাকার গাছপালা দেখা, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে দু’বছরে লিখে শেষ করলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইটি। বইটিতে বিভিন্ন গাছের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন গোপেশ মালাকার। শিল্পী গোপেশ মালাকার তখন চারুকলার (চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্র। গাছের ছবি আঁকতে তাঁকেও ঘুরতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অনেক জায়গায়। ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি বাংলা একাডেমিতে জমা দিয়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধ, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বইটি প্রকাশিত হয় ১৫ বছর পর ১৯৮০ সালে।
বইটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি মস্কোয়, ১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রগতি প্রকাশনে অনুবাদকের কাজ করতেন। এরপরও বইটি দুইবার ছাপা হয়েছে। প্রতিবারেই প্রথম বইটির সঙ্গে নতুন কিছু গাছপালা যুক্ত হয়েছে। প্রথম মুদ্রিত বইয়ে ছিল ৫২টি গাছের বর্ণনা, তৃতীয় মুদ্রণে যোগ হয়েছে ৩৬টি গাছ। সর্বশেষ ২০১৫ সালে শ্যামলী নিসর্গের তৃতীয় সংস্করণে পেয়েছি মান্দার, কুসুম, মণিমালা ও তমালগাছ— পেয়েছি গ্লিরিসিডিয়াকে যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর যৌবনের বসন্ত দিন।
ফাল্গুন-চৈত্র হলো বসন্তকাল, বসন্ত হলো ফুলের ঋতু। শীতের পাতা ঝরার পর গাছে গাছে নব পত্রপল্লব আর পুষ্পের উন্মেষ নিয়ে আসে এক অপার্থিব নৈসর্গিক সৌন্দর্য, আনন্দের বারতা। ঢাকা শহরেও গাছে গাছে বসন্ত এসেছে। লাল পলাশ, শিমুল, মান্দার ফুল ফুটেছে। সাদা, গোলাপি, বেগুনি— কাঞ্চন ফুটেছে। ফুটেছে গোলাপি-বেগুনি মণিমালা, গোলাপি গ্লিরিসিডিয়া। মধুগন্ধী গ্লিরিসিডিয়া থেকে নাগেশ্বর ফুলে ফুলে নেচে বেড়াচ্ছে মৌমাছিরা। সুগন্ধ বিলাতে শুরু করেছে মহুয়া ফুলেরা। গোলাপি ও সাদা নাগেশ্বর ফুল আর তাম্রবরণ বসন্তে উদগত নবীন পল্লবে এক অপরূপ সাজে সেজেছে নাগেশ্বরগাছগুলো।
রমনা উদ্যান ছাড়া এরূপ বসন্ত শোভা ঢাকা শহরে বিরল। জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে সে শোভা বিক্ষিপ্ত, রমনায় তা ভরাট। তাই এবার বসন্তের চৈত্র পরিক্রমায় হেঁটেছি রমনা উদ্যানের ভেতরে, বাইরে। চৈত্র দিনের ঝরাপাতা মাড়িয়ে তাকিয়েছি ঊর্ধ্বে— আহা পাতা ঝরা গাছগুলোর শাখায় শাখায় জীবনের কি নব উন্মাদনা! কচি পত্রপল্লবে শোভিত তরুরাজি যেন নতুন শাড়ি পড়া সুন্দরী রমণী, ফুলগুলো তার অলংকার।
নগর ঢাকার কাঞ্চন কন্যারা
বাংলাদেশে কাঞ্চনের ১৭টি প্রজাতি থাকলেও অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ঢাকা শহরে তিন প্রজাতির কাঞ্চন রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এ তিন প্রজাতির কাঞ্চন গাছের বাংলা নাম হলো রক্তকাঞ্চন (Bauhinia variegata), দেবকাঞ্চন (Bauhinia purpurea) ও শ্বেতকাঞ্চন (Bauhinia acuminata)। তিনটি প্রজাতিই ফ্যাবেসি গোত্রের, অর্থাৎ তারা একই পরিবারের তিন সহোদর।

রক্তকাঞ্চনের ইংরেজি নাম ‘হংকং অর্কিড ট্রি’, দেবকাঞ্চনের ইংরেজি নাম ‘অর্কিড ট্রি’ বা ‘বাটারফ্লাই ট্রি’ এবং শ্বেতকাঞ্চনের ইংরেজি নাম ‘স্নো অর্কিড ট্রি’। এদের প্রজাতিগত নামাংশ বাউহিনিয়া রাখা হয়েছে দুইজন যমজ ভাই যোহান বুহিন ও গ্যাসপার্ড বুহিনের নামের সম্মানে। তাঁরা ছিলেন ষোড়শ শতকের দুই বিখ্যাত সুইস উদ্ভিদবিজ্ঞানী। এই তিন কাঞ্চনেরই আাদি নিবাস এই ভারতীয় উপমহাদেশ ও মিয়ানমার। বিশেষ করে ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের অরণ্যভূমি এদের জন্মভূমি।
রক্তকাঞ্চন ও দেবকাঞ্চনের গাছ ছোট বৃক্ষ প্রকৃতির, শ্বেতকাঞ্চনের গাছ গুল্ম প্রকৃতির। রক্তকাঞ্চনের ফুলের রঙ ঘন ম্যাজেন্টা, ফোটে হেমন্ত ও শীতকালে, বসন্তেও কিছু ফুল দেখা যায়। দেবকাঞ্চনের ফুল গোলাপি বা হালকা বেগুনি, ফোটে বসন্তে। আর শ্বেতকাঞ্চনের ফুলের রঙ দুধের মতো ধবধবে সাদা, ফোটে বসন্ত থেকে শরতে। ফুলের রঙ ছাড়া আর কোনও কিছু দেখেই এ তিন প্রজাতির গাছকে সহজে আলাদা করার কোনও উপায় নেই। তিন প্রজাতির গাছেরই পাতা উটের খুরের মতো দ্বিফলক বিশিষ্ট, সবুজ। এজন্য এদের ‘ক্যামেল ফুট ট্রি’ নামেও ডাকা হয়। তিন প্রজাতির গাছেরই শীতে শীর্ণ দশা হয়, এ সময় গাছের সব পাতা ঝরে গাছ উলঙ্গ হয়ে যায়। বসন্ত এলেই তাতে পাতা গজানো শুরু হয়। বিশেষ করে দেবকাঞ্চন গাছে একটা পাতাও থাকে না, আগে ফোটে ফুল, ফুলের উচ্ছ্বাসে ছেয়ে যায় সব ডালপালা, এরপর আসে পাতারা। এ সময় ফুল ফোটা গাছকে দেখলে মনে হয়, ডালে ডালে যেন অজস্র গোলাপি প্রজাপতির মেলা বসেছে। সে কারণেই এদের বলা হয় ‘বাটারফ্লাই ট্রি’।


তিন কাঞ্চন ফুলেরই গড়ন প্রায় একই, দেখতে অনেকটা অর্কিড ফুলের মতো। পাঁচটি পাঁপড়ির মধ্যে একটির গড়ন একটু ভিন্ন। ঘন ম্যাজেন্টার উপর সাদায় কিংবা সাদার উপর মৃদু গোলাপি রেখায় অথবা হালকা গোলাপির উপর ঘন ম্যাজেন্টায় চিহ্নিত পাঁপড়িগুলো দেখতে অনেকটা কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো।
কৃষ্ণচূড়া ও কাঞ্চনের মধ্যেও গোত্রগত মিল রয়েছে। দুটি গাছই ফ্যাবেসি গোত্রের। তিন প্রজাতির কাঞ্চনের মধ্যে দেবকাঞ্চনের ফুল উগ্রগন্ধি। তিন রকম কাঞ্চনের ফল শিমের মতো চ্যাপ্টা, শিমগাছও একই গোত্রের। প্রথমে ফলগুলো বাদামি-সবুজ থাকে, পরে শুকিয়ে বাদামি হয়ে যায়। শুষ্ক ফল শক্ত। শুষ্ক ফল হঠাৎ শব্দ করে ফেটে যায় ও বীজগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। উপযুক্ত পরিবেশ ও সে মাটিতে রস পেলে সহজে বীজ থেকে চারা গজায়। চারা ও গাছ দ্রুত বাড়ে।

গত বছর রক্তকাঞ্চন ও শ্বেতকাঞ্চনের চারটি চারা নিয়ে লাগিয়েছিলাম টাঙ্গাইলের সখিপুরে কবি নজরুল পার্কে। এ বছর সেগুলো আমার চেয়ে বেশি উচ্চতায় পৌঁছে গেছে, ফুলও ফুটছে গাছগুলোতে। অথচ সেগুলো বীজের চারাই ছিল। নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ সালে নটরডেম কলেজে যোগ দেওয়ার পরপরই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আশেপাশে অনেকগুলো কাঞ্চনগাছ লাগিয়েছিলেন। কাঞ্চনের বেগুনি ও সাদা ফুলকে তিনি তুলনা করেছিলেন আমাদের চেতনার রঙের সঙ্গে।

ঢাকা শহরে এই তিন কাঞ্চনের এক সঙ্গে দেখা পেয়েছি রমনা পার্কে, মহুয়া চত্বরের পূর্বপাশের প্রাঙ্গণে রয়েছে কয়েকটি রক্তকাঞ্চন আর শ্বেতকাঞ্চনের গাছ। বসন্তে গিয়ে ফুলভরা গাছগুলোকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এর একটু দূরেই রয়েছে একটা দেবকাঞ্চনের গাছ। রমনায় কয়েকটা দেবকাঞ্চন গাছ রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬৫ সালে ঢাকা শহরে কাঞ্চনের অস্তিত্বের কথা জানাতে গিয়ে তাঁর শ্যামলী নিসর্গ বইয়ে লিখেছেন, ‘‘ঢাকায় পরীবাগ অঞ্চল ও হেয়ার রোডে দু’একটি কাঞ্চন দৈবাৎ চোখে পড়ে।’’ এখন রমনা পার্ক, সংসদ ভবন, চন্দ্রিমা উদ্যান, আজিমপুর রোড, বাংলা একাডেমি চত্বর— সর্বত্রই এখন ছড়িয়ে পড়েছে কাঞ্চন কন্যারা। এ তিন কাঞ্চনই আমাদের রূপসী তরুদের মধ্যে অন্যতম। যে কোনও বাগানে ও বাড়িতে এরা অনেকটা বিনা যত্নেই প্রচুর ফুল দেয়।
মহুয়ার খোঁজে
মহুয়া যে প্রাচীন ভারতের গাছ তার উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রায় দুই হাজার বছর আগে রচিত সংস্কৃত কবি কালিদাসের ‘কুমার-সম্ভব’ কাব্যে। এ কালের মানুষদের কাছে মহুয়া ফুলের কদর নেই সত্য, তবে সে কালের লোকেদের কাছে মহুয়ার কদর ছিল উপভোগ্য। সেকালে মেয়েদের অঙ্গরাগ তথা প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল নানা গাছের ফুল ও ফুলের রেণু। ফুল দিয়েই তারা তাদের দেহকে সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতেন। কালিদাসের এই কাব্যে দেখা যায়, সে যুগের মালবিকারা অনেক সময় ধরে ধীরে-সুস্থে প্রসাধন করতেন, গালে মাখতেন লোধ্ররেণু, গলায় মধুকের মালা, হাতে লীলাকমল। কালিদাসের ‘রঘুবংশম্’ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ম্বর সভায় ইন্দুমতীর রূপসজ্জার বর্ণনাতেও কবি কালিদাস লিখেছেন—
‘‘বাক্য অন্তে হেরি তারে যবে নির্বাক হয়ে করিলো নীরস-প্রণতি।
এলোমেলো হোলো দূর্বা-শোভিত মধুকমালিকাখানি, চলিলা ইন্দুমতী ॥’’
কালিদাসের ‘কুমার-সম্ভব’ কাব্যের সপ্তম সর্গে মহুয়ার যে বর্ণনা পাই তা হলো—
‘‘ধূপের ধোঁয়ায় শুষ্ক করিয়া কেশ, কুসুম সাজায়ে ঘন চিকুরের মাঝ,
শ্যামলদূর্বা পাণ্ডু মধুক ফুলে মালা গাঁথি নারী বাঁধিল অলক আজ।’’
মধুক হলো মহুয়া আর লীলাকমল হলো পদ্মফুল। আধুনিক যুগে লোধ্ররেণুর জায়গায় এসেছে ফেইস পাউডার, মধুকের জায়গায় এসেছে মুক্তা বা পুঁতির মালা আর পদ্মফুলের জায়গায় মেয়েদের হাতে উঠেছে ভ্যানিটি ব্যাগ বা ফুটানির থলে। তবে সেই প্রাচীনত্বের খানিকটা অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে সাঁওতাল মেয়েদের মধ্যে। এ কালেও তারা ফুলের মালা পরে, খোঁপায় ফুল গোঁজে। মহুয়ার মদিরা পান করে সাঁওতালরা মাতাল হয়ে জোছনা রাতে মাদল বাজিয়ে শালবনের মধ্যে উৎসব করে। সাঁওতালদের কাছেই যেন মহুয়ারা বেঁচে আছে আদরের সঙ্গে।



রমনা উদ্যানের মহুয়া চত্বরে রয়েছে পোলাও চালের গন্ধ বিলানো মহুয়া (Madhuca longifolia) গাছ, ফোটা ফুলগুলো থেকেই ওই সুগন্ধ ভেসে আসে। মহুয়া বেশ বড় বৃক্ষ। এ সময় ডালপালা প্রায় পাতাবিহীন, কিছু কিছু কচি পাতা ছাড়ছে। কিন্তু প্রতিটি শাখার আগায় ঝোপা ধরা দুল বা নাকছাবির মতো দুলছে নস্যি রঙের ফুলগুলো, কিছু ফুল থেকে ফল হচ্ছে। উত্তর-পূব দিকের প্রবেশপথ অরুণোদয় গেট দিয়ে ঢুকে একটু উত্তরে দিকে গিয়ে পেলাম আর একটি প্রাচীন মহুয়া গাছের দেখা। মহুয়ার সুউচ্চ শিখর গগনমুখী হলেও ফুলগুলো মৃত্তিকামুখী। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও সে আভাস:
‘‘রে মহুয়া নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধে ধরে।’’
মৈয়মনসিংহ গীতিকার একটি অন্যতম পালাগানের নাম ‘মহুয়া’। ময়মনসিংহে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিজ কানাই এ পালাগান রচনা করেন যার কেন্দ্রীয় চরিত্র বেদে সরদার হুমরা বেদের পালিত কন্যা ছিল মহুয়া সুন্দরী।
স্মৃতিময় গ্লিরিসিডিয়া
দ্বিজেন শর্মা ১৯৫৭-১৯৫৮ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখনও ছিল গ্লিরিসিডিয়া গাছ। কার্জন হলের সামনের সেই গ্লিরিসিডিয়া গাছের তলায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে তিনি তখন আড্ডা দিতেন। এমনকি জোছনাপ্লাবিত কোনও কোনও রাতে ওই গাছের নিচে বসে তিনি কল্পনায় দেখা পেতেন মোগল রাজকন্যাদের।
তাঁর ‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি জীবনস্মৃতি’ বইয়ের পণ্ডিতষ্মন্য বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন নিবন্ধে উঠে এসেছে গ্লিরিসিডিয়ার সেই স্মৃতিকাতরতা আর অপূর্ব সেই কল্পচিত্রের বর্ণনা, ‘‘নেহাল ও আমি প্রায়ই কার্জন হল চত্বরের বিস্তৃত তৃণাঙ্গনে বিকালে ঘুরে বেড়াতাম। এখানে তখন এত গাছগাছালি ছিল না। বোটানিক গার্ডেনের কিনার ঘেঁষে ছিল গ্লিরিসিডিয়ার দুটি বড় গাছ। আমাদের অনেক সন্ধ্যা কেটেছে ওই গাছের নিচে। গোধূলির ম্লান আলোয় কার্জন হলের মোগল স্থাপত্য রহস্যময় হয়ে উঠত। আমরা রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্প নিয়ে আলোচনা করতাম। এটি ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এবং এখানে কোনও মোগল শাহজাদির ক্ষুধিত আত্মা থাকার কথা নয়। কিন্তু এমন একটি বোধ আমাদের উপর আছর করত যেন তাঁদের কেউ না কেউ এখানে আছেন এবং জোছনাপ্লাবিত রাতে এই রমনার চত্বরে ঘুরে বেড়ান।’’

গ্লিরিসিডিয়ার বাংলা নাম খুঁজতে গিয়ে বইপত্রে ভারতীয় বাংলা নাম পেলাম ‘শারঙ্গ’, মারঠী নাম ‘গিরিপুষ্প’। বাংলাদেশের উদ্ভিদ নামের অভিধানে এর বাংলা নাম রয়েছে ‘বসন্ত মঞ্জরি’ ও ‘ইন্দুরমারা’। এ বইয়ে গ্লিরিসিডিয়ার দুটি প্রজাতির উল্লেখ রয়েছে আলাদাভাবে। একটি কুলামারা (Gliricidia maculata) ও অন্যটি ইন্দুরমারা (Gliricidia sepium)। কিন্তু ইন্ডিয়া বায়োডারভারসিটি পোর্টালের তথ্যে দেখা যায়, গ্লিরিসিডিয়া ম্যাকুলাটা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামটি গ্লিরিসিডিয়া সেপিয়ামের সমনাম বা পূর্বনাম।
এ পূর্বনামটারই উল্লেখ দেখা যায় অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মার শ্যামলী নিসর্গ বইয়ে। তিনি গ্লিরিসিডিয়া ম্যাকুলাটা প্রজাতির দুটি নামাংশের অর্থও দিয়েছেন সে বইয়ে। লিখেছেন, ‘‘গ্লিরিসিডিয়া লাতিন শব্দ— অর্থ ইঁদুর-মারা। বীজ ইঁদুরের বিষ, তাই এমন নামকরণ। ম্যাকুলাটা অর্থ— তিলকিত। সারা গাছে ছড়ানো তিলের মতো দাগের জন্যই এই নাম।’’ ইউরোপীয় লাইলাক ফুলের রঙের সঙ্গে গ্লিরিসিডিয়ার মিল থাকায় এর ইংরেজি নাম রাখা হয়েছে মেক্সিকান লাইলাক, অন্য নাম মাদার অব কোকোয়া, ট্রি অব আয়রণ, কুইক স্টিক, গ্লোরি সিডার ইত্যাদি।
দ্বিজেন শর্মা ১৯৬৫ সালে ঢাকা শহরে গ্লিরিসিডিয়া গাছের অবস্থান সম্পর্কে ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ইস্কাটনে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল রোডের কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন শেরেবাংলার সমাধির কাছেও আছে একটি পূর্ণবয়স্ক গ্লিরিসিডিয়া গাছ। ‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি জীবনস্মৃতি’ বইয়ে বলেছেন কার্জন হলের সামনের গ্লিরিসিডিয়া গাছের কথা। সে গাছটি আরও পুরনো। বসন্তের এক সকালে কার্জন হলের সামনে গিয়ে সেই স্মৃতিময় প্রাচীন গ্লিরিসিডিয়া গাছের সঙ্গে দেখা হলো। গাছের উচ্চতা ভবনের ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। সরু সরু দোলায়মান সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখাগুলো হালকা গোলাপি ফুলে ভরে আছে। মধুগন্ধে বিমোহিত মধুপায়ী মৌমাছিরা সেসব ফুলে এসে গুঞ্জরণ করছে। কিন্তু ফুলগুলো সবই গাছের মাথার উপরে। সাধারণ ক্যামেরায় তার ছবি তোলা কঠিন। ভালো ছবি হবে না। তাই আলোকচিত্রীর দ্বারস্থ হলাম। তিনি এর অনেকগুলো ছবি তুলে আমাকে পরে পাঠিয়ে দিলেন।


এ গাছ দেখে আর দ্বিজেন শর্মার বর্ণনা পড়ে শিহরিত হতে হয়। ঢাকা শহরে এত অত্যাচার-নির্যাতন ও দূষণ সহ্য করে সেই স্মৃতিময় গাছ যে এখনও কীভাবে টিকে আছে সেটিই আশ্চর্যের বিষয়। বুড়ো হয়েছে, গাছের বাকল ও ডালপালা জুড়ে সে বার্ধ্যক্যের ছাপ। তারপরও বসন্ত এলে সে গাছ অজস্র ফুল ফুটিয়ে পথিককে আন্দোলিত করে। গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর সকালবেলার ঝরা ফুলের পাঁপড়ি যেন পুষ্পশয্যা রচনা করেছে। সংরক্ষিত এলাকা বলেই হয়তো কার্জন হলের সামনের গ্লিরিসিডিয়া গাছ রক্ষা পেয়েছে।
গ্লিরিসিডিয়া মধ্যমাকৃতির বৃক্ষ, গোড়া থেকেই বহু শাখায় বিভক্ত, গাছের মাথার ডালপালা ছাতার মতো ছড়ানো, ডাল দীর্ঘ, নমনীয় ও নতমুখী। বাকল নরম, ধূসর ও অসংখ্য সাদা সাদা ফোঁটায় চিত্রিত। এসব দাগের জন্যই এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের শেষাংশ ম্যাকুলাটা বা তিলকিত। পাতা যৌগিক এক পক্ষল, ডালের ওপর পত্রকগুলো একে অপরের মুখোমুখিভাবে সাজানো। একেবারে মাথায় বা শীর্ষে রয়েছে একটি পত্রক। শীতে পাতা ঝরে যায়। কিন্তু খুব অল্প কয়েকদিনের জন্যই গাছ উলঙ্গ থাকে।
বসন্ত এলেই সেসব ডালপালা পুষ্পসজ্জায় ভরিয়ে দেন প্রকৃতিদেবী। বসন্তের শুরুতেই ফুল ফোটার ঐশ্বর্যে গরবিনী হয়ে ওঠে গ্লিরিসিডিয়া। সাদা বা হালকা গোলাপি রঙের লাখ লাখ কোটি কোটি ছোট ছোট ফুলে এলায়িত দীর্ঘ শাখার সৌন্দর্য দেখার মতো। শিমের মতো ফুল, আকৃতিতে অনেকটা মটরশুঁটি ফুলের মতো। ফুল শেষে হলে গজায় পাতা, ফুল থেকে হয় ফল। ফল চ্যাপ্টা, লম্বা, কাঁচা ফল ধূসর সবুজ, পাকলে হয়ে যায় খড়-সাদা। বীজ থেকে যার সহজে চারা জন্মে সে গাছ ঢাকা শহরের অন্যতম সুদর্শন পথতরু হিসেবে কেন এতেদিন লাগানো হয়নি, সেটিই প্রশ্ন।
এ গাছ বাড়েও খুব তাড়াতাড়ি। বীজের চারা হলেও মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। আমেরিকায় কোকো বাগানে ছায়া দেওয়ার জন্য গ্লিরিসিডিয়া গাছ লাগানো হয়। আগে চিনিনি, কিন্তু সিলেটের কিছু চা-বাগানে অনেক বছর আগে এ গাছ আমিও দেখেছি। এর ঝরা পাতা পচে মাটি উর্বর করে, গাছটির শিকড়ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চয় করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।
জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গ্লিরিসিডিয়া গাছ প্রথম শ্রীলংকায় আসে, পরে ১৯১৬ সালে লাগানো হয় কলকাতায়। এদেশে আসে এর পর। সে হিসেবে গ্লিরিসিডিয়া এ দেশে শতবর্ষী। মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে আছে অনেকগুলো গ্লিরিসিডিয়া গাছ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের বিপরীত দিকে গ্রন্থাগার ভবনের চত্বরে কয়েকটা গ্লিরিসিডিয়া গাছ লাগানো হলেও ঢাকা শহরে তেমনভাবে তা বিস্তার লাভ করেনি।
পাখি ফুল বা ব্রাউনিয়া
নব্বইয়ের দশকেই ড. নওয়াজেশ আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনের পাশে কলা ভবনের কোণে পাখি ফুলের একটি প্রাচীন গাছ দেখে ধারণা করেছিলেন, গাছটার বয়স হবে প্রায় একশো বছর। তাঁর ‘অনাপ্য বৃক্ষের সন্ধান’ নিবন্ধে সেই স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন, ‘‘সেদিন দেখা ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। অনুজপ্রতিম মুনতাসীর ঢাকা শহরের ইতিহাস উদ্ধারে নিমগ্ন। বলল, একটা অবহেলিত গাছের নাম জানাতে চাই। অপূর্ব মঞ্জরি বিন্যাস। বলেই হাঁটতে হাঁটতে মধুর ক্যান্টিনের দক্ষিণে কলা ভবনের এক কোণে একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। এই গাছটায় বছরে একবারই ফুল ফোটে। একেবারে লাল টকটকে ফুল আর কোথাও দেখিনি।’’ সে গাছটি দেখে ড. নওয়াজেশ আহমদ সেদিনই তাঁকে জানিয়েছিলেন, গাছটা বিদেশি, এ দেশে এসেছে ভেনেজুয়েলা বা মেক্সিকো থেকে।

শিম পরিবার অর্থাৎ ফ্যাবেসি গোত্রের সে গাছটার নাম ‘ব্রাউনিয়া’, উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ব্রাউনিয়া কক্সিনিয়া। ব্রিটিশ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ব্রাউনের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ব্রাউনিয়া কক্সিনিয়া (Brownea coccinea)। কক্সিনিয়া অর্থ মোরগের ঝুঁটির মতো উজ্জ্বল লাল।
জানা যায়, স্প্যানিশরা আঠারো শতকে এ গাছ ভারতবর্ষে আমদানি করে। আমাদের দেশে রাজা-মহারাজাদের ও জমিদারদের বাগানে, বিভিন্ন মন্দিরের আঙ্গিনায় এ গাছ প্রবেশ করে গত শতকে। নাটোর উত্তরা গণভবনে ও মুক্তাগাছার জমিদার বাড়িতে এ গাছ এখনও রয়েছে। কক্সবাজারের মহেশখালী আদিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণেও একটি পুরনো ব্রাউনিয়া গাছ আছে। ঢাকায় রমনা পার্কে ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে রয়েছে। তবে ঢাকা শহরে সবচেয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে একটি পাখি ফুলের গাছ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার আঙ্গিনায়। চৈত্র দিনে সে গাছ আলো করে অসংখ্য কুঁড়ি এসেছে ও ফুল ফুটেছে।
মধুর ক্যান্টিনের পাশে ব্রাউনিয়া গাছটির অবস্থা দেখতে এক চৈত্রের দিনে গিয়েছিলাম সেখানে। মুণ্ডিত মস্তকের সে গাছের গুড়ি দেখে গাছটার বয়স আন্দাজ করা যায়, নিঃসন্দেহে গাছটি অনেক বয়স্ক। গাছটাকে দেখে মনে হলো, পুরানো শাহবাগ এলাকায় এক সময় অনেক বিদেশি গাছ লাগানো হয়েছিল। এটাও হয়তো সেসব বিদেশি গাছগুলোর একটি হয়ে এখনও টিকে আছে।

দেখেছিলাম যমুনার ভেতরে থাকা গাছটির স্বরূপ। আহা কি শান্তিতে ছাতার মতো ছাউনি ছড়িয়ে একাকী সে গাছটি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও উপদ্রব নেই, ডালে ডালে অসংখ্য ফুলের কুঁড়ি, কুঁড়িগুলো যেন একট একটা গোলাপি রঙের ডিম লাইট বাল্বের মতো। উজ্জ্বল নবীন পাতার আড়ালে কুঁড়িগুলো যেন লাজুক নববধূ, ঘোমটা খোলার অপেক্ষায়। একটি মঞ্জরিতে অসংখ্য ফুল খোঁপার মতো বল করে গেঁথে আছে। ডালিম ফুলের মতো রঙ, সিঁদুর লাল। এক একটা খোঁপা বা পুষ্পমঞ্জরির বিস্তার প্রায় ছয় ইঞ্চি। ফুলগুলোকে কেউ যেন তোড়া বেঁধে রেখেছে। প্রতিটি ফুলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসেছে সোনালী হলুদ কেশর, কেশরগুলোর মাথায় হলদে রেণু। পাখি ফুল যেন আমাদের দেশের রডোডেনড্রন।
ব্রাউনিয়া ফুল বছরে একবারই ফোটে। ব্রাউনিয়া এর গণগত নাম। হানিসাকল বা মৌচুষি পাখিরা এ ফুল থেকে মধু খেতে আসে, তাই এর বাংলা নাম রাখা হয়েছে ‘পাখি ফুল’। তবে ফুলের সৌন্দর্য ও সম্মান রাজকীয় এবং স্বর্গীয়। তাই এ ফুলকে কেউ কেউ স্বর্গের পারিজাত ফুলের সঙ্গে তুলনা করে নাম দিয়েছেন পারিজাত, অন্তত নাটোর রাজবাড়ির মালিরা একে এ নামেই চেনেন। তবে সেটা ভুল নাম, মান্দারের আর এক নাম পারিজাত। এর ইংরেজি নাম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মাউন্টেন রোজ।
ভারতের অনেক পাহাড়েও এ গাছ দেখা যায়। ড. নওয়াজেশ আহমদ এর ইংরেজি নামের বাংলা অর্থ করে এ ফুলের নাম ‘গিরিকমল’ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তা জনপ্রিয় হয়নি। তেমনি ভারতীয় উদ্ভিদবিদ ড. মনীন্দ্র সান্ন্যাল তাঁর ‘বাংলা নামের বিদেশী উদ্ভিদ’ বইটিতে একে লোহিতাভ নামকরণ করলেও সেটি এ দেশে প্রচার পায়নি। এ ফুলের বীজ হলেও তা থেকে চারা হয় না, গুটি কলম করে চারা করা হয়।
পারিজাত বা মান্দার
নিসর্গী বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও মোকারম হোসেন মান্দারগাছই যে পারিজাত সেটি বোঝাতে গিয়ে কতগুলো ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করেছেন।
কাজী নজরুল ইসলামও পারিজাত নিয়ে রচনা করেছেন গান:
‘‘পরো কুন্তলে, ধরো অঞ্চলে
অমলিন প্রেম-পারিজাত।’’
কুমিল্লায় নার্গিসকে বিয়ে না করে বিয়ের আসর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম উঠে চলে এসেছিলেন। আসার পর নার্গিসের সঙ্গে তাঁর আর কোনও যোগাযোগ হয়নি। দীর্ঘ ১৫ বছর পর নার্গিসকে নজরুল একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিতেও রয়েছে পারিজাতের উল্লেখ: ‘‘তোমার যে কল্যাণ-রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মতো চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে।’’
স্বর্গের গাছ পারিজাত নিয়ে এক পৌরাণিক গল্প আছে। সত্যযুগে দেবতা ও অসুররা ঠিক করলেন, তারা অমৃত পান করে অজর-অমর হবেন। কিন্তু কোথায় সেই অমৃত? অমৃত লাভের আশায় তাঁরা মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসকী নাগকে রজ্জু করে সমুদ্র-মন্থন করা শুরু করলেন। সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈশ্রবা ও কৌস্তভ মণি উঠল। শেষে অমৃতভাণ্ড হতে উঠলেন ধন্বন্তরি, এরপর ঐরাবত বা হাতি। কৌস্তভ মণি নিলেন নারায়ণ, উচ্চৈশ্রবা বা ঘোড়া ও হাতি নিলেন ইন্দ্র। সবশেষে উঠল কালকূট বিষ। সেই বিষ কন্ঠে ধারণ করে মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ। এগুলোর সঙ্গে উঠেছিল পারিজাত বৃক্ষ। পারিজাত নিয়ে গেলেন ইন্দ্র। সে গাছ লাগানো হলো স্বর্গের রাজধানী অমরাবতীর বাগানে। সে গাছের মালিক হলেন ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবী।


একদিন শ্রীকৃষ্ণ পত্নী রুক্মিণীর সঙ্গে বসেছিলেন নিজেদের বাড়িতে। এমন সময় দেবর্ষি নারদ এলেন। নারদ যথারীতি শ্রীকৃষ্ণকে একটি পারিজাত ফুল দিয়ে প্রণাম জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই পারিজাত ফুল দিলেন রুক্নিণীকে। যখন শ্রীকৃষ্ণের আর এক পত্নী সত্যভামা জানতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্নিণীকে স্বর্গের ফুল পারিজাত দিয়েছেন, তখন তিনি সে ফুল পাওয়ার জন্য ক্রুদ্ধ ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বর্গের বাগান থেকে পারিজাত ফুল এনে দেওয়ার কথা দিলেন। একদিন তিনি সত্যভামাকে নিয়ে ইন্দ্রলোকে গেলেন। কিন্তু শুধু ফুল নয়, সত্যভামা সেই পারিজাত গাছটাই ইন্দ্রলোক থেকে নিজেদের নগর দ্বারকায় নিয়ে আসতে চাইলেন।
শ্রীকৃষ্ণ পত্নীর কথা রাখতে পারিজাত গাছ সেখান থেকে তুলে গরুর পিঠে উঠে যাত্রা করার সময় খবর পেয়ে ইন্দ্র ছুটে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে পরাজিত করে পারিজাতকে নিয়ে মর্ত্যের দ্বারকায়। অর্থাৎ স্বর্গ থেকে পারিজাত প্রথমে এলো এ পৃথিবীতে ভারতবর্ষে। সে কারণে পারিজাত একান্তই আমাদের দেশি গাছ। অন্য এক পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায়, স্বর্গের পারিজাতে ঘ্রাণ ছিল। একদিন মন্দার পর্বতে বসন্ত দিনে মহাদেব ও পার্বতী পারিজাত কাননে বসে সে ফুল ও ফুলের সৌরভে মত্ত হয়েছিলেন ভালবাসার আমোদে-প্রমোদে। মর্ত্যে এসে পারিজাতের সে ঘ্রাণ হারিয়ে গেছে। মর্ত্যের পারিজাতকে দেখে তাই মনে হয়:
‘‘স্বর্গভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপাহাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।’’
পারিজাত শিমগোত্রের গাছ, ফ্যাবেসি গোত্রের পারিজাত গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ইরিথ্রিনা ফিউস্কা (Erythrina fusca)। গ্রিক শব্দ ইরিত্রিনা অর্থ লাল রঙ। মান্দার ফুলের রঙ টকটকে লাল। এমন টকটকে সিঁদুরে লাল ফুলের জন্যই এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামাংশ হয়েছে ইরিথ্রিনা। মান্দার এ দেশে মোটেই দুর্লভ নয়। গ্রামের পথে ঘাটে, বাড়ির বেড়ার কোলে, খালপাড়ে ও খেতের আইলে এদের দেখা যায়। কিন্তু ঢাকা শহরে মান্দার গাছ খুঁজতে হলে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে। কেননা, ঢাকা শহরে মান্দারগাছ রয়েছে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে। একটি পরিকল্পিত মান্দারবীথি রয়েছে রমনা উদ্যানের ভেতরে। মিন্টোরোডের দিকে অরুণোদয় তোরণ দিয়ে ঢুকে সোজা হেঁটে গেলে সেই মান্দারবীথি চোখে পড়ে। চৈত্রে সেসব দীর্ঘগাছ পাতা ঝরিয়ে নিঃস্ব হলেও কুঁড়ি ও ফুলের আগমন তার সেই নিঃস্বতা ভরিয়ে দিতে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। একবার ফুল ফুটলে সেসব পুষ্পমঞ্জরিতে একের পর এক ফুল ফুটতে থাকে অনেকদিন ধরে। আর সেই ফাঁকে কন্টকিত শাখা-প্রশাখায় আসতে থাকে বিটপ আর পাতার উন্মেষ। মান্দারের এই শোভাকে আমরা সাধারণত গ্রাহ্য করি না। কেননা, বসন্তে বনে বাগানে এত বেশি ফুল এ দেশে ফোটে যে তার ভিড়ে মান্দার যেন পাত্তাই পায় না। দেশি গাছ বলেই কি মান্দারের প্রতি এই অবহেলা? ঢাকার বিদেশী গাছগুলো নিয়ে আমাদের যে উচ্ছ্বাস, তা মান্দারের বেলায় নেই।
মান্দার পাতাঝরা স্বভাবের মাঝারি আকারের বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫ থেকে ২০ মিটার হয়। ফিকে ধূসর সবুজ বাকল, কাঁটায় ভরা। তরুণ গাছে কাঁটা থাকে বেশি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার পরিমাণও কমতে থাকে। পাতা তিনটি পত্রিকার সমন্বয়ে গঠিত, পত্রিকাগুলো প্রায় ত্রিভূজাকৃতি। পাতার রঙ সবুজ, তবে সম্প্রতি এ দেশে ভেরিগেটেড মান্দার নামে যে গাছের প্রসার ঘটেছে তার পাতা বড় ও হলুদ-সবুজ রেখায় চিত্রিত, ফুল ফোটে কম, বাহারি গাছ হিসেবে লাগানো হয়। মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে নার্সারির কাছে বিচিত্র মান্দারের একটা বড় আছে। চুড়ার মতো অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরিতে অনেকটা পলাশ ফুলের মতো আকৃতির ফুল ফোটে। ফুল শেষে গাছে শিমের মতো ফল হয়। ফলের ভেতরে হয় বীজ। একটি ফলে একটি থেকে আটটি বীজ থাকে। এই বীজ থেকে চারা তৈরি করা যায়, আবার ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে তাও বেঁচে যায়। গাছ বাঁচে অনেক বছর।
নিসর্গী বিপ্রদাশ বড়ুয়া তাঁর ‘গাছপালা তরুলতা’ বইয়ে ঢাকা শহরে পারিজাত তথা মান্দারগাছের অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ইডেন কলেজের দক্ষিণ পাশে পারিজাত গাছ আছে। বসন্তে এর টকটকে লাল ফুল ফোটে। কার্জন হলের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি শতবর্ষী মাদারগাছ আছে, ১৯৯৬ সালে সেটি কেটে ফেলেছে।’’ তিনি একটি বিদেশী প্রজাতির মান্দার গাছ ঢাকায় দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একদিন শিশু একাডেমিতে বসে তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, ‘‘সে গাছে সাদা রঙের ফুল ফোটে।’’ সে ছবি দিয়ে তিনি তখন ইত্তেফাকে একটা লেখাও লিখেছিলেন। সেই সাদা ফুলের মাদার এখন আর নেই।
মণিমালা বা মিলেশিয়া
রমনা উদ্যানে মহুয়া চত্বরের পাশেই একটি মণিমালার চারা গাছ, ডালের আগায় থাকা ছড়ায় ফোটা ক্ষুদে শিমফুলের মতো গোলাপি-বেগুনি ফুলগুলো ঝরে পড়ছে। বসন্তে এ গাছের শোভা দেখার মতো। কাছাকাছি রয়েছে একটা বড় মিলেশিয়া বা মণিমালা (Millettia peguensis) গাছ, ফুল ফুটে ভরে আছে, গাছের তলায় ঝরে পড়ে আছে অজস্র ঝরা ফুল। চৈত্র মাসে মাত্র কয়েক দিনের জন্য মণিমালার এই রূপ, এরপরই ফুল ঝরিয়ে সে রিক্ত।

বাংলায় এ গাছের ‘মণিমালা’ নামটা রেখেছিলেন অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা। এর ইংরেজি নাম ‘জুয়েল অন এ স্ট্রিং’ থেকে সম্ভবত তিনি এর বাংলা নাম রেখেছিলেন মণিমালা। মালার মতো ছড়ায় পুঁতিসদৃশ ফুলগুলো সাজানো থাকে বলেই তিনি এর এরূপ নাম দিয়েছিলেন হয়তো। অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ গ্রন্থে মণিমালা গাছের একটা সারি ১৯৬২ সালে ঢাকায় জিপিওর সামনে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, ‘‘বসন্তে সেসব গাছ ছিল ফুলে ফুলে ভরা।’’ বলেছেন, ‘‘গাছটি এ দেশে নতুন। ব্রহ্মদেশের শুধুমাত্র প্রোম জেলাতেই একমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল।’’ সে গাছটি এখন আর সেখানে নেই।
লন্ডনের কিউ গার্ডেনের কিউরেটর প্রাউডলক ঢাকায় রমনা পার্ক স্থাপনের কাজ পাওয়ার পর বিদেশ থেকে অনেক গাছপালা সংগ্রহ করে রমনায় লাগান। মিলেশিয়া গাছও তার হাত ধরে এ দেশে আসাটা বিচিত্র না। এখন রমনা পার্ক ছাড়াও এ গাছের দেখা মেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ও সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ উদ্যানে। সাভার সেখানে ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি মিলেশিয়ার চারা লাগিয়েছিলেন ইরাকের তৎকালীন সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদের মহামান্য সহ-সভাপতি ইজ্জত ইব্রাহিম। সে গাছে বসন্তে প্রচুর ফুল ফোটে। ঘুরতে ঘুরতে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মুনীর চৌধুরী আবাসিক ভবনের প্রাঙ্গণে দেখতে পেলাম একটি বড় মণিমালা গাছের, ফুলে ফুলে ভরে আছে নিষ্পত্র ডালপালা।
প্রকৃতির মাঝে খুঁজি নিজেকে
প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই আশ্চর্যজনক কিছু না কিছু লুকিয়ে আছে, সৃষ্টির এ এক অপার রহস্য। বাংলাদেশে পাঁচটি ঋতু পেরিয়ে আসে বসন্ত, বসন্তে প্রকৃতি হয়ে ওঠে সবাক। শীতের পাতা ঝরা আমাদের শেখায় মলিনতা ও পুরনো জীর্ণ যা কিছু ঝেড়ে-মুছে ফেলার। বসন্ত আমাদের শেখায় চির নতুনের আহ্বান, সবকিছু হারিয়েও আবার নতুন করে সব ফিরে পাওয়ার মন্ত্র। জীবন আর প্রকৃতি তো এমনই, প্রকৃতি ছাড়া জীবন মৃত।
আমরা প্রকৃতির সন্তান। এই বৃক্ষ, এই নদী, এই সাগর, বিস্তীর্ণ আকাশ আমাদের দেয় উদারতা— শেখায় পরোপকারিতা। যত বেশি আমরা প্রকৃতিলগ্ন হব, তত বেশি আমাদের মানবিক গুণগুলো বিকশিত হবে। যত বেশি আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসব, তত বেশি আমরা আমাদেরও ভালবাসতে পারব। প্রকৃতিকে লীন হলে আসলে নিজেকে সত্যিকারভাবে খুঁজে পাওয়া যায়, অনুভব করা যায় স্রষ্টার রহস্য, আমাদের জীবনের বিকাশ।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: kbdmrityun@gmail.com