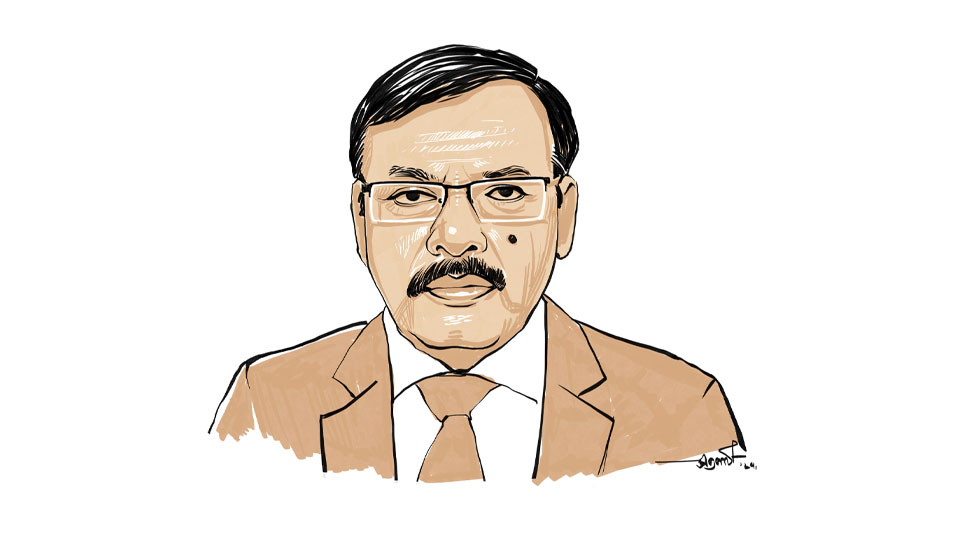নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়তো জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন জ্যৈষ্ঠ পর্ব।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: বৈশাখ পর্ব
নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ‘জীবনস্মৃতি: মধুময় পৃথিবীর ধূলি’ বইয়ে ঢাকা শহরে তাঁর চাকরি জীবন ও উদ্যান সৃজনের বেশ কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন যা থেকে আমরা সে সময়ে ঢাকা শহরের কিছু গাছগাছালির নব আগমন ও রোপণের তথ্য পাই। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় তাঁর অসাধারণ বই ‘শ্যামলী নিসর্গ’ গ্রন্থ লেখার আখ্যান। ১৯৬২ সালের কথা। তিনি উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকার নটরডেম কলেজে। বাসা নিয়েছিলেন তেজগাঁও এলাকার উত্তর প্রান্তে। বাজার করতেন তেজতুরী বাজার আর কারওয়ান বাজারে। সে সময় তেজগাঁও এলাকা ছিল অন্যরকম, দালানকোঠা তেমন ছিলই না।
সে স্মৃতিচারণ করে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, ‘‘সেসব এলাকা তখন একেবারে অন্যরকম। কোনো দালানকোঠা নেই, কেবল ছাপরা ঘর। বাসস্ট্যান্ডে ত্রিকোণ খালি জায়গা, হকারের আস্তানা। রাস্তার ওপরে একদিকে কৃষিফার্মের কয়েকটি লাল-ইটের বাড়ি, অন্যদিকে ইন্দিরা রোডের পাশে আমবাগান, এখনকার শেরে-বাংলা নগরে বিশাল পাটখেত, পাশে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কর্মীদের জন্য দুটি বহুতল ভবন। সবকিছু নিরিবিলি, শ্রীময়।’’
তেজগাঁও, রাজাবাজার, গ্রিন রোড আর শেরে-বাংলা নগরের অতীতের শ্রীময়ী রূপের এক অসাধারণ বর্ণনা পাই অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ‘সুফলা ধরিত্রী’ বই থেকে। এ বইটিও তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি ধারণ করে আছে। ১৯৬০ সালে তিনি এসব এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একদিন ঘুরতে বেরিয়েছিলেন গ্রামের ধানখেত আর সবুজের সেই শ্রীময়ী শোভা দেখার লোভে। পায়ে হেঁটে তাঁরা নিউ মার্কেট এলাকা থেকে মিরপুর রোড ধরে কলাবাগান থেকে সরু গলির মতো রাস্তাটা ধরে ডান দিকে নেমে পড়েছিলেন।
তিনি লিখেছেন, ‘‘পিচঢালা সে চিকন রাস্তার দুপাশে তখন গা-ছমছম করা গভীর জঙ্গল, মাঝে মাঝে উঁচু জমিতে আদিকালের কাঁঠাল বন। রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সত্যি সত্যি এক সময় গ্রামবাংলার একেবারে বুকের ভেতর এসে হাজির হলো সবাই— সেই ঝোপ, বাঁশ, শেয়ালের দেশ। বাঁ দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল আদি-অন্তহীন ধানখেতের সোনালি সাম্রাজ্য। সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই এক বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেতের তাজা সজীব ঘ্রাণ আর হাওয়ার শব্দ বুক ভরে নিতে লাগলাম। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ছোট্ট একটা কালভার্টের ওপর।’’
তিনি যে কালভার্টের কথা বলেছেন, তা আসলে আজকের গ্রিন রোডে ধানমন্ডি খালের উপরে ছিল। সেই ধানমন্ডি খালটি ক্রমে ক্রমে রাজাবাজার খাল নামে সেই কালভার্টের নিচ দিয়ে বয়ে আজকের পান্থকুঞ্জের ভেতর দিয়ে কাঁঠালবাগান হয়ে হাতিরঝিলে এসে পড়েছিল। ধানমন্ডি খালের অংশটি আজ হয়েছে ধানমন্ডি লেক, হাতিরঝিল হয়েছে আজ আরও রূপবতী।
ঐতিহাসিক আমতলা
আম আমাদের জাতীয় বৃক্ষ ও সকলের পরিচিত হলেও এই ঢাকা শহরেই একটি আম গাছের তলা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি জন্ম দিয়েছিল এক ইতিহাসের। সেই আম গাছটির অবস্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কলাভবনের সামনে (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জরুরি বিভাগ)। সেদিন ছাত্র-জনতা মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির দাবিতে পাক সরকারের ১৪৪ ধারা ও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে জড়ো হয়েছিলেন, সভা সমাবেশ করেছিলেন। এর আগেও তারা সেই আম গাছের তলায় বসে সভা করতেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় সেই আমতলায় শুরু হয়েছিল ছাত্রসভা। এই ছাত্রসভা থেকেই ১৪৪ ধারা অমান্য করার ঘোষণা দেওয়া হয়। সে সময় গেইটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল খাকি হাফপ্যান্ট পরা পুলিশ বাহিনী। সভা শেষে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ শ্লোগান দিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে ছাত্ররা বের হলে তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। তাতে শহীদ হন বরকত, জব্বার, রফিকসহ বেশ কয়েকজন ভাষাসংগ্রামী। বায়ান্নর সেই ঘটনার পর আম গাছটি হয়ে ওঠে ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী।

বর্তমানে সেখানে সেই আম গাছটি নেই, আছে ভাষা আন্দোলন স্মৃতি রক্ষা পরিষদ কর্তৃক সংরক্ষিত ‘ঐতিহাসিক আমতলা প্রাঙ্গণ’টি। কিছু ব্যানার লাগিয়ে স্মৃতিরক্ষার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে স্থানটি। দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৬৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই ঐতিহাসিক আমতলার একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে সে সময় সে গাছটিকে সেখানে বেশ ভালো অবস্থাতেই দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানকার স্থাপনার সঙ্গে আম গাছটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত আর একটি ছবিতে আমগাছটির সেই বেহাল অবস্থা দেখা যায়।
শেষে ১৯৮৮ সালে সেই ঐতিহাসিক গাছটি মারা যায়, ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর সেই ঐতিহাসিক মৃত আমগাছটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেটে তা ডাকসু সংগ্রহশালায় স্মারক হিসেবে তার কিছু অংশ সংরক্ষণ করা হয়। ইতিহাসের সেই স্মৃতি রক্ষার্থে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল মৃত আমগাছটির কাছাকাছি আর একটি আমগাছ লাগান। কিন্তু সেটিও টেকেনি। মোগল সম্রাট আকবরের লক্ষ আম গাছ লাগানো লাখবাগ, পলাশীর আম্রকানন, মুজিবনগরের বৈদ্যনাথতলার আম বাগান ইত্যাদি আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন— রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাক্ষী, স্মৃতির মণিকোঠার কিছু উজ্জ্বল রত্ন। সেই আমরত্ন রয়েছে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও—
‘‘ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—’’
বায়ান্নর সেই ঐতিহাসিক আম গাছ ছাড়াও ঢাকা শহরে আম গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক স্থানে। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে লিখেছেন, ‘‘ঢাকায় আমগাছ সহজদৃষ্ট এবং যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। শ্রীহট্টের অরণ্য অঞ্চলে বন্য-আম চোখে পড়ে, বৈজ্ঞানিক নাম ম্যানজিফেরা সিলভাটিকা। আমাদের আমের এটিই পূর্বপুরুষ।’’

বিজ্ঞানী ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, আমের আদি জন্মস্থান আসাম থেকে সাবেক ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার) পর্যন্ত অঞ্চল। সে অর্থে বাংলাদেশের পূর্বাংশও আমের জন্মভূমির দাবিদার। যেসব জাতের আম এ দেশে দেখা যায়, তার অধিকাংশ জাতেরই সৃষ্টি সেসব অঞ্চলে। বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যে আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগেও এ অঞ্চলে আম চাষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আসা পর্যটকরাও তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে আমকে সরস ফল বলে উল্লেখ করে গেছেন।
চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩২ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ দেশ ভ্রমণে আসেন। তিনিই প্রথম তার ভ্রমণ কাহিনীতে আমের কথা বর্ণনা করে বহির্বিশ্বে আমকে সরস ফল হিসেবে পরিচিত করেন। আমগাছ বাঁচে দুইশ বছরেরও বেশি। এ দেশে প্রায় ছয় হাজার প্রজাতির গাছ আছে, এর মধ্যে একক প্রজাতির সংখ্যা বিচারে আম প্রজাতির গাছের সংখ্যা সব প্রজাতির গাছগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ, এরপর সুন্দরী গাছ।

ঢাকা শহরে রমনা উদ্যানেও রয়েছে প্রায় ২৫০টি আমগাছ। রমনার পাঁচ হাজার গাছের যে কোনও প্রজাতির গাছের মধ্যে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যা। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি আম গাছ রয়েছে বেশ প্রাচীন, ৭০ থেকে ৮০ বছর হয়তো তার বয়স হবে।
আমকে বলা হয় ফলের রাজা। আম কেন ফলের রাজা উপাধি পেল তা নিয়ে ইতিহাসে এক সরস গল্প প্রচলিত রয়েছে। সম্রাট আকবরের আমের প্রতি আসক্তি নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একবার সম্রাট আকবর এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেই ভোজসভায় রাজন্যবর্গসহ মন্ত্রী ও সভাসদরা হাজির হলেন। ভোজসভায় সম্রাট আকবরের একজন প্রিয় সভাসদ বীরবলও উপস্থিত ছিলেন। বীরবল পেটপুরে বিভিন্ন খাবার খেলেন।
বীরবল সম্রাটকে জানালেন, তিনি এত খেয়েছেন যে, তার পেটে আর খাওয়ার মতো কোনও জায়গা নেই, আর নতুন করে কিছু খেতে পারবেন না। এমন সময় বীরবলের পাত্রে একজন খাবার পরিবেশনকারী বেশ কয়েক টুকরো আম রেখে যান। বীরবল আমের লোভ সামলাতে পারলেন না। আমের সেই টুকরোগুলো খেলেন তৃপ্তির সঙ্গে।
এ দৃশ্য দেখলেন সম্রাট আকবর। তিনি বীরবলকে বললেন, ‘‘কি, বীরবল, তোমার পেটে নাকি জায়গা নেই? আমগুলো তো নিমিষেই সাবাড় করে দিলে!’’ বীরবল সম্রাটকে মিনতি করে বললেন, ‘‘মহামান্য সম্রাট! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে যাওয়া শুরু করেন তখন রাস্তায় লোকজন থাকলেও তারা সরে যায়, রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়। মহারাজ আপনিও যেমন সম্রাট তেমনি আম্র হচ্ছে সম্রাট বা ফলের রাজা। আমার পেট ভরা থাকলেও সে আমার পেটে ঠিকই জায়গা করে নিয়েছে।’’
বীরবলের এ কথায় সম্রাট আকবর বেশ খুশি হলেন। বীরবলকে তিনি এক ঝুড়ি আম উপহার দিলেন। এই হলো আমের ‘ফলের রাজা’ উপাধি পাওয়ার কাহিনী।
আমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Mangifera indica ও গোত্র অ্যানাকার্ডিয়েসি। আম গাছ একটি বৃক্ষজাতীয় বহুবর্ষী দ্বিবীজপত্রী চিরসবুজ উদ্ভিদ। পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে গাছের উচ্চতা ৪০ মিটার পর্যন্ত হয়। আম গাছ বাঁচে শত বছরের উর্ধ্বে। গাছের প্রধান মূলতন্ত্র বেশ দীর্ঘ ও মজবুত হয়। গাছের কষ বা তরুক্ষীর আঠালো ও ঘন, কাণ্ড শক্ত, মোটা ও দীর্ঘ হয়ে থাকে। প্রধান কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বর্হিমুখীভাবে বিস্তৃত হয়ে ছাতার মতো ঝোপাল একটি গড়ন তৈরি করে। পাতা সরল, লম্বাটে পত্রফলক বিশিষ্ট ও একান্তর। পাতার বোঁটা এক থেকে ১২.৫ সেন্টিমিটার লম্বা।
পাতার আকার-আকৃতিতে বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। জাতের কারণে এরূপ হয়। সাধারণত যেসব গাছে বড় আকারের আম ধরে সেসব গাছের পাতা হয় বড়, ছোট জাতের আম গাছের পাতা হয় ছোট। প্রশাখা বা ডালের অগ্রভাগ থেকে শীর্ষক ছড়ায়, পুষ্পমঞ্জরী উৎপন্ন হয়। ডগাসমূহ পরিমিত মাত্রায় পূর্ণতা লাভের পরই কেবল তাতে পুষ্পমঞ্জরী উৎপন্ন হয়। এজন্য আমের অধিকাংশ জাতের গাছই এক বছর পর পর বা একান্তরক্রমিক বছরে অধিক ফল ধরতে দেখা যায়। অবশ্য এর জন্য আরও অনেক কারণ দায়ী।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণত প্রশাখার অগ্রভাগে কুঁড়ির বিকাশ ঘটে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে মুকুল বের হয়। জাতভেদে ফলের আকার ছোট থেকে বড় হয়, আকৃতিতেও পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত লতা আমগুলো ছোট আকারের, ব্রুনাই কিং জাতের আম সবচেয়ে বড়।
একটি আমের মধ্যে একটি বীজ থাকে। বীজ চ্যাপ্টা ও বড়, ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে আয়তাকার। পরিপক্ব আমের আঁটির খোসা শক্ত ও পশমাবৃত, কচি আমের খোসা নরম। বীজাবরণ বা অন্তত্বক পাতলা কাগজের মতো। বীজপত্র দুটি। সাধারণত একভ্রুণী, তবে বহুভ্রুণী বা পলিএমব্রায়নি জাতও আছে, যেমন— রাংগোয়াই। বহুভ্রুণী জাতের একটি বীজে একাধিক ভ্রুণ থাকায় সেই বীজ থেকে একাধিক চারা উৎপন্ন হয়।
কনকচূড়া বা পেল্টোফোরাম
ঢাকা শহরে মেট্রোরেল আমাদের উড়াল পথে আকাশ থেকে প্রকৃতির রূপ দর্শনের এক চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। স্বচ্ছ কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শাহবাগ থেকে বিজয় সরণি পর্যন্ত গেলে দু’পাশে গ্রীষ্মের দিনে চোখে পড়ে সবুজ শ্যামল গাছের মাথায় হলুদ আর লালের টোপর। কারওয়ান বাজার মোড়ে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের চারপাশে যেন ভেসে চলেছে সুন্দরের স্রোত। মেট্রোরেল থেকে হঠাৎ আলোর ঝলকের মতো এক পলক দেখা দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে অজস্র সোনারঙ ফুল ফোটা কনকচূড়ার ও রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়া গাছেরা। দেখে কবিগুরুর মতোই মনে হয় ‘‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত’’।

বিজয় সরণি মেট্রো স্টেশনের আগেই জাতীয় সংসদ ভবনের পূব পাশে রোকেয়া সরণি রাস্তার ধারের কনকচূড়া যেন জ্যৈষ্ঠের জয়টিকা পড়েছে সোনার মুকুটে। এ জন্যই বোধহয় নিসর্গী বিপ্রদাশ বড়ুয়া এর নাম রেখেছিলেন ‘স্বর্ণচূড়া’। আহা কি রাজসিক তার রূপ! কনকচূড়ার এ রকম মনকাড়া রূপ দেখা যায় ভারতের মুম্বাইয়ের হিউজেস রোডে গেলে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগে যেতে পথের বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি বুড়ো কনকচূড়া গাছ। জ্যৈষ্ঠের হাওয়ায় খসে পড়েছে সবুজ ঘাসের উপর শত শত ফুল। ঝরা ফুলের রূপ দেখে মনে হয় কোনও বেখেয়ালি বালিকা হয়তো ভুলে ফেলে রেখে গেছে তার কানের সোনার দুল। তবে সংসদ ভবনের পূবপাশে রোকেয়া সরণীতে সংসদ ভবনের বেষ্টনীর কোলে সারি করে থাকা গাছগুলো যে কোনও পথিকের দৃষ্টি কাড়বেই।

উজ্জ্বল হলুদ ফুলগুলো ফোটে প্যাগোডার মতো চূড়ায় চূড়ায়। পুষ্পমঞ্জরির এই শোভায়, উজ্জ্বল হলুদ রঙে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে মৌ-মাতাল মৌমাছিরা। গাছের ঘনসবুজ ঝাঁকড়া মাথায় অজস্র চূড়াধরা সোনারঙ ফুলে তেতে ওঠে গ্রীষ্মের দাহদিন। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রতপ্ত দুপুরে খাঁ খাঁ করা ফুলগুলো বিকাল হতেই পুষ্পচূড়ার গোড়া থেকে ঝরতে শুরু করে, সারা রাত ধরে ঝরে ঝরে গাছের তলা ছেয়ে ফেলে। সকালে আবার চূড়ার আগায় ফুল ফুটতে থাকে। আর কালবৈশাখী বাতাস হলে তো কথাই নেই। অজস্র ফুল ঝরে পড়ে প্রবল বাতাসে।
রমনা পার্কের ঝিলপাড়ে থাকা কনকচূড়া গাছগুলো যেন বৈশাখী বাতাসে মেতে ওঠে উল্লাসে। ফুল ঝরিয়ে ঝিলের জলে বাতাসে বাতাসে রচিত হয় তখন এক অদ্ভুত পুষ্পমালা, তির তির করে ফুলগুলো দলবেঁধে ভেসে চলে বাতাসে বাতাসে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সেরূপ আর এক দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল একদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে থাকা কনকচূড়া গাছের তলায় গিয়ে। বৈশাখি ঝড়ের পর অজস্র ফুলে ভরে আছে তলাটা। গ্রীষ্মে কনকচূড়ার ঝরা ফুলের একই শোভা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগে যেতে পথের পূবপাশে একটি প্রাচীন কনকছূড়া গাছের তলায়। সবুজ কার্পেট ঘাসের উপর হলুদের ছিট ছিট মাখামাখি। যেন সেগুলো কবিতার এক একটি শব্দ— অনেকগুলো ঝরা ফুলে রচিত সেখানে একটি সম্পূর্ণ কবিতা।

বাতাসে ফুল ঝরে, তাই বলে গাছ তো ফুল ফোটানো বন্ধ করে না। ফুল শেষে সেখানে চূড়াগুলো বদলে যায় তামাটে রঙের ফলে ফলে। সে আর এক সৌন্দর্য। ফুল শেষে ঘন কালচে সবুজ পাতার ঝোপের মাথায় তামাটে রঙের অসংখ্য ফলের স্রোত বয়ে যায়। শিমের মতো ছোট ছোট ফলের ভেতরে যে বীজ থাকে তা থেকে জন্ম নেয় নতুন গাছ। ফুলগুলো দেখার জন্য আবার অপেক্ষা করতে হয় আর এক গ্রীষ্মের।
কনকচূড়ার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম পেল্টোফোরাম টেরোকার্পাম (Peltophorum pterocarpum), গোত্র ফ্যাবেসি, উপগোত্র সিসালপিনিয়েসি। পেল্টোফোরাম এর গণগত নাম, ইংরেজি নাম ‘ইয়েলো ফ্লেমট্রি’ বা ‘ইয়েলো ফ্লেম’। দ্বিজেন শর্মা দৈনিক অবজার্ভার পত্রিকায় ‘প্রাইড অব দ্য ট্রিজ’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সে নিবন্ধে তিনি ১৬টি গাছের বাংলা নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তার একটি ছিল ‘পেল্টেফোরাম ইনার্মি’র বাংলা নাম ‘কনকচূড়া’। পরবর্তী সময়ে কনকচূড়ার এই উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম বদলে সমনাম হিসেবে টিকে থাকে, প্রজাতির নতুন নামকরণ হয় পেল্টোফোরাম টেরোকার্পাম।

দ্বিজেন শর্মার দেওয়া এই বাংলা নামটিকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করেছি। কনকচূড়া দক্ষিণ এশিয়ার গাছ। পাতাঝরা স্বভাবের এ গাছ ২৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়, গোড়ার দিকে বয়স্ক গাছের গুঁড়ির বেড় এক থেকে দেড় মিটার হয়। বাকল অমসৃণ ও ফাটা ফাটা, কালচে। গুঁড়ি কিছু দূর উঠার পর ঊর্ধ্বমুখীভাবে উঠে যায় অনেকগুলো ডালপালা। পাতা যৌগিক, পত্রাক্ষের দু’পাশে পত্রকগুলো বিপরীতমুখীভাবে সাজানো থাকে। পাতা ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা হলেও পত্রকগুলো খুবই ছোট। একটি পাতার পত্রদণ্ডের দু’পাশে ২০ থেকে ৪০টি ছোট ছোট সবুজ পাতা সুন্দরভাবে সাজানো থাকে। পত্রক বড়জোড় আড়াই সেন্টিমিটার লম্বা ও ১০ মিলিমিটার চওড়া হয়। ফুলের পাঁপড়ির রঙ উজ্জ্বল হলুদ। ফুলের পাঁপড়ির বিস্তার মাত্র আড়াই থেকে চার সেন্টিমিটার। পাঁপড়ির কিনারা কুঁচকানো ও সুগন্ধযুক্ত। ফল চ্যাপ্টা শিমের মতো, পাঁচ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা ও আড়াই সেন্টিমিটার চওড়া।

ফলগুলো প্রথমে লাল থাকলেও পাকার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তামাটে রঙ ধারণ করে, শেষে কালচে হয়ে যায় ও ফল ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি ফলের ভেতরে গড়ে চারটি বীজ থাকে। বীজ থেকে চারা হয়। সেসব চারা লাগালে দ্রুত বাড়ে ও চার বছরের মাথায় সেসব গাছে ফুল ফুটতে শুরু করে। ১০০ বছর পর্যন্ত এ গাছের বেঁচে থাকা বিচিত্র না।
কনকচূড়া গাছ এখন ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় আছে। রমনা, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, মতিঝিল, ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, তিন নেতার সমাধি সৌধ চত্বরেও আছে। ‘শ্যামলী নিসর্গ’ গ্রন্থে দ্বিজেন শর্মা ১৯৬৫ সালে ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি স্থানে কনকচূড়া গাছ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। এসব স্থানের মধ্যে মিন্টো রোডের গাছগুলোর কিছু প্রাচীন গাছ এখনও আছে, বেইলি রোড়ে ঢোকার মুখে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার পূব দিকের সীমানা প্রাচীরে, গণপূর্ত মন্ত্রীর বাসভবনের মধ্যে, রমনা উদ্যানের উত্তরায়ন গেইট দিয়ে ভেতরে ঢুকলেও চোখে পড়ে একটি বয়স্ক কনকচূড়া গাছ, আছে লেকের পূব পাশেও।
কিন্তু দ্বিজেন শর্মা বিআরটিসির গুলিস্তান বাস টার্মিনালের কাছের পার্কের যে গাছগুলোর কথা বলেছিলেন, সে গাছগুলো নেই, শ্যামলী নিসর্গের পরের সংস্করণে তিনিই সে কথা লিখে গেছেন। পাকিস্তান আমলেই পার্কের গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে, গাছে অনেকগুলো কাক বসে সভা করতো বলে। পাখির উৎপাত থেকে বাঁচতে এয়ারপোর্টের গাছ কাটা হয় শুনেছি, কিন্তু বাস টার্মিনালের গাছ কাটতে হয় বলে কখনও শুনিনি।
বঙ্গভবনের কাছে যে নতুন পার্কটি করা হয়েছে সেখানে অবশ্য কয়েকটা কনকচূড়া গাছ আছে। পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলীয় অনেক দেশেই কনকচূড়া শোভময়ী পথতরু ও উদ্যান বৃক্ষ হিসেবে লাগানো হয়। সেদিক দিয়ে ঢাকা শহরেও বলা যায় পথতরু হিসেবে কনকচূড়ারা বেশ দাপটের সঙ্গেই রয়েছে, রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঢাকা শহরে এখন কনকচূড়ার কোনও অভাব নেই, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে এ শহরে তাই চলছে কনকচূড়ার শোভা উৎসব।
বাস্তবে ছোট্ট হলেও যদি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ছায়াবিথী’র মতো কোথাও একটি নিরেট ঘন কনকচূড়া বিথী থাকত, তাহলে তার ছায়ার বসে নগরবাসীরা এ সময় কনকচূড়ার উৎসব করতে পারতো, গাইতে পারতো কনকচূড়ার গান, কবিরা লিখতে পারতো কনকচূড়া নিয়ে কবিতা, পড়তে পারত কনকচূড়ার সেসব কবিতা, অজস্র সোনারঙ ফুলের মতো উচ্ছ্বাসের ফুলঝুরি ছোটাতে পারতো কনকচূড়ার কথামালা। অন্তত ফুল ফোটার দিনগুলো জাপানের চেরি উৎসবের মতো নগরেও পালিত হতে পারতো ‘কনকচূড়া উৎসব’।
তপস্বী তমালের নীল ছায়া
প্রাচীনকালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা রূপের উদ্দীপনা হয়েছিল এই তমালের কাছেই। সে ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার ব্রজের বন্ধু অর্জুনের কাছে (মহাভারতের অর্জুন নয়)। বলেছিলেন, ‘‘বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই চিনবে সে সুন্দরীকে, ঠিক ঐ তমাল গাছটার ধারে এসে থমকে দাঁড়ালো, আর আমার দিকে চেয়েছিল কিংবা আনমনে ছিল জানি না, কিন্তু সে সঙ্গে এনেছিল একটি স্বর্ণযূথিকার লতা। সেই লতাটিকে কেন যেন কী ইচ্ছায় ঐ কালো তমাল গাছটায় জড়িয়ে দিলে। আমি কার রূপ দেখলাম? কালো তমালের শিহরিত রূপ? নাকি অপূর্ব সুন্দরীর রূপ বা স্বর্ণযূথিকার রূপ? আমি বহুক্ষণ মুদ্ধ হয়ে হতবাক॥ বোধহয় মূর্চ্ছিত হয়েছিলাম।’’
এই হলো শ্রীকৃষ্ণের চোখে বৈষ্ণব কবি ভর্ত্তৃহরির সংস্কৃত কবিতায় তমাল দর্শন—
‘‘ক্বচিৎ তমালদ্রুম পল্লবানাং
ছায়াসু তন্বী বিচচার কাচিৎ।
স্তনোত্তরীয়েণ করোদ্-ধৃতেন
নিবারয়ন্তী শশিনো ময়ূখাম্॥’’
(অর্থ: কোনও একদিন সন্ধ্যার পরে একদিন একা একটা উপবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম— তমাল গাছের ছায়ায় একটি তন্বী যুবতী একটু বিশ্রাম করছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। বুকের দু’টি স্তনের উপর থেকে পাতলা ওড়নাটা একবার নামাচ্ছে, একবার ঢাকা দিচ্ছে; আবার মাঝে মাঝে চাঁদের উজ্জ্বল কিরণ মুখে পড়ছে বলে তা আড়াল করছে। তখন কি আর ফিরে আসতে পারি?)

তমালের খোঁজ বেশি মেলে আমাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। অধিকাংশ বাংলা কবিতা ও গানে হিজল-তমাল দোসর হয়ে আছে। তমাল নিয়ে বিদ্যাপতির এক বিখ্যাত পদ আছে—
‘‘না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে
সেই ত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়।’’
সৈয়দ আলী আহসানের ‘আমার পূর্ব-বাংলা’ কবিতায়:
‘‘আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ …’’
সাহিত্য ছাড়া তমালের দেখা মেলে দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকা গোবিন্দ মন্দিরগুলোর আঙ্গিনায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তমালগাছ পূজিত হয়। সে অর্থে হিন্দুদের কাছে তমাল যেন এক পবিত্র ও ধর্মীয় বৃক্ষ। জয়দেবপুর ইন্দ্রেশ্বর শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে একদিন এক পূজারিণীকে তমাল গাছের গোড়ায় দুধ-জল-ফুল দিয়ে পূজো দিতে দেখেছিলাম। কৌতুহল হয়েছিল তমালের পূজা নিয়ে।

পূজারিণী জানিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহের রঙ ছিল কালো, তমালেরও দেহ কালো, তাই তমালকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের দোসর হিসেবে মনে করি। তাছাড়া রাধার জন্য তমালের তলায় শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজানোর কথা কে না জানতো? শ্রীকৃষ্ণ যে গাছকে এতো পছন্দ করতেন, সে গাছকে কেন আমরা ভালোবাসব না?
এ জন্যই কি পূজারিণী বলেছিলেন, ‘‘কৃষ্ণ কালো, তমাল কালো, তাইতো তমাল বাসি ভালো।’’ শ্রীকৃষ্ণ বহু বছর বেঁচেছিলেন, তমালের আয়ু যেন তার চেয়েও বেশি। আর বাড়েও খুব ধীরে। এজন্য তমালগাছ দেখে সহজে তার বয়স অনুমান করা যায় না। সেই তমালের দেখা পাব ঢাকা শহরে?

ঢাকা শহরে ড. নওয়াজেশ আহমদও তমালের দেখা পাননি। তবে তমালের আঁধারমাখা ঘন নীল ছায়ার বর্ণনা পাওয়া যায় ড. নওয়াজেশ আহমদের ‘মহাবনস্পতির পদাবলী’ বইয়ে। তিনিও ঢাকা শহরে কখনও তমালের দেখা পাননি, পেয়েছিলেন গ্রামীণ জঙ্গলে, জলাশয়ের ধারে।
দক্ষিণ ভারতের তাপ্তী নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে তমালগাছ জন্মায় বলে এর আর এক নাম ‘তাপিঞ্জ’ বা ‘তাপিঞ্চু’। বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, তমালের আবাসস্থল আসলে জলাশয়ের ধারে। ঢাকার মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে জলাশয়ের ধারে কয়েকটা গাছের একটি ছোট তমাল বিথী আছে। সেখানে তার তলায় গেলে তমালের সেই ঘন ছায়ায় মন জুড়িয়ে যায়। দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ১৯৬৫ সালে ঢাকার জয়কালী মন্দির রোডে যে তমাল গাছটি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন, উন্নয়নের চাপে তা উধাও হয়ে গিয়েছে। ঢাকা শহরে তিনি তন্ন তন্ন করে তমাল গাছ খুঁজে বেড়িয়েছেন।
সে বইয়ে তিনি ঢাকায় যেখানে তমাল তরুর দেখা পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘সমগ্র ঢাকা শহরে অনেক অনুসন্ধানের পর একটি মাত্র তমাল খুঁজে পেয়েছি গভর্নর হাউসের দক্ষিণ গেটের নিকটস্থ জয়কালী মন্দির রোডের রাম-সীতার আশ্রমে।’’
ঢাকা শহরে আর একটি তমালগাছের দেখা পেয়েছি দোয়েল চত্বরের কাছে ঐতিহাসিক ঢাকা তোরণের কোলে। মীর জুমলার কামানের ঠিক পিছনেই সেনাপতির মতো দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল গগন শিরিষ গাছ। আর কামানের সামনে রয়েছে আর এক সেনানী তমাল গাছ।
চৈত্রে দেখেছিলাম তার পাতা ঝরা রূপ, বৈশাখে দেখলাম ফলভারনতা শাখা-প্রশাখা, জ্যৈষ্ঠে তার চূড়ান্ত রূপ— ঘন পত্রপল্লবে ঠাসা, ছায়াঘন, ফলগুলো পেকে হলুদ হওয়ার পর শেষে কালো হতে শুরু করেছে। ডালে ডালে কড়ে মার্বেলের মতো গোলাকার প্রচুর ফল ঝুলছে। কাঁচা ফলগুলো ছিল কালচে সবুজ। আর একটি তরুণ তমাল গাছের দেখা পেয়েছি রমনা কালী মন্দিরের গেইট দিয়ে ঢুকে পুকুর পাড়ে। তমালগাছ ছোট থাকলে তার ডালপালায় অনেক বড় বড় কাঁটা হয়। সে গাছটির ডালপালাও কাঁটায় ভরা। জ্যৈষ্ঠে পাতা ঝরা ডালগুলো ভরে আছে সবুজ কোমল পত্রপল্লবে।

বাংলা সাহিত্যের পাতায় তমালের যতো উল্লেখ আছে ততটা উল্লেখ নেই এ দেশে উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রকৃতিবিষয়ক বইগুলোতে। এমনকি প্রেইন ও বেন্থল সাহেবও তাঁদের বইয়ে তমালের ব্যাপারে নীরব। কেউ কেউ তো গাবগাছকেই তমাল বলে বসে আছেন, বনগাব বললেও কিছুটা মানাতো। তমাল আর গাব একই গোত্রের হলেও দুটি আলাদা গাছ। তমালের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ডায়স্পাইরস্ মন্টানা ভার. কর্ডিফলিয়া (Diospyros montara var. cordifolia) ও গাবের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ডায়স্পাইরস্ পেরিগ্রিনা (Diospyros perigrina)।

ডায়স্পাইরস্ অর্থ স্বর্গীয় গম, কর্ডিফলিয়া অর্থ পান আকৃতি বা হৃৎপিণ্ডাকার পাতা, মন্টানা অর্থ পাহাড়ি। গাব ও তমাল পরষ্পর নিকটজন, একই গোত্রের গাছ, গোত্র ইবেনেসি। তমালের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। ফুল একলিঙ্গী, পুরুষ ফুলেরা গুচ্ছ ধরে ফোটে, অজস্র, কিন্তু আকারে খুব ছোট। স্ত্রী ফুল আকারে বড়, কিন্তু সংখ্যায় পুরুষের চেয়ে অনেক কম ফোটে। ফল দেখতে কিছুটা গাবের মতো হলেও আকারে ছোট, দুর্গন্ধযুক্ত, ভেতরে আট থেকে ১০টি বিচি, গাবের বিচির মতোই, পাকা ফলের বিচির উপর সাদা জেলির মতো আবরণ, ধীরে ধীরে তা কালো হয়ে যায়, স্বাদে তিতা ও বিষাক্ত।
অতীতে তমাল ফলের মণ্ড মাছের বিষ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তমালের আদিনিবাস মিয়ানমার, মালয় ও ভারতের শুষ্ক অঞ্চল। বীজ থেকে চারা হয়, কিন্তু গাছের বৃদ্ধি খুব ধীর।
ঢাকা শহরের একমাত্র ব্ল্যাকবিন গাছ
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার মালি খবর দিলেন, একটা অচিন গাছ— প্রতি বছরই ফুল ফোটে। বসন্ত থেকে ফুল ফুটছে। দেখতে চাইলে আসতে পারেন। অচিন গাছের কথা শুনে মনটা তড়বড় করে উঠলো। দেরি না করে পরদিন সকালেই মিন্টো রোড ও বেইলি রোডের সংযোগ স্থলে যমুনার সামনে গিয়ে হাজির হলাম।

সামনে গিয়ে খোঁজ করলাম মালি শহিদুলকে। দেখা হওয়ার পর তিনি নিয়ে গেলেন সে গাছটার কাছে। সে গাছটা কখনও আমার দেখা হয়নি। বিরাট গাছ, যমুনার উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানা প্রাচীরকে দু’ভাগ করে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা, আশেপাশের সবগাছের মাথা ছাড়িয়ে সে উঠে গেছে আকাশের দিকে। লম্বা দীর্ঘ বৃক্ষ, লম্বা গুড়ি, উপরের দিকে ডালপালা ছড়ানো। উচ্চতায় ২০ থেকে ২৫ মিটার হবে, গাছটাকে দেখেই বোঝা যায় তার বয়স হয়েছে। বয়স মাপার কোনও যন্ত্র হাতে থাকলে সেটা দিয়ে মেপে দেখতে পারতাম। তবে আন্দাজ গাছটার বয়স ১০০ বছরের বেশি হবে।
শহিদুল জানালেন, প্রায় ২৮ বছর ধরে তিনি যমুনায় মালি হিসেবে কাজ করছেন। এ গাছটাকে প্রথম থেকেই দেখে আসছেন বিরাট গাছের মতোই। তার মানে সে গাছটা ওখানে বহুকাল আগে থেকেই রয়েছে। নামটা তিনি শুনেছিলেন কারও কাছে, কিন্তু মনে করতে পারলেন না। উপরে তাকিয়ে গাছের ফুল-ফলের চেহারা দেখার চেষ্টা করলাম। অনেক উপরে ঘন পাতার আড়ালে থোকা ধরা কিছু লাল ফুলের দেখা পেলাম।
হঠাৎ তিনি গাছের তলায় ঝরে পড়া শুকনো পাতার ভেতর খুঁজে পেলেন কয়েকটা ফুল ও কুঁড়ি। দেখিয়ে বললেন, এ রকমই ছোট ছোট লাল ফুল ফোটে গাছটাতে বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। অত উঁচুতে ফোটা ফুলের ছবি তোলা সম্ভব হলো না, তাই কুড়িয়ে পাওয়া ফুলের ছবি তুললাম। ফুল দেখেই নিশ্চিত হলাম, গাছটা ব্ল্যাকবিন। বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য গাছের একটি।
গাছটাকে ভালো করে দেখে নিশ্চিত হলাম, এটাই সেই আলোচিত ব্ল্যাকবিন গাছ। ঢাকার শতবর্ষী গাছগুলোর মধ্যে একটি এবং জানা মতে ঢাকা শহরে এই একটি মাত্র গাছই বেঁচে আছে। সেই একমাত্র গাছটিকে দেখার উত্তেজনা আমাকে প্রবলভাবে আনন্দিত করলো। তেমনি হতাশ হলাম, নাগালের বাইরে থাকায় ফুলের ছবি তুলতে না পেরে। অগত্যা সেই কুড়িয়ে পাওয়া ফুলের ছবি তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।
ব্ল্যাকবিন গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ক্যাস্টানোস্পারমাম অস্ট্রাল (Castanospermum austral) ও গোত্র ফ্যাবেসি। নামের শেষাংশে অস্ট্রালি অর্থ বলে দেয় যে, গাছটার জন্ম অস্ট্রেলিয়ায়, ওই দেশে এ গাছ অনেক আছে। সেখানকার আদিবাসীরা এর বীজ আট থেকে ১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখে, এরপর শুকায় ও আগুনে ঝলসানো বীজ খাওয়ার আগে গুঁড়ো করে নেয়। তবে এখানে ব্ল্যাকবিন গাছ কী করে এলো তার সঠিক ইতিহাস কেউ লিখে রেখে যাননি।

১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। প্রশাসনিক কারণে তখন প্রয়োজন পড়ে অনেক নতুন নতুন ভবন নির্মাণ ও পথ তৈরির। মূল শহর তখন আজকের পুরান ঢাকা। সে জায়গা বাদ দিয়ে ইংরেজরা বেছে নিলেন রমনার খোলা প্রান্তরকে। দু’একটি করে সেখানে বাড়ি উঠতে লাগলো আর পথের ধারে ও বাড়ির খোলা জায়গায় গাছ লাগানো শুরু হলো।
১৯০৯ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ উদ্যানতত্ত্ববিদ রবার্ট লুইস প্রাউডলক পূর্ববঙ্গের উদ্যানতাত্ত্বিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান ও ঢাকায় আসেন। তখন থেকেই তিনি এ অঞ্চলের উপযোগী গাছপালা সংগ্রহ ও রোপণে লেগে পড়েন। গাছপালা সংগ্রহের জন্য তিনি ছুটে যান খুলনা থেকে শিলং, চট্টগ্রাম থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত। সেসব কাজে তাঁর সাথী ছিলেন অখিল চন্দ্র চক্রবর্তী।
প্রাউডলকের পরিকল্পনায় ঢাকার পথে-প্রান্তরে তখন দু’ধরনের গাছপালা লাগানো হয়— জারুল, নাগলিঙ্গম, তাল, তেঁতুল, আমের মতো দেশি গাছ এবং ব্ল্যাকবিন, গ্লিরিসিডিয়া, সিলভার ওক, পাদাউক, পাইন ইত্যাদি বিদেশী গাছ।
তাই সহজেই অনুমান করা যায়, এই ব্ল্যাকবিন গাছটিও সে সময় তাঁরই হাতে হয়তো লাগানো। তিনি গাছটি অস্ট্রেলিয়া থেকে আনেননি, মিয়ানমার থেকে পাদাউক গাছের সঙ্গে হয়তো ব্ল্যাকবিন গাছটি তিনি এনেছিলেন। ঢাকা শহরে অনেকগুলো পাদাউক গাছ শতবর্ষী গাছ হিসেবে টিকে থাকলেও ব্ল্যাকবিনের গাছ আছে মাত্র এই একটাই। যমুনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে, সীমানা প্রাচীর করার সময় এ গাছটাকে না কেটে নিশ্চিহ্ন হওয়ার হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। এখন উচিত এর বংশ রক্ষা করা।

ব্ল্যাকবিন চিরসবুজ বৃহৎ বৃক্ষ প্রকৃতির বহুবর্ষজীবী গাছ। কাণ্ড কালচে ধূসর ও অমসৃণ, রোমহীন। পাতা পক্ষল যৌগিক, ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা পত্রদণ্ডের দু’পাশে বিজোড়পত্রী পত্রকগুলো সাজানো থাকে, শীর্ষে থাকে একটি ছোট পত্রক। পত্রক উপবৃত্তাকার-আয়তাকার থেকে ডিম্বাকার-উপবৃত্তাকার, সামান্য লম্বা অগ্রভাগ, পশমহীন চর্মবৎ। পুরনো পাতার কোল থেকে বা কাণ্ড ফুঁড়ে বের হয় পুষ্পমঞ্জরি।
ফুল দেখতে খানিকটা বক ফুলের মতো, তবে আকারে বক ফুলের চেয়ে অনেক ছোট, পাপড়ির রঙ কমলা লাল, ফুলের বৃতি সবুজাভ হলুদ। পাপড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে পুংকেশরগুলো। ফল শিমের মতো, প্রতিটি ফলের ভেতর গোলাকার চার থেকে পাঁচটি বীজ থাকে। বীজ থেকে চারা হয়। ফুল ও ফল ধারণের সময় ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ। পথের ধারে পথতরু হিসেবে ও বিভিন্ন পার্কে গাছটি লাগানো যায়, সেভাবেই এ গাছের দ্রুত সম্প্রসারণ ঢাকাসহ অন্যান্য শহরেও করা দরকার।
শতবর্ষী পাদাউক
ঢাকা শহরে যদি শতবর্ষী বৃক্ষদের কোনও তালিকা করা হয় তবে সে তালিকায় আশা করি পাদাউক থাকবে শীর্ষে। মিন্টো রোডের রাস্তার ধারে রমনা উদ্যান লাগোয়া অংশে শতবর্ষী পাদাউকের যে দীর্ঘ সারিটি চোখে পড়ে, তা দেশের আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে হাঁটতে গেলেই গাছগুলোর দিকে তাকাই আর মহীরুহের কাছে নিজেকে সমর্পন করি।
কোনও কোনও পাদাউক গাছের গোড়া আমরা চার-পাঁচ জন হাতে হাত ধরাধরি করেও হয়তো ঘিরতে পারব না। সেসব গোড়া কি সুন্দর করে বাঁধানো। লাল পরিচ্ছন্ন ফুটপাত দিয়ে সেসব মহীরুহের ছায়ায় হেঁটে যেতে যেতে এক সুশীতল অনুভুতি আচ্ছন্ন করে ফেলে।

যখনই ও পথে যাই, গাড়ি বা রিক্সায় চড়ি না। ওই শীতল ছায়ার লোভে গাছগুলোর কোল দিয়ে হেঁটে চলি। কিন্তু বৈশাখের সকালে হঠাৎ এই শীতলতার সঙ্গে অন্য আর এক অনুভূতি আমাকে যেন মাতাল করে দিল। আহ! কি মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, গাছের তলায় হলদে গুড়ো গুড়ো ফুল পড়ে ভরে আছে, উপরে তাকাতেই দেখি কচি পত্রপল্লব জমাট থোকা থোকা হলুদ ফুলে ভরে আছে।
সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যটি দেখলাম রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার ভেতরের পাদাউক গাছটিতে। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়েও স্পষ্ট নজরে এলো ফুলে ফুলে ছাওয়া সে সবুজে মেশানো হলুদের ছোপ দেওয়া এক অপূর্ব কোলাজ চিত্র। ঠিক এ রকমই কি না জানি না, ১৯৬৪ সালে নিসর্গী দ্বিজেন শর্মার অনুভূতিকেও নাড়া দিয়েছিল পাদাউক।

‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে তিনি লিখেছেন, ‘‘এই প্রস্ফুটনের স্মৃতি আমার চিরদিন মনে থাকবে। ১৯৬৪ সালের বসন্তের শেষে একদিন ভোরে কলেজে যাচ্ছিলাম। জিপিও-ও কাছে সেকেন্ড গেটে বাস থেমেছে। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক আশ্চর্য সুগন্ধ এলো। প্রথমে আমারই চোখে পড়ল কাছে পাদাউক গাছ, সারা শরীর ছেয়ে নেমেছে হলুদের ঝরনাঝারা। আমি বাস থেকে নেমে গেলাম।’’
আমিও তাই করি, হেয়ার রোডে গেলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ি। পাদাউক গাছে এ রকম হলুদের স্রোত আগে কখনও আমার চোখে পড়েনি। হঠাৎ একদিন দেখলাম, ছবি তুললাম। পরদিন আরও ভালো ছবির আশায় আবার গেলাম গাছগুলোর কাছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! নেই। সব যেন এক দিনের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেছে।
কয়েকটি ডাল সাক্ষ্য দিচ্ছে স্বল্প কিছু ফুল মাথায় নিয়ে। না হলে হয়তো বিশ্বাসই হতো না যে কাল ওই গাছগুলোতেই আমি অজস্র ফুলের শোভা দেখে বিমোহিত হয়েছিলাম। সব পুষ্পমঞ্জরির ফুল ফোটার এমন বিস্ফোরণও হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া আর কোনও গাছের ক্ষেত্রে ঘটে বলে আমার জানা নেই। কোমল সবুজ পাতা ভরা ফুলহীন গাছের শোভাটাও কম না।

দ্বিজেন শর্মা হেয়ার রোড ও মিন্টো রোডের এসব পাদাউক গাছের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং হেয়ার রোডের সামনের পাদাউক গাছের সারিটি যে সুন্দর তা বলতেও ভুল করেননি।
পাদাউক নামটা বর্মী হলেও সে আসলে আমাদের ভারতবর্ষের গাছ। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম টেরোকার্পাস ইন্ডিকাস (Pterocarpus indicus) ও গোত্র ফ্যাবেসি, গ্রিক শব্দ টেরোকার্পাস অর্থ পক্ষল বা ডানাযুক্ত ও ইন্ডিকাস অর্থ ভারতীয়।
পাদাউক এখন বাংলা নামই হয়ে গিয়েছে। এর ইংরেজি নাম বার্মিজ রোজ-উড। পাদাউক বিরাট উঁচু বৃক্ষ, বহুবর্ষী, পত্রঝরা। নিচের দিকে ঝুলন্ত ডালপালায় পাতা থাকে ঝোপাল হয়ে। পাতা যৌগিক, পত্রদণ্ডের দু’ধারে পত্রকগুলো সাজানো থাকে, পত্রদণ্ডের শীর্ষের পাতাটি বিজোড়।
গ্রীষ্মে হঠাৎ ফুল ফোটে, প্রধানত বৈশাখ মাসে। তবে কোনও কোনও গাছে দেখলাম একাধিক দফায় ফুল ফোটে। জ্যৈষ্ঠ্যের প্রথমেও স্বল্প কিছু ফুলের দেখা মিলেছিল রমনা উদ্যানের উত্তরায়ন গেইট দিয়ে ঢোকার মুখে থাকা গাছটায়। শীতে গাছের সব পাতা ঝরে যায়। তখন গাছকে মরা মনে হয়। কোনও কোনও ডালে ঝুলতে থাকে কিছু শুকনো ফল।

বসন্তে আবার নতুন পাতা গজায়, গ্রীষ্মে ফোটে ফুল। ফুল ফোটে মঞ্জরিতে, অজস্র, ছোট ফুলগুলোর রঙ উজ্জ্বল হলুদ। ফল গোলাকার চাকতির মতো। শুকালে ফলের রঙ হয় বিবর্ণ-ধূসর। শুকনো ফল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সসারের মতো অনেক দূরে চলে যায়।
বীজ থেকে চারা হয়। তবু এই মহীরুহ ঢাকা শহরে বিস্তার লাভ করলো না কেন, সেটাই এক রহস্য! এর কাঠ খুব শক্ত, মজবুত ও মূল্যবান। সারকাঠ পোড়া ইটের মতো লাল। বাকল কালো ও অমসৃণ, ফাটা ফাটা। পথতরু ও মূল্যবান কাঠের গাছ হিসেবে পাদাউক অনন্য।
গাছ লাগাই শ্যামল করি
উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসের (১৭০৭-১৭৭৮) শোয়ার ঘরের দরজায় লেখা ছিল ‘যদি একটি গাছের মৃত্যু ঘটে, তার জায়গায় আর একটি গাছ রোপণ করো।’ আমাদের ‘চামেরি হাউস’-এর সামনে মোড়ের বাগানবিলাসওয়ালা বিশাল অশ্বত্থ গাছটি উন্নয়নের নামে ঢাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একদিন কেটে ফেলল। কিন্তু সে জায়গায় আর একটি গাছ লাগানো হলো না।
তারা কবি জর্জ পপ মরিসের কথাও ভাবল না। আমেরিকার এক কাঠুরে নিউইয়র্ক শহরে গাছ কাটতে এলে কবি জর্জ পপ মরিস (১৮০২-১৮৬৪) একটি কবিতা লিখে তাকে গাছটি না কাটতে অনুরোধ করেছিলেন। লিখেছিলেন,
‘‘কাঠুরে ভাই, ওই গাছটিকে রক্ষা করো।
ওর একটা ডালও ছুঁয়ো না।
যুবাকালে ও আমায় আশ্রয় দিয়েছিল,
ওকে রক্ষা করার ভার এখন আমার।’’
কাঠুরে কবির অনুরোধ শুনেছিলেন। নিউইয়র্ক শহরে ৯৮ স্ট্রিট ও ওয়েস্ট অ্যান্ড এভিনিউর ক্রসিংয়ে থাকা সে গাছটি কবির স্মারক হয়ে টিকেছিল। কিন্তু ঢাকা শহরে গাছ কাটা বন্ধ নেই। গত বছর পরিবেশবাদীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কাটা হয়েছে সাত মসজিদ রোডের বড় গাছগুলো। ঢাকার গাছ ফাঁকা করে আমরা নগরবাসীকে একটি তাপিষ্ণু নগরী উপহার দিচ্ছি, এবারও বৈশাখে ঢাকা শহরের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে।
ঢাকা শহরকে গাছ লাগিয়ে শ্যামল করতে না পারলে, ভবনগুলোকে সবুজ ভবন হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে, জলাশয় রক্ষা না হলে তাপদগ্ধ হয়ে একদিন হয়তো এ নগরীতে আর কেউ থাকবে না। তখন ঢাকা শহরে গাছপালাদেরই রাজত্ব হবে আশা করি।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: [email protected]