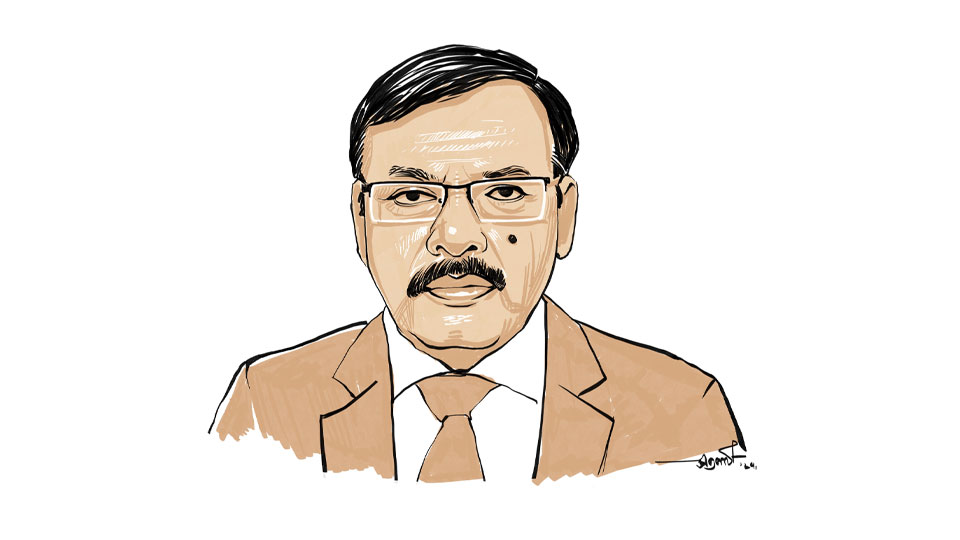নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়তো জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন আশ্বিন পর্ব।
ঢাকা শহরে ধানমণ্ডি এক অভিজাত ঐতিহ্যবাহী শ্যামলিমাময় এলাকা। ১৮৫৯ ও ১৯২৪ সালের মানচিত্রেও ধানমণ্ডির অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে সে সময় ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা ছিল না— ছিল ধান চাষের জমি ও উৎপাদিত সেসব ধান বিক্রির জন্য ছিল কিছু গদিঘর। সেসব গদিঘরকে স্থানীয়ভাবে বলা হতো মুণ্ডি। ‘মুণ্ডি’ শব্দটি হিন্দি-উর্দু ‘মাণ্ডি’ থেকে এসেছে, যার অর্থ বাজার বা পণ্য কেনাবেচার স্থান। এভাবেই ধান কেনাবেচার স্থান থেকে এলাকাটির নাম হয় ধানমণ্ডি। পরবর্তীকালে, ১৯৫৬ সালে গড়ে ওঠে ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা। সেসময় গ্রিন রোডের নাম ছিল ‘কুলি রোড’, যার দু’পাশে ছিল সবুজ শ্যামল ভরা ঘন জঙ্গল। জঙ্গল গেছে, জঙ্গলের সেসব গাছপালার জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের সুউচ্চ ভবন। খানিকটা শ্যামলিমা আজও প্রশান্তি দিচ্ছে ধানমণ্ডি লেকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষগুলো। জঙ্গলটা সবুজ ছিল, তাই সে স্থানের সড়কের নাম হয়েছে গ্রিন রোড।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: ভাদ্র পর্ব
আজকের জনবহুল এলিফ্যান্ট রোড এলাকাটি ১৮০০ সালে ছিল বিশাল গাছপালায় ভরা ছোটখাটো বন। হাতিরপুলে ছিল পিলখানা থেকে ‘পিল’ বা হাতির পালের হাতিরঝিলে যাওয়ার জন্য রেললাইনের ওপর একটি পুল। ভূতেরগলি ছিল গাছপালাভরা গা ছমছম করা অন্ধকারময় গলিপথ। দিগন্ত বিস্তৃত ধানখেত ছিল আজকের ধানমণ্ডি, শুক্রাবাদ, লালমাটিয়া, সংসদ ভবন আর তেজগাঁও ফার্মের বিরাট এলাকা। তেজগাঁওয়ের সেই ফার্ম এখন নেই, সেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে জাতীয় সংসদ ভবন, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, চন্দ্রিমা উদ্যান। সেই শস্যখামার বা ফার্মের প্রবেশদ্বার আজ না থাকলেও তার ‘ফার্মগেট’ নামটি আজও রয়ে গেছে।
ধানমণ্ডির আরেক এলাকা হলো ভূতের গলি। স্থপতি ও কবি রবিউল হুসাইন তাঁর ‘কৃষ্ণ যবনিকা অমিয় সবুজে’ নিবন্ধে লিখেছেন, ‘‘ধানমণ্ডির পূবে সেন্ট্রাল রোড ও আউটার সার্কুলার রোড অঞ্চলে ছিল বিশাল আমবাগান। এই আমবাগানে ছিল বিপ্লবী ত্রৈলক্যনাথ মহারাজের বাড়ি। বাড়ি তো নয় বরং বলা চলে রাজনীতির আখড়া। ভূতের ভয় দেখিয়ে এই আখড়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো অবাঞ্ছিত লোকদের। কিংবদন্তীর নায়ক ত্রৈলক্যনাথের এই কৌশলের ফলেই এক সময় এলাকাটির প্রধান রাস্তার নামই হয়ে দাঁড়ায় ভূতের গলি।’’ মতান্তরে জনৈক ইংরেজ ‘বুথ’ সাহেবের নামানুসারে ওই রাস্তার নাম হয়েছিল ভূতের গলি। ভূতের গলি ছাড়িয়ে রাজাবাজার এমনকি ইন্দিরা রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই আমবাগান। সেসব আমবাগান এখন আর নেই, দু’একটি পুরনো আমগাছ এ এলাকায় রয়ে গেছে সেকালের সাক্ষী হয়ে।
সেকালের ঢাকা আর না থাকলেও এই ঢাকাতেও ঋতুবৈচিত্রের কিছুটা আভাস আমরা পাই আজও। গ্রামে যেমন শরতের আগমণী বার্তা রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করে নদী ও বিলের পাড়ে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা কাশ ফুলেরা। কিন্তু ঢাকা শহরে শরতকে দেখতে ছুটে যেতে হয় ছাতিম গাছের কাছে। শিউলি ও ছাতিমের গন্ধে ভর করে নগরে হাজির হয় শরতের ভোর আর সন্ধ্যা, জগডুমুরের ডালগুলো ভরে ওঠে লাল লাল ডুমুরে। হরিতকী, বহেড়া কিংবা অর্জুনের থোকা ধরা ফলও যুক্ত হয় সেই শারদীয় সংগীতে।

ছাতিম
প্রায় দু’হাজার বছর আগে কবি কালিদাসের ‘ঋতুসংহারম্’ কাব্যের তৃতীয় সর্গে শরৎ-বর্ণনায় ছাতিম ফুলের দেখা পাওয়া যায়, ছাতিম সেখানে সপ্তচ্ছদ ফুল। এই সপ্তচ্ছদই সপ্তপর্ণ। ছাতিমের একটি পল্লবে একটি বোঁটায় সাতটি পাতা থাকায় ছাতিমের আর এক নাম হয়েছে সপ্তপর্ণী বা সপ্তপর্ণা। শরতে ফোটা সে ছাতিম ফুলের তীব্র গন্ধ মাতিয়ে দিয়েছে শরতের প্রকৃতিকে। ফুলে ফুলে শোভিত শরতের এমন চমৎকার প্রকৃতির বর্ণনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? বর্ষার পর স্থির জলাশয় ও নদীতল, সেখানে ফুটে আছে পদ্ম-শাপলা ফুল, সে জলে সাঁতার কাটছে সাদা হাঁসেরা, রাতে শরতের আকাশে যখন চাঁদ উঠল, সে আলোয় ফুটে উঠল ছাতিম ও মালতী ফুলেরা। ভোর হতেই বোঁটা খসে কালিদাসের কাব্যের সেসব ফুল ঝরে পড়ল বনতলে—
‘‘কুমুদে শুভ্র সরোবর আজি মরালে শুভ্র নদীজল,
চন্দ্রকিরণে শুক্লা যামিনী নবকাশ ফুলে ধরণী,
ছাতিম পুষ্পে শুভ্র বনানী মালতী কুসুম বনতল
করতে আজিকে সেজেছে সবাই মোহন শুভ্রবরণী।’’
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর অপু আর দুর্গাকে মনে আছে? ‘‘অপু বলিল কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে, না দিদি? তাহাদের মা বলিল তাহাদের জ্যেঠামশায়ের ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। তাহার পর সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়। ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরাদ্র নৈশবায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাতে বেনুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালার ডালে পাতায় চিকচিক করছে।’’
বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসে ছাতিমের গন্ধ যেন আরও বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে, সেখানে ছাতিমের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, ‘‘পাহাড়ের ওপরে ঘন বন ঠেলিয়া কিছুদূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পরিচিত— প্রথমটা ধরিতে পারি নাই, তারপরে চারিদিকে চাহিয়া দেখি— ধঞ্ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই— এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।’’
অবশ্য, সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার ছাতিমকে পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, ‘‘আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না রবীন্দ্রনাথ এই গাছকে কী কারণে পছন্দ করতেন? না করলে শান্তি নিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে কেন ছাতিম ফুলের পাতা উপহার দেওয়া হতো?’’ ছাতিমের সাথে শিক্ষাঙ্গনের এক মহাযোগসূত্র ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাতিমকে জাতে তুলে দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করে বলে গেছেন—
‘‘ওই যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি।’’

ছাতিমের উপযুক্ত স্থান হলো শিক্ষাঙ্গন। ঢাকার মোহাম্মদপুরে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ভেতরে একই জায়গায় একজোড়া বড় ছাতিমগাছের দেখা পেয়ে তাই মনটা ভরে গিয়েছিল। গাছ দুটোর মাথা ভরে থোকায় থোকায় ফুটে আছে হালকা সবুজাভ সাদা রঙের অসংখ্য ছাতিম ফুল। লাগোয়া গণভবনের সামনের সড়কের বিভাজিকায়ও আছে একটি তরুণ ছাতিম গাছ। সকালে পূবের নরম রোদে ফুলগুলো চিকচিক করছে। তবে রাস্তার ধুলোর প্রলেপে পাতাগুলো বড্ড মলিন। জলবায়ু পরিবর্তনে এখন হেমন্তেও শিশির পড়েনা পাতায় পাতায়। পথের পাঁচালীর বর্ণনা মতো শিশিরার্দ্র ছাতিম ফুলের দেখা পেয়েছিলাম কয়েক বছর আগে হেমন্তকালে বরিশাল শহরের বঙ্গবন্ধু পার্কের ভেতরে। এখনও ঢাকা শহরে ছাতিমের দেখা মেলে শরত-হেমন্তকালে।
প্রকৃতির কি এক অদ্ভুত খেলা! রাতে যে ফুলের এত গন্ধ, সকালেই তা কি করে কর্পূরের মতো উবে যায়! আবার নিশিশেষে বাসি ফুল থেকে ভেসে আসে তীব্র ঝাঁঝাল মদির গন্ধ, সে গন্ধে মাথাটা ঝিমঝিম করে। এক রাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ছাতিমের মাতাল করা গন্ধে মনটা উতলা হয়ে উঠেছিল ওকে দেখার জন্য। সকালে ফিরে এলাম সে পথে। দেখা হলো ছাতিমের সাথে। কিন্তু সে গন্ধ কই? তবে ফুলের স্ফূরণ দেখে মনটা ভরে গেল। কোনও গাছে এত ফুল ফোটে!
কদম যেমন বর্ষার দূত, ছাতিম তেমন শরৎ ও হেমন্তের দূত। এবার দেখলাম ঢাকা শহরে পথতরু হিসেবে বেশ কিছু ছাতিম গাছ লাগানো হয়েছে। ছাতিম গাছ খুব দ্রুত বাড়ে। তিন চার বছরের মধ্যেই গাছগুলো পথচারীদের ছাতার মতো ছায়া দিতে পারে। দু’বছর আগে টাঙ্গাইলে কবি নজরুল পার্কে তিনটে ছাতিম গাছ লাগিয়েছিলাম। পরের বছর দেখলাম সেগুলো অনেক বড় হয়ে ডালপালা ছাড়তে শুরু করেছে।
প্রাচীনকালে ছাতিম গাছের কদর ছিল। টোল বা পাঠশালার প্রাঙ্গণে ছাতিম গাছ লাগানো হতো। শিক্ষক ছাত্রদের নিয়ে সেই ছাতিম গাছের ছায়াতলে বসে পাঠদান করতেন। এছাড়া এর কাঠ দিয়ে বানানো হতো ব্ল্যাকবোর্ড। চকপেন্সিল দিয়ে সে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হতো। এজন্যই কিনা জানিনা, এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের অংশ হিসেবে যুক্ত রয়েছে লাতিন ‘স্কলারিস’ শব্দটি। ছাতিমের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম Alstonia scholaris, গোত্র অ্যাপোসাইনেসী (Apocynaceae)।
একালে ছাতিমের প্রয়োজন হয়ত ফুরিয়েছে, কেউ আর এখন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখে না। তাই এর কাঠেরও দরকার হয় না। সচরাচর ছাতিম গাছ কেউ লাগায় না। তবু সারা দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছাতিম গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর কারণ, ছাতিম গাছের বীজের বাতাসে ভেসে চলার অদ্ভুত ক্ষমতা। ছোট কাঠির মতো বীজের সাথে প্রান্তে থাকে পশমের মতো অঙ্গ। ফল ফেটে বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে তা বাতাসে ভেসে ভেসে অনেক দূরে চলে যায়। সুবিধা মতো জায়গায় পড়লে সেখানেই ছাতিম গাছ গজিয়ে ওঠে।
লেখক সমরেশ মজুমদার অবশ্য ছাতিমের গন্ধে বিরক্ত হয়ে সে গাছ কাটার জন্য কলকাতা সিটি কর্পোরেশনে একবার নালিশ জানাতে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ছাতিম এক বিষাক্ত গাছ, এর ফুলের গন্ধে তাঁর নাকি তীব্র মাথাজ্বালা শুরু হয়। তাঁর শোয়ার ঘরের পাশেই ছিল একটা ছাতিম গাছ। সেটিকে সরানোর জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাতিম প্রীতির কথা আগেই বলেছি। তাঁর বৃক্ষরোপণ উৎসব কবিতায় তিনি যা লিখেছেন, ছাতিম গাছ দুটোকে দেখে সে কথাগুলোকেই বড্ড সত্যি বলে মনে হলো—
‘‘পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।’’
ফুল ফোটা ছাতিমের ঝাঁকরা মাথা শরতের নীল আকাশ ছুঁতে চায়। তার ছায়ায় রয়েছে পথিকবন্ধুর জন্য খোলা আমন্ত্রণ। ছাতিম ফুলের গন্ধে তাই বার বার ছুটে যেতে মন চায় তার কাছে। ছাতিম পবিত্রতার প্রতীক, ভারতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যবৃক্ষ। বিশাল ছাতিম ছায়া তো ধ্যানের স্থান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ধ্যানে শান্তি নিকেতনে শিক্ষার্থীদের বসিয়েছিলেন ছাতিম তলায়।
নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা তাঁর শ্যামলী নিসর্গ বইয়ে ঢাকা শহরে ছাতিম সম্পর্কে লিখেছেন, ‘‘ঢাকায় ছাতিমের সংখ্যা খুবই কম। পি.জি. হাসপাতালের পাশে, ফজলুল হক হলের পুকুরপাড়ে, সার্কিট হাউজের উল্টোদিকে একটি করে এই গাছ চোখে পড়ে। ঢাকাবাসী তাই ছাতিমের প্রস্ফুটন এবং উদ্দাম গন্ধপ্রবাহের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন।’’ ১৯৬৫ সালে তিনি ঢাকা শহরে ছাতিমগাছের অন্যতম অবস্থান হিসেবে পি.জি. হাসপাতালকে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়) নির্দেশ করেছেন। সেখানে ছাতিম বৃক্ষ আছে। তবে সবচেয়ে বয়স্ক ও পুরনো ছাতিম গাছ রয়েছে রমনা পার্কের মধ্যে ও বেইলী রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রাঙ্গণে। এছাড়া এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলার প্রবেশ পথের বাম পাশে রয়েছে একটি বড় ছাতিম গাছ। পুরনো আরেকটি ছাতিম সহজেই চোখে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশে হাকিম চত্বরে। ছাতিম আছে বাংলা একাডেমির সামনের ফুটপাতে আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিন নেতার মাজারের কাছেও। মিরপুর-২ নম্বর সেকশনে কেন্দ্রীয় মন্দিরের পাশে একটি সরকারি অফিস প্রাঙ্গণে আছে সুবিশাল এক ছাতিম। এছাড়াও ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু ছাতিম চোখে পড়ে— বলা ভালো শরত-হেমন্তে পথ চলতে গিয়ে ছাতিমের তীব্র গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারে।

শিউলি
শিউলি ফুল হলো শরতের প্রতীক। কবি কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম শরতের শিউলিকে সাহিত্যে নিয়ে এনেছেন নানাভাবে। কবি কালিদাসের কাছে যে শিউলি পুরুষ-চিত্ত-উতলা, নজরুলের কাছে সে শিউলি আবার বিধবার হাসি, শিউলি আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রশান্ত শিউলি। তবে বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আরণ্যক উপন্যাসে শিউলি ফুলের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়—
‘‘দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘনঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনো উঁচু-নিচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরনা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝরনার উপলাকীর্ণ তীরে। আরো কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে, বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল, নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল— বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মতো মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।’’
বিভূতিভূষণের বর্ণনায় শুধু শিউলি নয়, শরতে ফোটা অন্যান্য আরও অনেক ফুলের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সে বর্ণনায় তিনি শিউলিকে শরতের বৃক্ষ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।
কালিদাস তাঁর ‘ঋতুসংহার’ কাব্যের তৃতীয় সর্গে শরতের উপবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে শিউলিকে ডেকে এনেছেন। লিখেছেন:
‘‘শেফালি ফুলের রঙে রাঙা উপবনে
পাখির কাকলীগান উঠিয়াছে বাজি,
হরিণী-নয়ন-কমল পাইছে শোভা
পুরুষ-চিত্ত উতলা করিছে আজি।’’
শিউলির অনেক নাম— শেফালি, শেফালিকা, পারিজাত ইত্যাদি। তবে এদেশে মাদারকে পারিজাত নামে অভিহিত করায় শিউলির এ নাম আমাদের অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু তাতে কি? ভারতবর্ষের এক উপকথায় শিউলি পরিচিতি পেয়েছে পারিজাত নামে। শেফালি ফুলের সংস্কৃত নাম পারিজাত। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ও পৌরাণিক কাহিনীতে পারিজাত ফুলের উল্লেখ রয়েছে। ভাগবতপুরাণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে সমুদ্র মন্থনের সময় পারিজাতের উৎপত্তি হয়েছিল। সেই পারিজাত গাছ স্বর্গরাজ ইন্দ্রের স্বর্গোদ্যানে লাগানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে সেই পারিজাত গাছ নিয়ে যুদ্ধ হয়। মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের তৃতীয় সর্গে পারিজাতের উল্লেখ রয়েছে। দেব ও অসুরদের সমুদ্র মন্থনের সময় ক্ষীরসাগর থেকে উঠেছিল পারিজাত। পারিজাতক নামে নাগরাজের এক কন্যা ছিল। সূর্যদেব তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। পরে সূর্যদেব অন্য একটি নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেন। এই দুঃখে নাগরাজকন্যা পারিজাতক দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের স্থানেই এই ফুলগাছের জন্ম হয়। সূর্যদেবের প্রতি অভিমানে পারিজাতক সূর্যের মুখ আর দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। সেজন্য সূর্য উদয়ের আগেই সে ঝরে পড়ে।

শিউলির এ স্বভাবের সাথে তার ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামেরও মিল রয়েছে। শিউলির ইংরেজি নাম ‘নাইট জেসমিন’, অন্য নাম ‘ট্রি অব সরো’— এগুলোর অর্থ ‘নিশি পুষ্প’ ও ‘বিষাদ বৃক্ষ’। পৌরাণিক এ উপকথা বা গল্পের সাথে এসব নামের সাযুজ্য পাওয়া যায়। শিউলির উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম নাইকট্যানথেস আরবর-ট্রিসটিস (Nyctanthes arbor-tristis) গোত্র ওলিয়েসী। শেফালির উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের প্রথম অংশ নিকট্যানথাস অর্থ রাতের এবং আরবরট্রিসটিস অর্থ বিষাদিনী। এ নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে এ ফুলের দুঃখগাঁথা। রাতে ফুল ফোটে, সকালেই ঝরে পড়ে। শেফালি যেন অসূর্যম্পশ্যা, সূর্যের ছোঁয়া তার সহ্য হয় না।
শিউলি গাছ মাঝারি আকারের কাষ্ঠল গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ প্রকৃতির গাছ। গাছ ১৫ থেকে ২০ ফুট লম্বা হয়। কাণ্ড অসমৃণ, ধূসর ও মধ্যম পুরু বাকল। পাতা অমসৃণ বা খসখসে। পাতার অগ্রভাগ সূঁচালো ও কিনারা করাতের দাঁতের মতো খাঁজকাটা, রঙ চকচকে সবুজ, নিচের পিঠ সাদাটে সবুজ। পাতার বোঁটার দিকটা কিছুটা ডিম্বাকার, পাতা দেখতে অনেকটা পানপাতার মতো। তবে বোঁটার কাছে পান পাতার মতো খাঁজ নেই। ফুলের পাঁপড়ির রঙ সাদা, বোঁটার রঙ কমলা। বোঁটা নলের মতো। পাঁপড়ির সংখ্যা ছয়টি। পাঁপড়ির সংখ্যা পাঁচ থেকে আটটিও হতে পারে। ফুল সুমধুর সুগন্ধযুক্ত। ডালের আগায় থোকা ধরে ফুল ফোটে। ফুল ফোটে শরতকালে। তবে বছরের অন্য সময়ও দু’একটি ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফল হয় শীতকালে। সে সময় গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়। ফল বোতামের মতো চ্যাপ্টা, ফলের আকৃতিতে একটি খাঁজ দ্বারা বিভক্ত দুটি খণ্ডে দেখা যায়। প্রতিটি খণ্ডের ভেতরে একটি বীজ থাকে। কাঁচা ফলের রঙ সবুজ। ফল পাকলে ও শুকালে বাদামি হয়ে যায়। বীজ থেকে চারা করা যায়।
শিউলি শুধু ফুলের গাছ না, এর অনেক ঔষধি গুণও আছে। এ ফুল রঙ তৈরি ও সুগন্ধি তেল তৈরি করতেও ব্যবহার করা হয়। সেই রঙ খাদ্যদ্রব্য রঙ করতে কাজে লাগে। বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলংকার অধিকাংশ মন্দির প্রাঙ্গণে শিউলি ফুল গাছ আছে। শিউলি ফুল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও থাইল্যান্ডের কাঞ্চনবুড়ির রাজ্যফুল।
নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ষাটের দশকে ঢাকায় শিউলি গাছের দেখা তেমন পাননি, তিনি তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে সে কথা লিখেছেন: ‘‘ঢাকায় এ তরু দুস্প্রাপ্য, প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ (বর্তমান জগন্নাথ হল) ও পাবলিক লাইব্রেরির প্রাঙ্গণ ব্যতীত পথের পাশে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে শেফালি তেমন একটা চোখে পড়ে না।’’ কিন্তু এর পর থেকে পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরের অনেক স্থানেই শিউলি চারা রোপণ করা হয়েছে। জগন্নাথ হলের পুকুর পাড়ে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে সারি করে লাগানো সাতটি শিউলি গাছ। পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণের শিউলি গাছ কাটা পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পাশে মধুর ক্যান্টিনের প্রবেশ মুখে আছে একটি প্রাচীন বয়স্ক শিউলি গাছ। এছাড়া বেশ কয়েকটি বয়স্ক শিউলি গাছ রয়েছে রমনা পার্কের উত্তরপূর্ব প্রান্তের সীমানা ঘেঁষে। শিউলি গাছ আছে কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি সৌধ প্রাঙ্গণে ও রামকৃষ্ণ মিশন মন্দির প্রাঙ্গণে।

অর্জুন
গ্রীষ্মকালে ফোটে অর্জুন ফুল, ফল হয় বর্ষা-শরতে। লম্বা পুষ্পমঞ্জরিতে দুধের ক্ষীরের মতো সে ফুলের রং ও রূপ, যেন তা কোনও ক্ষীণকটি তরুণীর কোমরবিছা, সকালের আলোয় আলো ঝলমল। কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যের ষোড়শ সর্গে গ্রীষ্মকালে প্রস্ফুটিত সেই অর্জুনমঞ্জরীর এক মনোহর ছবি এঁকেছেন—
‘‘অর্জুনফুল মঞ্জরীগুলি চূর্ণ পরাগ মেখে
পিঞ্জর রঙে করিল ধারণ অপরূপ রূপ মরি,
ধূর্জটি-রোষে ভস্ম মদন, চূর্ণ ধনুর্গণ,
মনে হলো রাজে সে ধনুকগুণ কুসুমের রূপ ধরি।’’
কবি নজরুলের গানেও ছড়িয়ে আছে অর্জুনের প্রশস্তি। কবি কালিদাসের মতোই তাঁর কাব্য নায়িকারা পুষ্পশোভিতা, কানে অর্জুন ফুলের দুল আর গলায় কদম ফুলের মালা—
‘‘স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এসো মালবিকা
অর্জুন-মঞ্জরি-কর্ণে গলে নীপ মালিকা, মালবিকা॥
ক্ষীণ তন্বী জল-ভার-নমিতা
শ্যাম জম্বু-বনে এসো অমিতা
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি থালিকা, মালবিকা॥’’
বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে অর্জুনগাছের ভেষজ ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে অন্তত ৩,০০০ বছর পূর্ব থেকে ভেষজ গাছ হিসেবে অর্জুন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিস্ময়কর ভেষজগুণের কারণে অর্জুনগাছকে বলা হয় হৃৎপিণ্ডের অভিবাবক বা ‘‘Guardian of the heart’’। মহাভারতে অর্জুন ছিলেন পাণ্ডবদের রক্ষাকারী বীর যোদ্ধা। তেমনি এ গাছও মানুষের হৃৎপিণ্ড তথা জীবনের রক্ষাকারী। এজন্যই মহাভারতের চরিত্র অর্জুনের নামের সাথে মিল রেখে এ গাছের নাম রাখা হয়েছে অর্জুন। অর্জুন নামের আর একটি তাৎপর্য রয়েছে। এ শব্দটিকে বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় অর্জ+উনন্। এই অর্জ অর্থ বল; অর্জুন হৃৎপিণ্ডে বলদান করে বলে তার নাম অর্জুন। বৈদিক শব্দাভিধানে অর্জুনের এরূপ অর্থ করা হয়েছে। অর্জুন বা অর্জুনা গাছের ইংরেজি নামও— arjun tree। অর্জুনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম টার্মিনালিয়া অর্জুনা (Terminalia arjuna) ও গোত্র কম্ব্রিটেসী (Combretaceae), অর্জুন গাছের উৎপত্তি ভারত ও শ্রীলংকায়, সে অর্থে অর্জুন আমাদের দেশি গাছ।

বাংলাদেশের সর্বত্র অর্জুন গাছ রয়েছে। পার্কে ও রাস্তার ধারেও এ গাছ পথতরু হিসেবে লাগানো হয়। তবে নদী ও খাল তীরবর্তী এবং শুষ্ক জলাশয়ের ধারে অর্জুন গাছ বেশি জন্মে। বীজ দ্বারা অর্জুনগাছের বংশবৃদ্ধি হয়। এক কেজিতে প্রায় ৭৭৫-৮০০টি বীজ হয়। বীজ শক্ত। তাই নরম করার জন্য বীজ মাটিতে বা বীজতলায় বোনার আগে ৩৬ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। গত বছরে সংগৃহীত বীজ বুনতে হয়। ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে বীজের গজানোর ক্ষমতা ৩ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।
অর্জুন বৃক্ষ প্রকৃতির চিরসবুজ বা স্বল্প পত্রঝরা প্রকৃতির গাছ। গাছ প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিটার লম্বা হয়, ডালপালা বিস্তৃত ও নিচের দিকে ঝুলানো। পাতা লম্বাটে ও কোণাকৃতি, কচি পাতা হালকা বাদামি, বয়স্ক পাতা সবুজ, মসৃণ। বাকল মসৃণ, ধূসর। ফুল হালকা হলুদ, ফুল ফোটে এপ্রিল-জুন মাসে, এর পর ফল ধরে। ফল কাষ্ঠল, ২-৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ফল পাঁচটি খাঁজ বা ডানাযুক্ত, দেখতে অনেকটা ছোট কামরাঙার মতো।
সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে ফল পাকে। গাছ লাগানোর ৬-৭ বছর পর ফল ধরতে শুরু করে। সাধারণত গ্রীষ্মকালে নতুন পাতা আসে। গাছ চিরসবুজ হলেও বুড়ো পাতা ঝরে যায় ও নতুন পাতা আসে। কখনও কখনও খুব অল্প সময়ের জন্য গাছের সব পাতা ঝরে যায়। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে নতুন পাতা আসে। এ সময় পুরনো পাতা ঝরতে থাকে।
ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অর্জুন এক পবিত্র গাছ। কেননা, এ গাছের পাতা ও ফুল দেবতা বিষ্ণু ও গণেশ পূজায় লাগে। তবে অর্জুন গাছের বেশি কদর তার ভেষজ গুণের কারণে। বাণিজ্যিকভাবে অর্জুনগাছ থেকে নানারকমের আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে বাজারজাত করা হয়। এমনকি অর্জুনের চা ও ক্যাপসুলও আছে। ওষুধ হিসেবে অর্জুনের প্রধানত বাকল ব্যবহার করা হয়। এজন্য অর্জুনকে নিয়ে দুর্মুখদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে— ‘‘কারো উপকার করলে কি হয় অর্জুন গাছই তার প্রমাণ।’’ অন্যান্য অংশও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাকল পানিতে ভিজিয়ে সেই পানি পান করা হয়। এশিয়ার অনেক দেশে রাস্তার ধারে শোভাবর্ধক পথতরু হিসেবে অর্জুনগাছ লাগানো হয়। ভারত ও শ্রীলংকায় কফি বাগানের ছায়াতরু হিসেবে অর্জুনগাছ লাগানো হয়।
নির্মাণকাজ, নৌকা ও গাড়ি তৈরির কাঠ হিসেবেও অর্জুনগাছ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও প্লাইউড তৈরিতেও অর্জুনকাঠ ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের কাঠ বেশ শক্ত। জ্বালানি কাঠ ও চারকোল বা কাঠকয়লার জন্যও অর্জুন কাঠ উত্তম। ভূমিক্ষয় রোধে অর্জুনগাছ অতুলনীয়। ভারতে ট্যানিন তৈরিতে অর্জুনগাছের বাকল, পাতা ও ফল ব্যবহার করা হয়। অর্জুন ট্যানিন দিয়ে চামড়া রঙ করা হয়। বাকল প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ। তাই ভারতে বাকল পুড়িয়ে চুন তৈরি করে তা পানের সাথে খাওয়া হয়। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অর্জুনের ছাল বা বাকল। পূর্ণবর্ধিত একটি অর্জুনগাছ থেকে বছরে প্রায় ১৫-২০ কেজি শুষ্ক ছাল পাওয়া যায়। সাধারণত ৩ কেজি কাঁচা ছাল শুকিয়ে ১ কেজি শুষ্ক ছাল পাওয়া যায়। গাছের বয়স ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত ছালের উৎপাদন বাড়তে থাকে। গাছ প্রায় ৬০ বছর বাঁচে।

সুপ্রাচীনকাল থেকে অর্জুনের বহুমূখী ভেষজ গুণের কারণে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অর্জুন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে হৃদযন্ত্রের টনিক তৈরিতে অর্জুন এক মূল্যবান বৃক্ষ। হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহী নালীসমূহকে ভালো রাখতে অর্জুনের কোনও জুড়ি নেই। এ ছাড়া ইনসুলিন হরমোনের ওপরও অর্জুনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে যা ডায়াবেটিস রোগীদের ভালো রাখতে সাহায্য করে। অর্জুন গাছের কষ বা ট্যানিন এন্টিঅক্সিডেন্টের একটি উত্তম উৎস যা দেহের বার্ধক্যকে বিলম্বিত করে দেয়। অর্জুন রক্ত পরিশোধনের কাজ করে ও মূত্রাশয়ের কাজ ভালো রাখে। মেয়েদের হরমোন চক্র নিয়ন্ত্রণ ও অতিস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে দেহকে ভালো রাখে। রক্তের কোলেস্টরল কমানোর জন্য অর্জুন উত্তম। কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়লে রক্তনালীতে ব্লক তৈরি হয় যা হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ফুসফুস ভালো রাখতেও অর্জুন সাহায্য করে এতে শ্বাসক্রিয়া ভালো থাকে। দেহের ক্লান্তি দূর করে কর্মক্ষম রাখতে অর্জুন সাহায্য করে। দেহের যে কোনও বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হ্রাসে অর্জুন কাজ করে। হাড় ফেটে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে অর্জুন তা দ্রুত জোড়া লাগতে ও ক্ষত পূরণ করতে সাহায্য করে।
নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে ঢাকা শহরে অর্জুন সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘যদি কোনদিন পাবলিক লাইব্রেরি থেকে সোজা বক্সীবাজার রোড দিয়ে পশ্চিমে যাওয়ার সময় পুরনো প্রাদেশিক পরিষদের (বর্তমান জগন্নাথ হল) কাছাকাছি পৌঁছে পথের দুপাশে তাকান তখন দু’সারি বিশাল মহীরুহ অবশ্যই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এদের দিকে তাকানো মাত্রই হতভাগ্য গাছগুলোর কাণ্ডের দুর্দশা আপনার চোখে পড়বে। বছরের পর বছর কে বা কারা অত্যন্ত নির্মমভাবে এদের বাকল চেঁছে নিয়ে গেছে এবং নিচ্ছে। ঢাকার বেইলী রোডে আর একটি অর্জুন বিথী আছে এবং তাও অনুরূপ দুর্দশাগ্রস্ত।’’ সৌভাগ্য যে অর্জুন গাছগুলোর সাথে এখন সেই নির্মমতা আমাদের দেখতে হচ্ছে না। কেননা, গাছগুলো এখন আর সেখানে নেই। আণবিক শক্তি কমিশনের কাছে দ্বিজেন শর্মা যে অর্জুন গাছগুলো ১৯৬৫ সালে দেখেছিলেন সেগুলোও বর্তমানে নেই।
ঢাকা শহরে অর্জুনগাছের দেখা মেলে প্রধানত পার্কে ও রাস্তার ধারে। শের-ই-বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে রাস্তার ধারে সারি করে অনেকগুলো অর্জুন গাছ লাগানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে পুরনো (হয়ত শতবর্ষী) অর্জুন গাছ রয়েছে রমনা পার্কের ভিতরে। পূব দিকের অরুণোদয় গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পিচের রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে কুসুম বাগের মধ্যে রয়েছে সে গাছটি। অর্জুন গাছের চেহারা দেখে আসলে বয়স আন্দাজ করা যায় না। কারণ গাছটির বৃদ্ধি হয় বেশ ধীরে। বয়স্ক গাছে বাকল তুলতে তুলতে শেষে তার গোড়ার দিকটা আর স্বাভাবিক চেহারায় থাকে না, স্বভাবগত কারণেও হয়ত অর্জুনের গুড়িতে টিউমারের মতো ফোলা ফোলা অসংখ্য গিঁট তৈরি হয়। ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে কাবাব ঘরের পাশে থাকা অর্জুন গাছটিকে দেখলে তাকে এক অনন্য সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক স্থাপত্য সম্বলিত বনসাইয়ের মতো মনে হয়। ধানমণ্ডি সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের মধ্যে গ্রিন রোডের পাশে সীমানা প্রাচীরের কোলে রয়েছে অর্জুন গাছ।

আকাশমণি
এক বৈশাখের সকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গলটায় ঘুরছিলাম, সাথে ছিলেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের উদ্ভিদ গবেষক আবদুর রহিম। অনেকগুলো আকাশমণি গাছ। তার তলায় সবুজ ঘাসের মধ্যে রহিম ভাই হঠাৎ কি যেন আবিষ্কার করলেন, বললেন, আকাশমণির চারা খুঁজে পেয়েছি। মনে মনে ভাবলাম, এ আর এমন কি? এই চারা নিয়ে রহিম ভাইয়ের এত কৌতুহল কেন? দুজনে বসে পড়লাম সেখানে, চারাগুলোর কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। ইঞ্চি দুয়েক লম্বা চারায় দুটি পাতা ছেড়েছে, পাতাগুলো তেঁতুল বা বাবলা পাতার মতো। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো যে, ওগুলো আকাশমণির চারা। আকাশমণির পাতা অন্যরকম, কাস্তের মতো বাঁকা চ্যাপ্টা পত্রবৎ ফলক। আর এটা তো বাবলা পাতার মতো। রহিম ভাই বললেন, বীজ ফুটে চারা বেরোনোর পর আকাশমণির পাতা এরকমই থাকে। কিন্তু পরে সেসব পাতা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, সবুজ যে পাতাগুলো আমরা আকাশমণি গাছে দেখি সেগুলো প্রকৃত পাতা না, পর্ণবৃন্ত, অর্থাৎ পাতার মতো আকৃতির পাতার বোঁটা। চারাটির পাতাগুলো দেখে তাই আরও মনোযোগ দিয়ে কথাটার মানে বুঝার চেষ্টা করলাম। সত্যিই তাই। দেখলাম, একটা পাতার মাথার দিকে একটি পত্রকের রূপান্তর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বাবলার মতো আর সে পাতাটি দেখা যাচ্ছে না, সেটি ধীরে ধীরে কাস্তের মতো রূপ ধরেছে। আকাশমণির এমন নিবিড় সান্নিধ্য না পেলে এরূপ একটি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ত জীবনে কখনও দেখাই হতো না।

আর একবার বিস্মিত হয়েছিলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাবু ডাইংয়ের উষর উত্তল জমিনে গিয়ে। খটখটে শুকনো মাটির বুকে আহা কি চমৎকার সবুজের লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশমণির বনে বনে, প্রতিটি গাছের পত্রাঞ্চল ভরে আছে হলদে রঙের ফুলে ফুলে। খাটো খাটো পুষ্পমঞ্জরিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র ফুলের স্রোত যেন মাতিয়ে তুলেছে মৌমাছিদের, মধুগন্ধে আমোদিত চারদিক।
বিদেশিনী আকাশমণির এতো রূপ? অখচ এই শোভাময়ী অরণ্যবৃক্ষটি নিয়ে আমাদের কতই না উদ্বেগ! এই সুন্দরী লাস্যময়ী তরুটি নাকি পরিবেশবান্ধব নয়! শেষবার মুগ্ধ হলাম এ বছর বৈশাখে ঢাকার চন্দ্রিমা উদ্যানে গিয়ে। সেখানে আকাশমণি গাছের ছড়াছড়ি। গ্রীষ্মের দুপুরে ঝাঁ রোদে আঁকাবাঁকা ফিতার মতো জড়ানো প্যাঁচানো ফলগুলো শুকিয়ে মচমচে বাদামি হয়ে দলা পাকিয়ে ঝুলছে ডালের আগায়। ফলের খোসা ফেটে ভেতর থেকে বীজগুলো আলগা হয়ে বেরিয়ে উঁকি দিয়ে যেন দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বীজ তো নয় যেন কোনও কৃষ্ণরত্ন— কষ্টি পাথরের কণা, সোনালী সুতোয় দুলের মতো দুলছে হাওয়ায়। আকাশমণির বীজ থেকে বীজের, অর্থাৎ জীবনচক্রের এরূপ দর্শনের সুযোগ হয়ত সবার ভাগ্যে জোটে না, এ কথা ভেবে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। যতটুকু রাগ ছিল বিদেশিনী আকাশমণিকে নিয়ে এসব বিস্ময়কর প্রাকৃতিক রূপ দর্শনে তার খানিকটা প্রশমিত হলো।

আকাশমণির সাথে আমার পরিচয় সেই যৌবন বয়সে, আশির দশকে— ময়মনসিংহে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। থাকতাম শাহজালাল হলের পূর্ব ব্লকে। এ ব্লকের পিছনেই ছিল একটা ঝিল। ঝিল আর হলের সীমানা প্রাচীরের মাঝে রাস্তা। সে রাস্তার দু’পাশে ছিল সারি করে লাগানো ছিল অনেকগুলো আকাশমণি গাছ। গাছপালার প্রতি তখন তেমন আগ্রহ ছিল না, তবে সেসব গাছের তলা দিয়ে শরতের সকালে যখন হেঁটে যেতাম, রাস্তা ভরা হলদে গুঁড়ো ফুলে চরণ দুটো যেন ধন্য হতো। কেউ একজন সহপাঠী বলেছিল, ও গাছের নাম ‘অ্যাকাশিয়া’, কাঠ খুব শক্ত, কাঠ দিয়ে বাস-ট্রাকের বডি বানায়। অ্যাকাশিয়া কি করে যে আকাশমণি নাম ধারণ করল, তা জানা নেই।
তবে, এ গাছের সোনারঙা ঝুলন্ত মঞ্জরির রূপে মুগ্ধ হয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বাংলা নাম দিয়েছিলেন— ‘সোনাঝুরি’। কিন্তু এ নামে এ দেশে আরও দুটো গাছ রয়েছে, সোনাইল গাছকেও বলা হয় সোনাঝুরি, গোল্ডেন শাওয়ারকেও কেউ কেউ বলেন সোনাঝুরি লতা। এ কারণে অ্যাকাশিয়ার নাম সোনাঝুরি বললে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। কারও কারও কাছে আকাশমণি হয়ত সোনার গাছ। কয়েক বছরের মধ্যেই ছোট গাছগুলো সাইজ করে কেটে কাগজকলে পাঠানো যায়, বড় গাছের কাঠ বেচে অনেক টাকা আসে। কিন্তু যারা এ গাছ লাগিয়েছেন তারা কি কখনও দেখেছেন যে এসব গাছে পাখি বসে না, পাখির খাওয়ার জন্য কোনও ফল নেই এ গাছে! যেখানে আকাশমণি গাছ থাকে তার তলায় তো অন্য কোনও গাছও জন্মে না। আবার মাটি থেকে গাছগুলো প্রচুর পানি শুষে নেয়। ঝরা শুকনো পাতা ভালো জ্বালানিও হয় না। এগুলোই আকাশমণির দুর্ভাগ্য!

অ্যাকাশিয়া এ গাছের গণগত নাম। এই গণে বিশ্বে ১,০৮৪ প্রজাতির গাছ রয়েছে, আকাশমণি এর একটি প্রজাতির গাছ। এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম অ্যাকাশিয়া অরিকুলিফরমিস (Acacia auriculiformis), গোত্র ফ্যাবেসী (Fabaceae), উপগোত্র মাইমোসয়ডি। চিরসবুজ বৃক্ষ প্রকৃতির গাছ। পত্রবৎ পর্ণবৃন্ত, এটা যে সত্যিকার পাতা না তা তার শিরাবিন্যাস দেখলেই বোঝা যায়। আকাশমণি দ্বিবীজপত্রী গাছ, তাই এর পাতার শিরা জালিকাবিন্যাস হওয়া উচিত। কিন্তু আকাশমণির চামড়ার মতো শক্ত পাতার শিরাবিন্যাস সমান্তরাল, অনেকটা একবীজপত্রী ধান বা নারিকেল পাতার মতো। পর্ণবৃন্ত কাস্তে বা ছুরির ফলার মতো আকৃতিবিশিষ্ট। ফুল খুব ছোট, ঝুলন্ত মঞ্জরিতে অনেকগুলো ফুল ফোটে, ফুলের রং হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ। ফুলে মৃদু সুগন্ধ আছে। ভাদ্র-আশ্বিন ফুল ফোটার সময়। ফল ফিতার মতো ও আঁকা বাঁকা। কাঁচা ফল সবুজ, পাকলে হয়ে যায় বাদামি। পাকা ফল আপনা আপনি ফেটে যায় ও কালো বীজ ছড়িয়ে পড়ে।
ঢাকা শহরে ষাটের দশকে আকাশমণি গাছের কথা বলতে গিয়ে নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা শ্যামলী নিসর্গ বইয়ে রমনা ও গুলিস্তানের কাছের সড়কের কথা উল্লেখ করেছেন। রমনা ও চন্দ্রিমা উদ্যানে, ঢাকা জিপিওর সামনে, ঢাকা শহরের ঝিল ও বিভিন্ন সড়কের পাশে বর্তমানে অনেক আকাশমণি গাছ আছে। মহাখালী থেকে বনানী চেয়ারম্যানবাড়ি পর্যন্ত যেতে এয়ারপোর্ট রোডের ডানপাশে একটি আকাশমণি বিথী আছে। আকাশমণি গাছের এখন ঢাকা শহরে কোনও অভাব নেই।

বাজনা
গাছের পাতার বিন্যাস অনেকটা আমড়া গাছের মতো বলে প্রথম দেখে বাজনাকে আমড়া গাছ বলে ভুল হতে পারে। কাছে গেলে দেখা যায় গাছের কাণ্ডভর্তি শুধু বড় বড় কাঁটা আর কাঁটা। এজন্য এ গাছের ইংরেজি নাম ‘পিকল্ ট্রি’। অন্য বাংলা নাম কাঁটাহরিণা, তামবুল ও বাজিনেলি। বাজনা একটি অরণ্যবৃক্ষ।

বাজনা গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম জ্যান্থোজাইলাম রেটসা (Zanthoxylum rhetsa) ও গোত্র রুটেসী (Rutesceae)। লেবুগোত্রীয় গাছ হওয়ার কারণে কি না জানিনা, বাজনা পাতা ডললে তা থেকে লেবুর ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সহজে বাজনা গাছ চেনা যায়। বাজনা মাঝারি আকারের পাতাঝরা স্বভাবের বৃক্ষ। গাছ ১৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের কাণ্ড ও ডালপালা কাঁটযুক্ত। পাতা যৌগিক। পাতা ডিম্বাকার ও কিনারা অল্প খাঁজকাটা। প্রতিটি অনুপত্র প্রায় ৭-১২ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতা ডললে এক ধরনের তীব্র ঝাঁঝ বের হয়। পাতায় তৈলগ্রন্থি বা পেলুসিড থাকায় এরূপ গন্ধ হয়। পাতা লম্বা, পত্রদণ্ডের দুপাশে সারি করে বিপরীতমুখীভাবে পত্রকগুলো সাজানো থাকে। প্রতিটি পাতায় ১৬-২৫টি অনুপত্র থাকে। ডালের আগায় চারদিকে ছড়িয়ে থাকে পাতাগুলো।
ফুল ছোট, সাদা বা হালকা হলুদ রঙের। ফল গোলাকার বুটের মতো, থোকায় অনেকগুলো ফল থাকে ডালের আগায়। ফল পাকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। কাঁচা ফলের রং সবুজ, পাকলে ফলের রং লালচে হয়ে যায়। ফল শক্ত। ফলের ভেতরে একটি মাত্র বীজ থাকে। বীজের রং কালো ও চকচকে। বীজ থেকে তেল হয়। তেলের ঘ্রাণ অনেকটা ঘিয়ের মতো। গরম ভাত বাজনার তেল দিয়ে মেখে খেতে খুব মজা লাগে। তেল ঘানি বা কলে ভাঙিয়ে করা হয় না, বাড়িতে বীজ ছেঁচে পানিতে সিদ্ধ করে পানি থেকে ভাসমান তেল তোলা হয়। তেল চর্মরোগে উপকারী। কাঁচা পাতা ও ফল মশলা হিসেবেও খাওয়া হয়। বীজ থেকে চারা হয়।
গাজীপুরের ভাওয়ালের জঙ্গলে গেলে সহজে দেখা মেলে বাজনা গাছের। লাল মাটির শালবনের গাছ। তাই ঢাকা শহরেও বাজনা গাছ অনেকই থাকার কথা। কিন্তু শহর খুঁজে বাজনা গাছের দেখা পেয়েছি মাত্র তিনটি জায়গায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনের পাশে আইবিএ ভবনের প্রবেশ মুখে একটি বড় গাছ আছে। আরেকটি বাজনা গাছ আছে চারুকলার বকুলতলা মঞ্চ ও গ্যালারির মাঝের আঙ্গিনায়। এছাড়া মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ক্যাকটাস হাউজের কাছে বড় একটি বাজনা গাছ আছে।

বন্ধু হই প্রকৃতির
আমেরিকান পরিবেশবাদী লেখিকা রাসেল কারসন পরিবেশ বিষয়ক কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর বিখ্যাত বইটি হলো ‘দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং’ যা আমেরিকায় পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এবং তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন পরিবেশ আন্দোলনের জননী রূপে। তাঁর কথা হলো— ‘‘Man is a part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself।’’ অর্থাৎ ‘‘মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ, এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ মানে অনিবার্যভাবে তা তার নিজের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ।’’ প্রকৃতির সাথে তাই কোনও সংঘাত বা প্রভূত্ব নয়, বরং তার সাথে মিলেমিশে সহাবস্থানই কাম্য। প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে সহজ-সরল জীবন যাপন ও চিন্তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রকৃত সুখ। এই সহজ সত্য ও মিত্রতা যেন আমরা ভুলে না যাই। প্রকৃতির সাথে কোনও বিরোধ নয়, বরং ভালোবেসে তাকে কাছে টেনে নিই, রক্ষা করি প্রকৃতির গাছপালা ও জীব-জড়দের, প্রকৃতি যেমন আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, আমরাও বাঁচাই তাদের। নিজের ও সমগ্র মানব জাতির জন্যই তা হবে মঙ্গলের।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: [email protected]