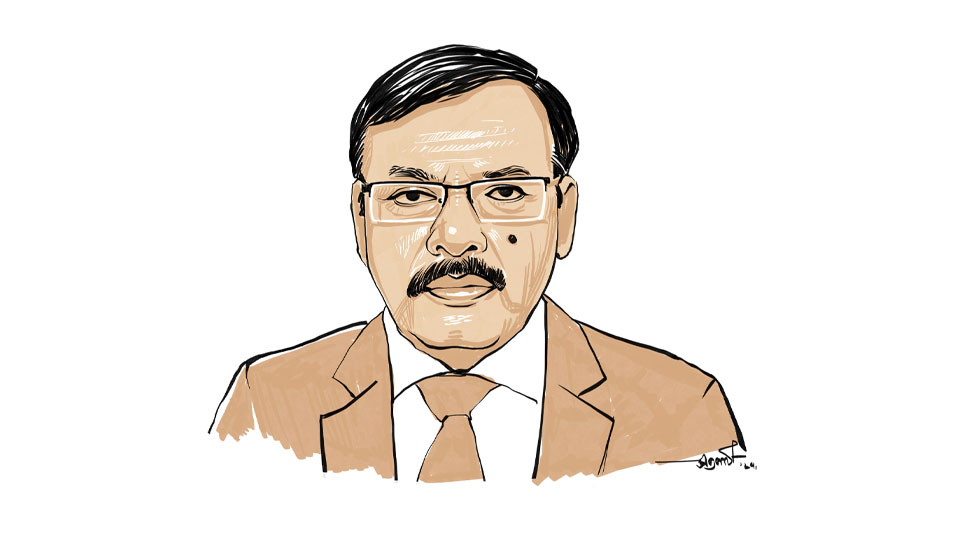নিসর্গী অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন ‘শ্যামলী নিসর্গ’। বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত সে বইটি এখনও ঢাকার বৃক্ষচর্চার আকরগ্রন্থ। তিনি শ্যামলী নিসর্গ লিখে রেখে না গেলে সেকালের ঢাকার পথতরুর বৃত্তান্ত আমরা হয়ত জানতে পারতাম না। কিন্তু ঢাকার সেসব পথতরুর এখন কী অবস্থা? আজও কি সেগুলো বেঁচে আছে? দ্বিজেন শর্মার আত্মজ সে বৃক্ষরা এখন ঢাকার কোথায় কীভাবে আছে সে কৌতুহল মেটানো আর একালের পাঠকদের সঙ্গে ঢাকার সেসব গাছপালা ও প্রকৃতির পরিচয় করিয়ে দিতে এই লেখা। কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মৃত্যুঞ্জয় রায় সরেজমিন অনুসন্ধানে তুলে ধরছেন ঢাকার শ্যামলী নিসর্গের সেকাল একাল। ঢাকার প্রাচীন, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও অনন্য পথতরুর বৃত্তান্ত নিয়ে সকাল সন্ধ্যার পাঠকদের জন্য বাংলা বারো মাসে বারো পর্বের ধারাবাহিকের আজ পড়ুন কার্তিক পর্ব।
ঢাকা শহরের বৃক্ষ বৃত্তান্ত: আশ্বিন পর্ব
বিভিন্ন শাসনামলে এ দেশের নগর উদ্যানের শোভা বাড়ানোর জন্য বিদেশ থেকে গাছপালা আনা হয়। জানা যায় বরিশাল শহরে ১৮৯৬ সালে ‘বেলস পার্ক’ নামে একটি পার্ক স্থাপন করা হয় যে পার্কে তখন রয়্যাল পাম গাছ বিদেশ থেকে এনে সারি করে লাগানো হয়। বিদেশ থেকে আনা গাছপালাকে প্রবর্তিত তরু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধারা মোগল আমলে ছিল সবচেয়ে বেশি। মোগলরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাগান ও উদ্যান গড়ে তুলতে অনেক বিদেশি গাছ নিয়ে আসেন। কোম্পানি আমলেও ইংরেজ, পর্তুগীজ, ফরাসি ও আর্মেনীয় বণিক এবং শাসকরা বেশ কিছু বিদেশি গাছ এ দেশে প্রবর্তন করেন যেগুলো অতীতে ছিল না। ঢাকার বলধা গার্ডেনের প্রকৃতিপ্রেমিক নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এবং জামালপুরের চৈতন্য নার্সারির ঈশ্বর চন্দ্র গুহ বেশ কিছু বিদেশি গাছ নানা দেশ থেকে এ দেশে নিয়ে এসে তাঁদের বাগানে লাগান। এ ধারা এখনও চলমান রয়েছে। সম্প্রতি নকাচুয়া, চায়না ডল, চীনা বট, ত্রিকোণ বট ইত্যাদি গাছ এ দেশে নতুন এসেছে। ধারণা করা হয় প্রায় তিনশ প্রজাতির বিদেশি বৃক্ষ গত কয়েক দশকে এদেশে প্রবেশ করেছে। এগুলোর মধ্যে ইউক্যালিপটাস, মেহগনি ও বিভিন্ন পামগাছ অন্যতম। এ পর্বে ঢাকা শহরের কিছু বিদেশি গাছের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ইউক্যালিপটাস
এই গাছ দেখে সেই ‘অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড’ রূপকথার কথা মনে পড়ে। কত আজব গাছ যে সেই ওয়ান্ডারল্যান্ডে ছিল! কিন্তু এই পৃথিবীতে এখনও আছে সে রকমের কিছু আজব গাছ। মনে হবে, কেউ যেন অ্যালিসের সেই ওয়ান্ডারল্যান্ড থেকে এই গাছটাকে তুলে এনে পৃথিবীর মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। রঙধনুর সাতরঙ মেখে সে গাছ দাড়িয়ে আছে গভীর বাদল বনে, নাম তার রঙধনু গাছ। রেইনবো ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus deglupta) গাছের গা জুড়ে যেন রয়েছে ফালি ফালি রংধনুর আলপনা— লম্বালম্বিভাবে সাজানো বাকলের সেই রঙ এই গাছকে করেছে বৈচিত্র্যময়, অন্যান্য ইউক্যালিপটাস গাছগুলো থেকে আলাদা। এই গাছগুলোকে দেখে মনে হবে কোনও রঙের কোম্পানি হয়ত ইউক্যালিপটাস গাছগুলোকে বেছে নিয়েছে তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য। কিন্তু এই প্রজাতির ইউক্যালিপটাসগাছ আমাদের দেশে নেই। এ প্রজাতির গাছ ঢাকা শহরে না থাকলেও বিদেশি ইউক্যালিপটাসের অন্যান্য প্রজাতির গাছের অভাব নেই।

অ্যান্টার্কটিকা ছাড়া বিশ্বের প্রায় সব মহাদেশেই ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। মির্টেসী গোত্রের ইউক্যালিপটাস গণে বিশ্বে প্রায় ৭০০ প্রজাতির সন্ধান মিললেও সচরাচর ১৫টি প্রজাতির দেখাই মেলে। বাংলাদেশে আছে ৭ প্রজাতির ইউক্যালিপটাস গাছ। মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে রয়েছে ৬ প্রজাতির ইউক্যালিপটাসগাছ। ঢাকা শহরে যেসব ইউক্যালিপটাস দেখা যায় সেগুলো প্রধানত ইউক্যালিপটাস সাইট্রওডোরা (Eucalyptus citriodora), ইউক্যালিপটাস গ্রান্ডিস (Eucalyptus grandis) ও ইউক্যালিপটাস স্যালিগনা (Eucalyptus saligna) প্রজাতির। মিরপুরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের রেস্ট হাউসের সামনে রয়েছে একটি লাল ফুলের ইউক্যালিপটাস (Corimbia ficifolia)। অন্য প্রজাতিগুলোর গাছে বসন্তে ছোট ছোট সাদা রঙের ফুল ফোটে, এরপরই ফল ধরে, শক্ত বীজ থেকে চারা হয়। এ গাছ লাগানোর অপকারিতা হলো, এরা মাটির অনেক গভীর থেকেও রাত দিন ২৪ ঘন্টাই পানি শোষণ করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। ফলে মাটির নীচে পানির স্তর নেমে যায়, আশেপাশে থাকা অন্য গাছেরা তখন জলকষ্টে ভুগতে থাকে। এ গাছের পাতা বিষাক্ত, পাতা ঝরে যে মাটিতে পড়ে সে মাটিতে আর কোনও গাছের চারা জন্মাতে পারে না, ফুলের রেণু অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী, এ গাছে সাধারণত কোনও পাখি বসে না। এজন্য এ গাছকে বলা হয়েছে পরিবেশ বিপর্যয়কারী উদ্ভিদ।

ঢাকা শহরে ইউক্যালিপটাস গাছ ১৯৬৫ সালে নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা দেখেছিলেন রমনা পার্কে, সেগুলো এখনও আছে। এছাড়া হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ও শেরে বাংলা নগরের ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কিছু গাছ এখনও আছে। বড় কিছু ইউক্যালিপটাস গাছ আছে শেরে বাংলা নগরে চন্দ্রিমা উদ্যানেও। রমনা পার্কে লেকের পশ্চিম পাড়ে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবনের সামনে বিশাল থামের মতো লম্বা গুড়ির ইউক্যালিপটাসগাছের বাকল খসতে দেখেছি বৈশাখে, ফুল দেখেছি জ্যৈষ্ঠে, আষাঢ়ে ফল। বাকল খসার পর সেসব গাছের কাণ্ড বেরিয়ে পড়ে ফর্সা স্থূল উরুর মতো, মোটা কাণ্ড, একহারা রং, টানা খাড়া গড়ন। কাণ্ডের মসৃণতা, সুঠাম থামের মতো কাণ্ডবিশিষ্ট স্বল্পপত্রী এরূপ গাছ এদেশে বিরল। এর প্রধান শাখাগুলো উর্ধমুখী হলেও প্রশাখাগুলো চিকন ও নতমুখী। চিরসবুজ বৃক্ষ প্রকৃতির এ গাছ বাড়ে খুব তাড়াতাড়ি। পাতা দেখতে ছুরি বা বর্শার ফলার মতো, লেবুগন্ধী। বসন্ত থেকে বর্ষার শেষ পর্যন্ত ফুল ফোটে। শাখা-প্রশাখার সীমান্তে ক্ষুদ্র ফুল ফোটে মঞ্জরিতে। ফুল মৃদু সুগন্ধী ও সাদা। ফুলের পাঁপড়ি প্রায় চোখেই পড়ে না, কেবল সুতার মতো পরাগকেশরগুলো দেখা যায়। ফল ডিম্বাকৃতি ও অজস্র।
বিদেশে ভিন্ন আরেক প্রজাতির ইউক্যালিপটাসের অবশ্য একহারা রং থাকে না, সেখানে দেখা যায় রংধনুর মতো সাত রং। কিন্তু এই রং সৃষ্টির রহস্যটা কি? ইউক্যালিপটাস গাছের বাকল কাগজের মতো পাতলা। শুকিয়ে গেলে তা গুড়ি বা ডালের গা থেকে আপনা আপনি উঠে আসে। এসব বাকলের ভেতর দিকটা প্রথমে থাকে উজ্জ্বল সবুজ। পরে সময়ের সাথে সাথে সে রং বদলে ধীরে ধীরে হয়ে যায় নীল, বেগুনি, কমলা ও মেরুণ লাল। সব বাকল একবারে ওঠে না— দফায় দফায় বাকল ওঠে আর বিভিন্ন রঙের আবির্ভাবও ঘটে দফায় দফায়। শেষে গিয়ে পুরো গাছটির গা দেখে রঙধনুর সাতরঙে রাঙানো মনে হয়।
ইউক্যালিপটাস পৃথিবীর বহুদেশে জন্মে, কিন্তু রঙধনু ইউক্যালিপটাস জন্মে শুধু উত্তর গোলার্ধে। আমেরিকার হাওয়াই, লুইজিয়ানা, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে এ গাছের দেখা মিলতে পারে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, পাপুয়া নিউগিনি ইত্যাদি দেশেও এ গাছ দেখা যায়। আমরা অনেকেই জানি যে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় এক ধরনের সুগন্ধ আছে, কোয়েলা প্রাণিরা এর পাতা খেতে খুব পছন্দ করে, কিন্তু এ গাছে পাখিদের খুব একটা বসতে দেখা যায় না। ইউক্যালিপটাসের কাঠ প্রধানত সাদা কাগজের মণ্ড তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই গাছ খুব লম্বা হয়, উচ্চতায় ২৫০ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। পাতাগুলো খুব ছোট ও পত্রাঞ্চল নিবিড় ছায়াময় নয়। ইউক্যালিপটাস এর গণগত নাম Eucalyptus, যার অর্থ বৃতি দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ পুষ্প।

চীনা পাম
পাম গাছের কথা বলতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে জীবনানন্দ দাশের ‘এই ডাঙা ছেড়ে হায়’ কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি—
‘‘বাসমতি ধানক্ষেত ছেড়ে দিয়ে মালাবারে— উটির পর্বতে
যাব নাকো, দেখিব না পামগাছ মাথা নাড়ে সমুদ্রের গানে।
কোন দেশে,— কোথায় এলাচিফুল দারুচিনি বারুণীর প্রাণে।’’

অ্যারিকেসী গোত্রের গাছগুলোকে বলা হয় পামগাছ বা পামজাতীয় গাছ। পাম জাতীয় গাছের আবাস প্রধানত আমেরিকা ও ভারতবর্ষ, আফ্রিকাতেও জন্মে পামগাছ। তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর, বন খেজুর ইত্যাদি। এর সাথে যোগ হয়েছে অয়েল পাম, তালি পাম, অ্যারিকা পাম, রয়্যাল পাম, ফিশটেইল পাম, ফ্যানলিফ পাম বা ইউরোপিয়ান ফ্যান পাম, চীনা পাম ইত্যাদি বিদেশি পামগাছ যেগুলোর অধিকাংশ লাগানো হয় শোভা বাড়ানোর জন্য। এসব বাহারি পামগাছের মধ্যে চীনা পাম অন্যতম। এই পামগাছের জন্ম চীন দেশে, তাই এ দেশে গাছটি চীনা পাম নামে পরিচিতি পেয়েছে।

চীনা পামগাছ দেখতে অনেকটা তালগাছের মতো। তবে তালগাছের সাথে এর পার্থক্য হলো, চীনা পামগাছ তালগাছের মতো লম্বা ও মোটা হয় না। রমনা পার্কে যতগুলো চীনা পামগাছ দেখেছি তার কোনোটাই ৩০-৩৫ ফুটের বেশি লম্বা না। গাছও তাল বা নারিকেল গাছের মতো মোটা না, নারিকেল গাছের চেয়েও সরু, কিন্তু সুপারির চেয়ে অনেক মোটা, পাতা হাতপাখার মতো আকৃতিবিশিষ্ট। পাতার বোঁটা বেশ শক্ত ও মজবুত, দুই প্রান্ত তীক্ষ্ণভাবে করাতের দাঁতের মতো খাঁজবিশিষ্ট। চীনা পামগাছ চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এর পাতা দেখে চেনা।

পাতা দেখতে অনেকটা তালপাতার মতো হলেও তালপাতার পত্র-গঠন ও চীনা পামগাছের পত্র-গঠনের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। তালপাতার আগাগুলো যেখানে খাড়া বা সোজা ও তীক্ষ্ণ, সেখানে চীনা পামগাছের পাতার আগাগুলো ভাঁজ হয়ে ঝুলতে থাকে। চীনা পামের পাতাগুলোকে দেখলে মনে হয় পাতার আগাগুলো যেন ঝরনাধারার মতো মাটির দিকে নেমে আসছে। তা ছাড়া তালগাছের মতো চীনা পামগাছের মেয়ে ও মর্দা গাছ আলাদা না, একই গাছে পুষ্পমঞ্জরিতে উভয়লিঙ্গিক ফুল ফোটে। গাছের মাথায় যেখান থেকে পাতাগুলো জন্মে সেখানে কাঁদিতে গ্রীষ্ম-বর্ষাকালে লম্বা ছড়ার মতো পুষ্পমঞ্জরিতে অত্যন্ত ছোট ছোট ফিকে সবুজ রঙের ফুল ফোটে। একটি কাঁদিতে প্রচুর ফুল ও ফল ধরে। কাঁদিগুলো গাছের শীর্ষে চারদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় জন্মে। কাচা ফল কালচে সবুজ বা গাঢ় নীলচে সবুজ, চকচকে, ডিম্বাকার থেকে লম্বাটে ডিম্বাকার ও ছোট। পাকলে ফলের রং গাঢ় বেগুনি বা কালচে হয়ে যায়। বীজ থেকে চারা হয়। গাছ বেশ মজবুত।

চীনা পামের ইংরেজি নাম Chinese Fan palm,উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লিভিস্টোনা চাইনেনসিস (Livistona chinensis) এবং গোত্র অ্যারিকেসী (Arecaceae)। লিভিস্টোনা নামটি এসেছে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড লিভিস্টোনের নাম থেকে, চাইনেনসিস অর্থ চৈনিক বা চীনদেশীয়। চীন, জাপান, তাইওয়ানে এ গাছ অনেক দেখা যায়। ঢাকা শহরে রমনা পার্কে পূর্বপাশের অরুণোদয় গেট দিয়ে প্রবেশ করলে মহুয়া, সোনালু, নাগলিঙ্গম, রয়্যাল পাম ও গগন শিরীষ বেষ্টিত এক খণ্ড সবুজ লনের মধ্যে কয়েকটা চীনা পাম গাছ চোখে পড়ে। সদরঘাটের কাছে আহসান মঞ্জিলের এক পাশে এক সারি চীনা পামগাছ আছে।
রয়্যাল পাম
রয়্যাল মানে রাজকীয়। প্রাচীনকালে রাজা বাদশাহ ও জমিদাররা তাদের প্রাসাদ বা বাড়ির প্রবেশ পথের দুপাশে রয়্যাল পাম লাগিয়ে তাদের আভিজাত্য প্রকাশ করতেন। রাজকীয় ভঙ্গিতে ‘চির উন্নত মম শির’ সেসব গাছগুলো যেন সেসব শাসকদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করত। এখনও নাটোরে উত্তরা গণভবনের সামনের রাস্তায় সে নিদর্শনের কিছুটা আলামত পাওয়া যায়। ঢাকা শহরেও বোধ হয় নগর পরিকল্পনাবিদেরা রয়্যাল পামের সেই আভিজাত্য ও রাজকীয় মর্যাদার কথা জানতেন। সে কারণে কি না জানি না, আমাদের জাতীয় সংসদ ভবনের দুটি প্রবেশ পথের এক পাশেও দুটি সারি করে রয়্যাল পাম গাছ লাগানো আছে। তাল ও নারকেল গাছের সহোদর হলেও উদ্যান ও পথের শোভা বাড়ানো ছাড়া এ গাছ আর কোন কাজে লাগে? এর ব্যবহার বা উপযোগিতার কথা বাদ দিলে রয়্যাল পামের মতো শোভাবর্ধক আর কোনও পামগাছ নেই।

ঢাকা শহরে এ গাছের ছড়াছড়ি। নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ১৯৬৫ সালে ‘বটল পাম’-এর দেখা পেয়েছিলেন বৃটিশ কাউন্সিল প্রাঙ্গণে। আজও সেখানে কিছু গাছ আছে। তিনি তাঁর ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে লিখেছেন, ‘‘রয়েল পাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের আপন তরু। ঢাকায় ভিক্টোরিয়া পার্কে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) একদা এই পামের অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি বিথী ছিল, এখন নেই। বর্তমানে সদরঘাটের বুড়িগঙ্গার তীর, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং বেইলী রোডে এই পাম কিছু কিছু চোখে পড়ে।’’
ঢাকা শহরে ঘুরতে ঘুরতে আরও অনেক জায়গায় রয়্যাল পামের সাথে দেখা হয়েছে। আগারগাঁওয়ে সমাজ সেবা অধিদপ্তর অফিসের আঙিনায় প্রাচীরের কোলে সারি করে লাগানো রয়্যাল পাম গাছগুলো শোভা ছড়াচ্ছে। রমনা পার্কের দক্ষিণ কোণে পাম কর্নারে অন্যান্য পামগাছের সাথে দাঁড়িয়ে আছে বয়স্ক কয়েকটি রয়্যাল পাম গাছ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশে তিন নেতার মাজারের সামনে আছে এ গাছের একটি সুদৃশ্য বিথী। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে রাস্তার ধারে লাগানো হয়েছে এক সারি রয়্যাল পাম গাছ, এ বছর দেখলাম সেসব গাছের কয়েকটিতে ফুল ও ফল ধরেছে। শেরে বাংলা নগরের আরও কয়েক স্থানে আছে। এ গাছ আছে শিক্ষা ভবন ও মিরপুরে চিড়িয়াখানার আগে বিসিআইসি কলেজের সামনে।

রয়্যাল পামের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম র্যয়স্টোনিয়া রিজিয়া (Roystonea regia) ও গোত্র অ্যারিকেসী। আমেরিকান জেনারেল রয় স্টোনের নামের সারণিক এর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম, রেজিয়া অর্থ রাজকীয়। সে অর্থে এ গাছের নাম রয়্যাল পাম যথার্থ। রয়্যাল পামকে কেউ কেউ অবশ্য ‘বটল্ পাম’ বলেও সম্বোধন করেন। আসলে বটল্ পাম ও রয়্যাল পাম স্বগোত্রীয় হলেও দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির গাছ। বটল্ বা বোতল পাম (Hyophorbe lagenicaulis) গাছের গোড়া স্ফীত, বোতলের মতো। আর রয়্যাল পামের কাণ্ডের গোড়া তরুণ অবস্থায় কিছুটা ফোলা থাকলেও পরে বড় হওয়ার সাথে সাথে কাণ্ড লম্বা চোঙ্গার মতো হয়ে যায় ও মাঝখানটা ফোলা থাকে, গোড়া ও আগার দিক কিছুটা চিকন থাকে, কাণ্ড প্রায় মসৃণ। কাণ্ড ২০ থেকে ৩০ মিটার লম্বা হয়। কিন্তু বটল্ পাম গাছ কখনও এত বেশি লম্বা হয় না। বটল্ পামগাছে কখনও চার থেকে ছয়টির বেশি পাতা মেলানো অবস্থায় থাকে না, কচি পাতার রং লালচে থেকে হালকা কমলা, পরিণত পাতার রং সবুজ। কিন্তু রয়্যাল পাম গাছে এর চেয়ে বেশি পাতা খোলা অবস্থায় থাকে, গড়ে একটি গাছে সব সময় প্রায় ১৫টি পাতা থাকে। প্রতিটি পাতা প্রায় ৪ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়, কাণ্ড খাড়া, মজবুত ও সরল-সোজা। পাতাগুলো লম্বা থামের মতো কাণ্ডের মাথায় এক সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে।

রয়্যাল পাম এজন্যই পামগোত্রীয় গাছগুলোর মধ্যে সেরা সুন্দরী। সুপারির মতো কঁদিতে ফুল ফোটে। ফুলের রং সাদা, পরাগকেশর গোলাপি। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়ণ ঘটায়। ফল গোলাকার বা উপবৃত্তাকার, দেখতে অবিকল সুপারির মতো। আকারেও প্রায় সুপারির সমান। কাচা ফলের রং সবুজ বা গাঢ় সবুজ, পাকলে খোসার রং হয় হলদে কমলা। শেষে হয়ে যায় বেগুনি-কালচে। পাকা ফল পাখি ও বাদুড়রা খেতে পছন্দ করে। এরাই বীজগুলো দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে দেয়। বীজ থেকে চারা হয়।
বনসুপারি
খামারবাড়ির মোড় থেকে আসাদ গেটের দিকে আড়ং পর্যন্ত হেঁটে যেতে কতবার কত রূপে যে মানিক মিয়া অ্যাভেনিউর পাশে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে এক সারি বন সুপারি গাছ দেখেছি। কখনও দেখেছি গাছের মাথা থেকে গোল গোল সুপারির মতো অসংখ্য লম্বা ছড়ায় ঝুলছে কাঁদি কাঁদি ফল। ফলের ভারে কাঁদি যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। একটা কাঁদির ওজন এক মণেরও বেশি হবে হয়ত! দীঘল পাতা, পত্রদণ্ডের দুপাশে কাতলা মাছের লেজের পাখনার মতো পত্রফলক, কুঁচকানো, ভাঁজ করা, পত্রকপ্রান্ত খাঁজকাটা। পাশাপাশি দুটি পত্রপত্রক রাখলে মাছের লেজের মতোই দেখায়। সারি করে বিপরীতমুখীভাবে ত্রিভুজাকার পত্রকগুলো পত্রদণ্ডের দুপাশে সাজানো, হাওয়ায় দুলিয়ে পাতারা তার আভিজাত্য প্রকাশ করছে। পাতাগুলোর এরূপ চেহারার কারণে এ গাছের ইংরেজি নামকরণ করা হয়েছে ‘ফিশটেইল পাম’। দীর্ঘ ছড়ায় গোল গোল মার্বেলের মতো ফলগুলো মালার মতো সাজানো থাকে।

ফলগুলো ছোট সুপারির মতো বলে বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে বনসুপারি, অন্য নাম কিতুল পাম, ওয়াইন পাম ও সাগু পাম। এর পাকা ফল খেতে পাখিরা আসে, এসে কাঁদির উপর বসে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। সে বিষ্ঠা কাঁদির খোলের ভেতর আটকে থাকে। সেখানে বিষ্ঠার মধ্যে থাকা বীজ থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় বট-অশ্বত্থ চারা। এসব গাছের শিকড় গাছের মাথাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে চেপে ধরে যে অত শক্তিশালী সুউচ্চ রাজকীয় গাছ হওয়ার পরও আর সেগুলোর বাঁচা কঠিন হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মাথা শুকিয়ে গাছগুলো মরতে থাকে, মৃত অংশে শুরু হয় ছত্রাকের সংক্রমণ। আবার কখনও কখনও দেখেছি কাঁদির মধ্যে দলা দলা সাদা রঙের বড় বড় ছাতরা পোকাদের আস্তানা গাড়তে। তাজা কাঁদি থেকে ওরা দলে দলে রস চুষে খেয়ে কাঁদিকে শুকিয়ে বাদামি করে ফেলে। যে শোভা বাড়ানোর জন্য গাছগুলো লাগানো হয়েছিল, সেখানে সেসব গাছের শোভা হয়ে পড়েছে হতশ্রী। এ দৃশ্যও দেখেছি বছরের পর বছর ধরে সেখানে। রমনা পার্কের সীমানা প্রাচীরের কোলেও এ গাছ চোখে পড়ে। ঢাকা শহরে বিক্ষিপ্তভাবে আরও কিছু জায়গায় ছড়িয়ে আছে বনসুপারি গাছ।

বনসুপারি গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ক্যারিয়াটা ইউরেনস (Caryata urens) ও গোত্র অ্যারিকেসী। বনসুপারি গাছ তাল বা সুপারি গাছের মতোই ডাপালাবিহীন দীর্ঘদেহী কাণ্ডের একবীজপত্রী গাছ। কাণ্ড গোলাকার চোঙার মতো। গাছ ১৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। দ্বিপক্ষল পত্রকগুলোর আকৃতি ত্রিকোণাকার, গাঢ় সবুজ। পাতার একটি শক্ত দণ্ডের দুধারে পত্রকগুলো সাজানো থাকে। একটি পাতা সাড়ে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতাগুলো শক্ত খোলের দ্বারা কাণ্ডের সাথে গাছের মাথায় আটকে থাকে ও মাথা থেকে চারদিকে বিস্তৃত থাকে। পাতা বুড়ো হলে সেসব খোসা বা খেলস আলগা হয়ে ঝরে পড়ে। খোলস অনেকটা সুপারি পাতার খোলসের মতো।
পাতার কোল থেকে পুষ্পমঞ্জরি জন্মে। মালার মতো লম্বা ছড়ায় অসংখ্য ফুলে ভরা থাকে প্রতিটি পুষ্পমঞ্জরি। পুষ্পমঞ্জরি ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় যা মাটির দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় থকে। একটি কাঁদিতে অনেকগুলো পুষ্পমঞ্জরি বা ছড়া থাকে, দেখে সেগুলো ঘোড়ার লেজের মতো মনে হয়। ফুলের রং সাদা। গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে। ফুল ফোটার সময় গাছের তলায় অসংখ্য ফুল ঝরে পড়ে। ফুল একলিঙ্গিক। অসংখ্য ফল ধরে প্রতিটি কাঁদিতে। ফল গোলাকার মার্বেলের মতো। কাচা ফলের রং সবুজ, পাকলে লাল হয়ে যায়। পাকা ফলের অক্সালিক অ্যাসিড থাকায় তার স্পর্শে ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই এ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের শেষাংশ রাকা হয়েছে ‘ইউরিয়েনস’ যার অর্থ জ্বালাকারী। এ নামের প্রথম অংশ ‘ক্যারিওটা’, গ্রিক এই শব্দের অর্থ কঠিন ফল। প্রতিটি ফলের ভেতরে একটি শক্ত বীজ থাকে যা সুপারির বিকল্প হিসেবে খাওয়া যায়। বীজ থেকে চারা হয়। এই বীজ কাঠবিড়ালীদের খুব পছন্দ, তারা ফল পাকলে বীজ খেতে গাছে ওঠে।
বনসুপারি গাছের কাণ্ড যথেষ্ট শর্করাসমৃদ্ধ, তালগাছের মতো ফুলের কাঁদি কেটে মিষ্টি রস নামানো যায়। সে রস জ্বাল দিয়ে গুড় বানানো যায়, রস থেকে মদও তৈরি হয়। শ্রীলংকায় এ গাছের এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে। হাতিরা এ গাছের পাতা খায়। পাতার আঁশ খুব শক্ত, আঁশ থেকে কম্বোডিয়ায় দড়ি ও ঝুড়ি বানানো হয়, তবে আমাদের দেশে এ গাছ শোভাবর্ধক বৃক্ষ হিসেবেই লাগানো হয়। কাণ্ডের নরম শাঁস খেতে সাগুর মতো লাগে।
সরস্বতী চাঁপা
একেই বলে দশচক্রে ভগবান ভূত! দশজন যদি ভগবানকে ভূত বলে ডাকে তবে তার সে নামটাই একদিন স্থায়ী হয়ে যায়। লোকমুখের রটনা খুবই মারাত্মক। কখনও কখনও তা বিপর্যয়ীও হয়। তবে সরস্বতী চাঁপার ক্ষেত্রে কথাটা কতটা সত্য হবে জানিনা। কেননা এ গাছের চারা সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছে ভারত থেকে। এ গাছের আর কোনও বাংলা নাম না থাকায় নার্সারির লোকেরা একে ডাকতে শুরু করেন ‘সরস্বতী চাঁপা’ বলে। এরপর সেসব নার্সারি থেকে যারা চারা কিনে নিয়ে বাগানে লাগান তখন তার ধবধবে সাদা সুগন্ধী ফুলের রূপে বিমোহিত হয়ে নার্সারির লোকদের দেওয়া সে নামকেই আপন করে নিয়ে সে গাছকে তারা ডাকতে শুরু করেন ‘সরস্বতী চাঁপা’ বলে। আবার কেউ কেউ এ নামটাকে এতটাই পছন্দ করেছেন যে, সে নামের পক্ষে বেশ জোরালো একটা যুক্তিও দাঁড় করিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, এ গাছের কাঠ দিয়ে বাদ্যযন্ত্র— বীণা তৈরি হয়। বীণা আর বই হলো সরস্বতীর হাতের শোভা, সঙ্গীতকলা ও জ্ঞানের প্রতীক। আবার ফুলের শুভ্রতাও শুভ্রবসনা সরস্বতীর সাথে মানানসই। তাই এ গাছের নাম সরস্বতী চাঁপা তো হতেই পারে!

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরাই সাধারণত যে কোনও উদ্ভিদের নামকরণ করেন তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। বৈশিষ্ট্যের ওপর ভর করে প্রথমে করা হয় তার দ্বিপদী নামকরণ, যাকে আমরা উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম বা প্রজাতিগত নাম বলি। এসব নামের দুটো অংশ থাকে যাকে বলে ‘এপিথেট’ বা নামাংশ। এরপর করা হয় তার সাধারণ নাম, যা সাধারণত ‘ইংরেজি নাম’ হিসেবে পরিচিত হয়। এরপর আসে স্থানীয় নাম। এটা বিভিন্ন ভাষাভাষীর কাছে বিভিন্ন আঞ্চলিক নামে প্রতিষ্ঠা পায়। এসব নাম যে বিজ্ঞানীরা করেন তা নয়, স্থানীয় লোকেরাই এসব নাম দেন, তাই এগুলোকে বলা যায় ‘লোক নাম’।
‘সরস্বতী চাঁপা’ নামটিকে যদি বাংলাদেশি লোকেরা নাম দিয়ে থাকেন তবে সেটা দোষের কিছু নয়। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে, তার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামটা যেন আমরা না বদলাই, সে অধিকার বিজ্ঞানীরা আমাদের দেননি।
পাঁচ ছয় বছর আগে ধানমণ্ডি ৯ নম্বর রোডের একটা বাড়ি ‘টোনাটুনি’তে সরস্বতী চাঁপা গাছ দেখেছিলাম। খুব ছোট সে গাছে লম্বা ঝুলন্ত ছড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা রঙের ফুল ফুটতে দেখেছিলাম। তেমন আহামরি রূপ না থাকায় তাকে বেশি গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু বাগানের মালিক ডা. ফেরদৌস আরা যখন সে ফুলের সুগন্ধ শুঁকে দেখতে বললেন, তখন সে সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে গেলাম। ওই ছোট্ট ফুলের এত সৌরভ! তিনি জানিয়েছিলেন, গাছটা তিনি ঢাকার বৃক্ষমেলা থেকে কিনেছিলেন। এরপর থেকেই গাছটার খোঁজ খবর নিতে শুরু করি। সংবাদ পেয়েও যাই নানাজনের ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে। তার মানে সরস্বতী চাঁপা বাংলার মাটিতে ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু এর বিস্তারিত তথ্য তেমন পেলাম না।

বছর দুয়েক আগে আশুলিয়ার চারাবাগের এক নার্সারিতে চারা পেয়ে আমিও তা কিনে নিয়ে টাঙ্গাইলের সখিপুরে যাদবপুর গ্রামে ‘কবি নজরুল পার্ক’-এর চাঁপাবাগে লাগাই। সেখানে অন্যান্য চাঁপাগাছের সাথে সরস্বতী চাঁপার গাছও বড় হতে থাকে ও পরের বছরই তাতে ফুল ফোটে। পাতার কোল থেকে প্রায আট-দশ ইঞ্চি লম্বা ছড়া বা পুষ্পমঞ্জরিতে অনেকগুলো সাদা রঙের ফুল ফোটে দফায় দফায়। তার কাছে যেতেই সেই সুগন্ধ। পরের বছর দেখলাম গাছটা আরও বড় হয়েছে, বাড়ছে বেশ দ্রুত।
তবে, ঢাকায় রমনা পার্কের মধ্যেই যে সরস্বতী চাঁপার একটা বয়স্ক গাছ আছে তা কোনোদিন চোখে পড়েনি। মহুয়া চত্বরের পাশে সে গাছটায় বর্ষাকালেও ফুল ফুটছে। বড় বৃক্ষের পাতার ফাঁকে ছোট ছোট লম্বা মঞ্জরিতে ছোট ছোট ফুল থাকায় হয়ত তা চোখ এড়িয়ে গেছে। গাছটার বাকলও অদ্ভুত। বাদামি রঙের টিস্যু পেপারের মতো পরতে পরতে সাজানো বাকল, লম্বা চেরা চেরা ফাটলের মতো দাগ, বর্ষার জলে ভিজে জবজবে হয়ে আছে।
কিন্তু এ দেশের বইপত্র ঘেঁটে এই গাছের কোনও উল্লেখ কোথাও পেলাম না। অবশ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিদেশি একটি বইয়ে ওর উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম পেলাম— Citharexylum spinosum, গোত্র ভার্বেনেসী, ইংরেজি নাম ‘ফ্লোরিডা ফিডলউড’। তার মানে এ গাছটার জন্মভূমি আমেরিকার ফ্লোরিডা। ক্যারিবীয় দেশগুলোতে এ গাছ বেশ দেখা যায়। গাছ আছে ভেনেজুয়েলা, গায়ানা ও সুরিনামে, ভারতেও আছে। মনে হয় সেখান থেকেই আমাদের দেশে এ গাছের অনুপ্রবেশ। প্রতিবছর বৃক্ষমেলার সুবাদে এদেশে চারা ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে, বিশেষ করে ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে বহু নতুন নতুন গাছ এনে বাংলার উদ্ভিদসম্পদকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছেন। এটিও তেমনিভাবে এসেছে। এ গাছের প্রতিষ্ঠিত কোনও বাংলা নাম নেই। সরস্বতী চাঁপা নামটিই আমরা গ্রহণ করতে পারি।

সরস্বতী চাঁপা ছোট বৃক্ষ প্রকৃতির বহুবর্ষজীবী চিরসবুজ গাছ। গাছ ১৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা উপবৃত্তাকার, পাতার বোঁটার রং কমলা আভাযুক্ত। পাতা ও ডালের সংযোগস্থল বা কক্ষ থেকে লম্বা ছড়ার মতো পুষ্পমঞ্জরিতে প্রায় সারা বছরই ফুল ফোটে, ফুলগুলো অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। পুষ্পমঞ্জরির দৈর্ঘ্য ৮ থেকে ১৬ সেন্টিমিটার, পাঁপড়ি পাঁচটি। হিজল ফুলের মতো ছড়ায় পুষ্পমঞ্জরি ঝুলতে থাকে। ফুলশেষে গোলাকার ফল হয়। পাকলে ফলের রং হয় লাল থেকে কালো। বন্যপ্রাণী ও পাখিদের খুব প্রিয় এই ফল। সুগন্ধী ফুল প্রজাপতিদেরও আকৃষ্ট করে। বীজ থেকে চারা হয়। তাই সহজে বাগানে এ গাছের বংশবৃদ্ধি নিজেরাই করা যায়। এ গাছ আধোছায়া ও রোদে ভালো হয়। বাগানের শোভাময়ী গাছ হিসেবে লাগানো যায়। গাছ মাঝারি লবণাক্ততা সইতে পারে। তাই উপকূলীয় অঞ্চলের বাগানেও এ গাছ লাগানো যায়।
সফেদা
এ দেশে মিষ্টি ফলের সংখ্যা খুব কম। তাই আম ও কলা বাদ দিলে মিষ্টি আর রসাল যে ফলটির কথা প্রথম মনে আসে তা হলো সফেদা। এ দেশে উপকূলীয় এলাকায় নারিকেল-আমড়া ছাড়া অন্য ফল বিশেষ একটা হয় না। কিন্তু সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশালে গেলে দেখা যায় অজস্র সফেদা গাছ। বলা যায় উপকূলীয় অঞ্চলের এটি একটি অন্যতম প্রধান ফল। তেমনি ভারতের উপকূল অঞ্চল যথা— মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যেও প্রচুর সফেদা জন্মাতে দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকা আর থাইল্যান্ডে এখন ভালো সফেদা হচ্ছে। সেসব দেশে সফেদার অনেক আধুনিক জাত উদ্ভাবিত হয়েছে।

সফেদা ফল দেখতে মেটে রঙের, খসখসে খোসা, দেখতে পোড়া মাটির বলের মতো মনে হয়। কিন্তু পাকা ফল যে এত রসাল, সুস্বাদু আর মিষ্টি তা না খেলে বোঝা যায় না। ফলের গড়ন অনুসারে এ দেশে প্রধানত তিন ধরনের সফেদা দেখা যায়। এক ধরনের সফেদা গোলাকার বলের মতো ও বড়, এটি অঞ্চলভেদে গবেদা নামেও পরিচিত। তুলনামূলকভাবে এই সফেদা কম মিষ্টি ও সমভাবে পাকে না, শাঁস অন্য সফেদার চেয়ে কম রসাল ও নরম, বারোমাস ফলে। অন্যটি ডিম্বাকার ও ছোট, এটির স্বাদ মিষ্টি ও শাঁস রসাল। সম্প্রতি এমন মাকু আকৃতির সফেদা এ দেশে দেখা যাচ্ছে। এ আকারের সফেদাও দুই রকম— ছোট ও বড়। ছোট জাতটি আমাদের দেশি যা বকুল সফেদা নামে পরিচিত। বকুল সফেদা সবচেয়ে সুস্বাদু ও মিষ্টি। মাকু আকৃতির বড় সফেদার জাত বিদেশি, এগুলোও মিষ্টি, প্রচুর ধরে।
সম্প্রতি এ দেশে ডিম্বাকার সফেদার একটি নতুন জাতের চাষ শুরু হয়েছে। জাতটি এসেছে থাইল্যান্ড থেকে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে ‘থাই সফেদা’। এ জাতটি তুলনামূলকভাবে এ দেশের ডিম্বাকার সফেদার চেয়ে বড়, লম্বা, রসাল এবং ফলনও বেশি, বীজ ছোট। এমনকি বীজবিহীন সফেদাও এখন থাইল্যান্ড থেকে এ দেশে প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। এবার বৃক্ষমেলায় গিয়ে দেখতে পেলাম নতুন আরেক জাতের সফেদা গাছ যার পাতাগুলো সবুজ না, সবুজে-হলুদে চিত্রিত। একে ভেরিগেটেড বা বিচিত্র সফেদা গাছ বলা যায়। বাগানের বৈচিত্র্য বাড়াতে এ শোভাময়ী গাছকে ঠাঁই দেওয়া যেতে পারে। তবে এসব গাছে ফল কেমন ধরবে তা পরীক্ষা-নীরিক্ষার বিষয়।
সফেদার ফুল ও ফল ধরার সময় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নয়। সারা বছরই গাছে ফুল-ফল দেখা যায়। সম্প্রতি বিদেশি কিছু জাত আসায় ফল ধরার সব মৌসুমী বাধা ভেঙ্গে গেছে। তাছাড়া জোড়-কলম করে চারা উৎপাদন করায় ছোট ও অল্পবয়সী গাছেই ফল ধরে। ঢাকায় সফেদা গাছ কম চোখে পড়ে। রমনা উদ্যানে সফেদা গাছ আছে। ঢাকার অনেক ছাদবাগানে এখন সফেদা গাছ লাগানো হয়েছে।

সফেদার ইংরেজি নাম নিসবেরি বা স্যাপেটা। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ম্যানিলকারা জ্যাপোটা (Manilkara zapota), গোত্র স্যাপোটিসী। জ্যাপোটা সফেদার মেক্সিকান নাম। আমেরিকার উষ্ণমণ্ডল তথা মেক্সিকো এর আদিনিবাস। সফেদা চিরসবুজ মাঝারি আকারের বৃক্ষ। কাণ্ড সরল, বাকল অমসৃণ ও কালচে বাদামি। ডালপালা সুবিস্তৃত ও ছাতার মতো গাছের গড়ন। কাঠ খুব শক্ত ও লালচে-বাদামি। ডাল ও পাতা ভাঙলে সাদা দুধের মতো কষ বের হয় যাকে বলে ল্যাটেক্স বা দুধকষ। এজন্য এদের ক্ষীরীবৃক্ষও বলা হয়।
পাতা ডালের আগায় গুচ্ছবদ্ধ, বল্লমাকার, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ, মসৃণ, টকটকে সবুজ, নিচের পিঠ হালকা সবুজ, কিনারা মসৃণ ও খাঁজবিহিন। প্রচুর পাতা হওয়ায় গাছটি ছায়াদানকারী ও শোভাময়ী। প্রধানত গরমকালে ফুল ফোটে, তবে অন্য সময়েও ফুল দেখা যায়। ফুল অনেকটা মহুয়া ফুলের মতো, অনাকর্ষণীয়, উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট। ফুলের পাপড়ি প্রায় অদৃশ্যমান, যা পাপড়ির মতো দেখায় সেগুলো রূপান্তরিত পরাগকেশর। পাপড়ি থাকে ছয়টি, যুক্ত দল, কিন্তু পাপড়ির উপরের দিক বিযুক্ত। কাচা ফল শক্ত ও বাদামি, গুঁড়ার মতো এক ধরনের আবরণে আবৃত থাকে কাচা ফলের খোসা। ফল পাকার সময় এসব গুঁড়ো খোসার গা থেকে সরে যায় ও খোসা মসৃণ হয়ে ওঠে। খোসা খুব পাতলা, ভেতরে কোয়ার মতো শাঁস থাকে। পাকা ফলের শাঁস রসাল, নরম ও সুস্বাদু, হালকা বাদামি রঙের, শাঁসের মধ্যে লম্বাটে ডিম্বাকার কালচে খয়েরি চকচকে শক্ত বীজ থাকে। বীজ থেকে চারা হলেও তা করা যায় না। সফেদার চারা তৈরি করা হয় খিরখেজুর বা খিরনির চারার ওপর জোড়-কলম করে। কলমের গাছে তিন-চার বছর বয়স থেকেই ফল ধরতে শুরু করে। ঢাকা শহরে বিভিন্ন বাগানে, উদ্যানে, জলাশয়ের ধারে সফেদা গাছ লাগানো যায়।
মেহগনি
মেহগনি গাছ নিয়ে লেখার ইচ্ছে ছিল না। কেননা, এ গাছটি আমার পছন্দ না। হয়ত পড়েছিলাম কোনোদিন যে, মেহগনি গাছ বিষবৃক্ষ, মাটি ও পরিবেশের জন্য এ গাছ কল্যাণকর নয়। কিন্তু পরে ভাবলাম, আমেরিকায় জন্ম নেওয়া এই বিদেশি গাছ কি করে আমাদের দেশে এতো ছড়িয়ে পড়ল আর মূল্যবান কাঠের গাছ হয়ে উঠল?

বর্তমানে সারা দেশে তো বটেই, ঢাকা শহরেও মেহগনি গাছের ছড়াছড়ি। সচিবালয়ের সামনের সড়কে জিপিও মোড় থেকে শিক্ষা ভবন পর্যন্ত সড়ক বিভাজকেই রয়েছে মেহগনি গাছের একটি দীর্ঘ সারি। গবেষকরা বলছেন, মেহগনির পাতায় ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকায় তা গাছের তলায় পড়ার পর মাটিকে অনুর্বর করে তোলে, এমনকি সেরূপ স্থানে কোনও পোকামাকড়ও বাঁচতে পারে না। পাতা পানিকেও দূষিত করে। ফলে তা মাছ ও হাঁসের জন্যও ক্ষতিকর। আর ফলগুলো এতটাই বিষাক্ত যে তা ভেঙ্গে পানিতে ভিজিয়ে তা কীটনাশক হিসেবে স্প্রে করলে পোকামাকড় মরে যায়। যে গাছ আমাদের পরিবেশের বাস্তুসংস্তানকে নষ্ট করছে সেই গাছকে আমরা সোৎসাহে লাগাচ্ছি শুধু কাঠের প্রয়োজন মেটাতে। অথচ ফিলিপাইনে পরিবেশবিদেরা পরিবেশ ও বন্যজীবের ওপর মেহগনির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে মেহগনি গাছ রোপণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কজনই বা এসব কথা জানেন বা বোঝেন? তাই তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না। কথাগুলো বলার জন্যই শেষে মেহগনি নিয়ে লিখতে হলো। এতেও হয়ত কেউ মেহগনি গাছ লাগানো বন্ধ করবে না। অদেখা ক্ষতির চেয়ে দেখা লাভটাই মুখ্য। এখন তো দরোজার কাঠ ও আসবাবপত্র তৈরির জন্য মেহগনি কাঠের কদর ও দর দুইই বেড়ে গেছে। বৃটিশরা মেহগনি কাঠ দিয়ে জাহাজ বানাত। একশ বছর আগে মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি ইংরেজ অধিকৃত একটি স্প্যানিশ জাহাজকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একশ বছরেও সেসব কাঠের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। মেহগনি কাঠ এমনই টেকসই। কাঠের মূল্যে মেহগনি গাছ বিশ্ব স্বীকৃত।
মেহগনির আদি জন্মস্থান জ্যামাইকা ও মধ্য আমেরিকা। জানা যায়, ১৭৯৫ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে মেহগনি গাছকে ভারতবর্ষে আনা হয় আসবাবপত্রের কাঠ উৎপাদনের জন্য। আঠারো শতকের শেষে মেহগনি প্রথম এ উপমহাদেশে আসে কলকাতার রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনে। এরপরপরই মেহগনি লাগানো শুরু হয় আমাদের দেশে। বৃটিশ কোম্পানির লোকজন স্থানে স্থানে মেহগনির বাগান গড়ে তোলে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘ঢাকার ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রণেতা শ্রী যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, ‘‘পূর্ব্বে এই জেলায় মেহগনি বৃক্ষ ছিল না। ক্লে সাহেবের (ঢাকার তদানিন্তন কালেক্টর) রিপোর্টের ফলে গবর্নমেন্ট কয়েকটি মেহগনি বৃক্ষ ঢাকাতে রোপণ করেন। মিঃ ক্লে বলেন, নিম্নবঙ্গের ভূমি মেহগনি চাষের উপযোগী।’’ এখন তো আর উঁচু-নিচু বাছ বিচার নেই— সব জায়গাতেই এখন মেহগনি গাছ লাগানো হচ্ছে।
বাংলাদেশে দুই প্রজাতির মেহগনি দেখা যায়। ছোট পাতার মেহগনি (Swietenia humilis) ও বড় পাতার মেহগনি (Swietenia macrophylla)। দুটি প্রজাতিই মেলিয়েসী গোত্রের। মেহগনি পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ। বসন্তের শুরুতে মেহগনি গাছের সব পাতা ঝরে যায়। রিক্ত সেসব ডালে পাতা গজায় বসন্তের শেষে। গাছের গুড়ি বা কাণ্ড সরল-সোজা, বাকল অমসৃণ ও পুরু, কাঠ লালচে বাদামি। পাতা যৌগিক, একপক্ষল, জোড়পক্ষ, পত্রিকার একদিক সামান্য বাঁকানো, গাঢ় সবুজ, মসৃণ ও চকচকে। তরুণ বা চারা গাছের পাতা বয়স্ক গাছের চেয়ে বড়। ক্ষুদ ফুল বর্ণে ম্লান সবুজ ও অনুজ্বল। বসন্তের শেষে ফুল ফোটে। ঝরা ফুল গাছতলায় পড়ে প্রচুর। ফল প্রায় গোলাকৃতি, শক্ত, পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত বহুবীজবিশিষ্ট ও বাদামি। উন্নতমানের আসবাবপত্র তৈরি হয়, প্লাইউড তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। মেহগনির বীজের তেল উন্নত জৈবকীটনাশক ও খৈল সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। চর্ম রোগ, একজিমা, উচ্চরক্তচাপ এবং গনোরিয়াসহ বহুবিধ যৌন রোগ ও ডায়াবেটিস রোগ নিরাময়ে মেহগনির বীজ ব্যবহার করা হয়। মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে গাছের বীজ সংগ্রহ করতে হয়। বীজ গজানোর হার প্রায় শতকরা ষাট ভাগ।

ঢাকা শহরে বড় পাতার মেহগনি গাছই প্রায় সর্বত্র চোখে পড়ে। ধানমণ্ডি এলাকায় ছোট পাতার মেহগনি গাছ চোখে পড়ে দু’একটি, বিশেষ করে ছয় নম্বর রোডে। আঠারো শতকের শেষ বা ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে, বিশেষ করে যখন ঢাকার বৃক্ষ রোপণ পরিকল্পনা করা হয় তখন বিদেশ থেকে কিছু মেহগনির চারা এনে লাগানো হয়। ঢাকা শহরে মেহগনি গাছ সম্পর্কে নিসর্গী দ্বিজেন শর্মা ‘শ্যামলী নিসর্গ’ বইয়ে লিখেছেন, ‘‘ঢাকায় নিউমার্কেট থেকে ইডেন কলেজ পর্যন্ত আজিমপুর রোড এবং ফজলুল হক হলের পাশের কলেজ রোড মেহগনি বিথীতে ছায়ানিবিড়। এ ছাড়াও রমনার টেলিফোন হাউস এবং পার্ক অ্যাভেনিউতে এদের প্রাচুর্য চোখে পড়ে।’’
আজও সেসব গাছের অনেকগুলো পুরনো মেহগনি গাছ সেখানে চোখে পড়ে। বিশেষ করে রমনা উদ্যানের মধ্যে টেনিস কোর্টের পাশের অংশে অনেকগুলো প্রাচীন বড় মেহগনি গাছ দেখা যায়। ধানমণ্ডির বিভিন্ন সড়কের পাশে রয়েছে কিছু বয়স্ক মেহগনি গাছ। ঢাকা শহরে পথতরু হিসেবে মেহগনি গাছ লাগানোর উপযোগী।
বৃক্ষের চেয়ে সুন্দর কোনো কবিতা নেই
‘‘আমার ধারণা, একটি গাছের চেয়ে সুন্দর কবিতা আর কোথাও মিলবে না।’’ কথাগুলো লিখেছিলেন জয়েস কিমলার (১৮৮৬-১৯১৮) তাঁর ‘ট্রিজ’ কবিতায়। কবিতাটি ১৯১৩ সালের আগস্ট সংখ্যায় পোয়েট্রি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত শুধু এ কবিতাটিই নয়, বৃক্ষ সম্পর্কে তাঁর বোধ আমাদের বিস্মিত করে। যেমন তিনি বলেছিলেন, ‘‘কবিতা আমার মতো মূর্খেরাই নির্মাণ করে, তবে কিনা ঈশ্বরই কেবল বৃক্ষ সৃষ্টিতে সক্ষম।’’ যখন কোনও গাছের কাছে যাই, অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। কী অভাবনীয় সাম্য ও সুন্দর তার প্রতিটি অঙ্গে তারা ধরে রেখেছে। গাছের ডালপালা আর পাতা এমনভাবে জন্মে যেন একটি পাতা আর একটি পাতাকে সূর্যালোক পাওয়াতে আড়াল না করে। ফুলগুলো পুষ্পমঞ্জরিতে এমনভাবে ফোটে যাতে প্রতিটি জীব ওদের দেখতে পায়। ফুলে এমন সব রঙের বিন্যাস সৃষ্টি করে যা কোনও শিল্পীই পারেন না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেলে বর্ণকণিকার এসব রঙের খেলা দেখে স্রষ্টার প্রতি মাথা নত হয়ে আসে, প্রকৃতিমাতার এসব রহস্য আমাদের বোধের অতীত।
বৃক্ষ কেবল একটি বৃক্ষ না, এর প্রতিটি পাতা এক একটি অক্ষর, ফুল-কুঁড়িরা ছন্দের অলংকার— সব মিলিয়ে প্রতিটি বৃক্ষই এক একটি স্বতন্ত্র কবিতা। কেবল সে বৃক্ষকে পড়ার শক্তি আমাদের থাকা চাই, তাহলেই আমরা কবিতার মতোই প্রকৃতির রসসুধা পান করে তৃপ্ত হতে পারব।
লেখক: কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক।
ইমেইল: [email protected]